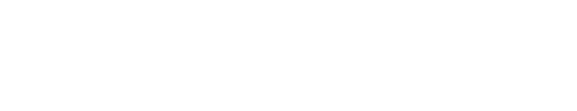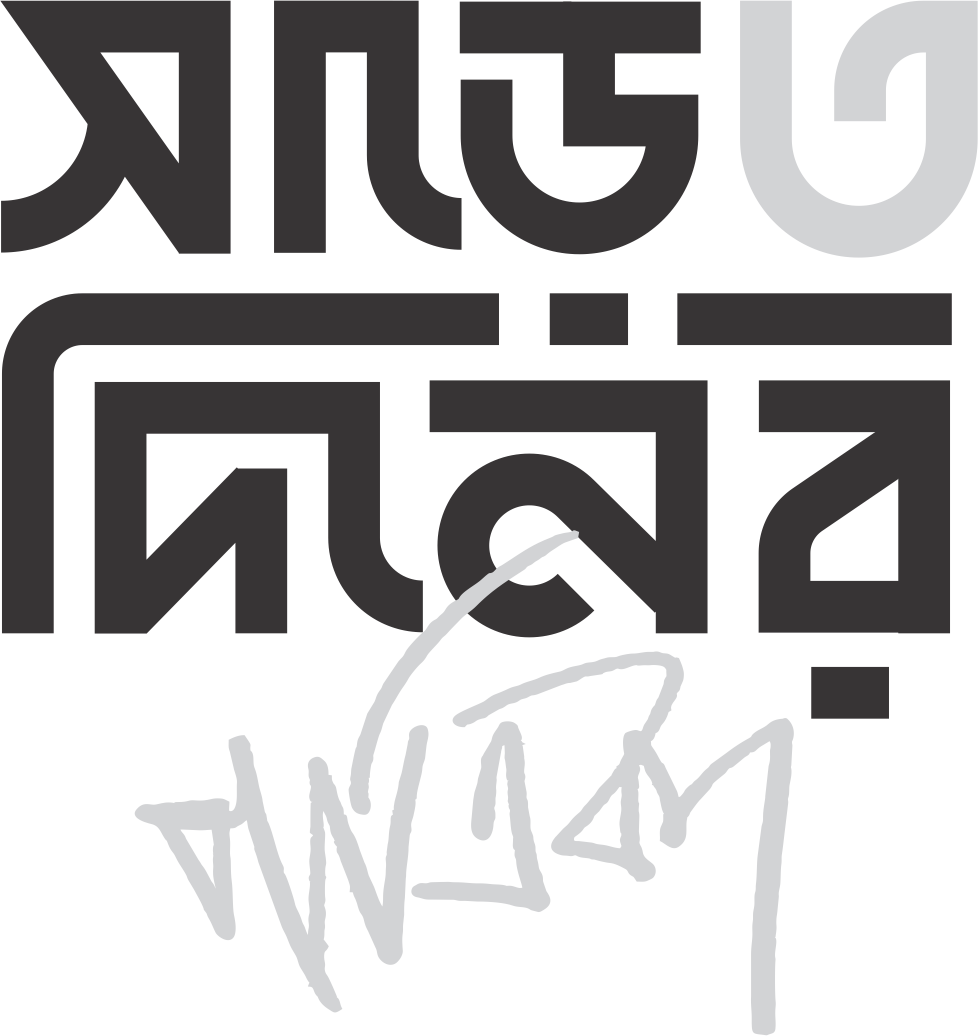খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনুবাদক পরিচয়ে সমধিক পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। পেশাগতভাবে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত এই মানুষটির আস্থা অনুবাদের সৃজনশীলতায়। মূল ভাষা থেকে লক্ষ্যভাষায় এসে একটি টেক্সট আলাদা একটি সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে একজন অনুবাদক স্বাধীনতা নিতেই পারেনÑতিনি এরকমই মনে করেন। অনুবাদকর্মের জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পুরস্কারসহ নানান সম্মাননা। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থÑস্বীকারোক্তি : জাঁ-জ্যাক রুশো; মিথের শক্তি, বিল ময়ার্সের সঙ্গে কথোপকথন : জোসেফ ক্যাম্পবেল; জোরবা দ্য গ্রিক : নিকোস কাজানজাকিস; আত্মজীবনী, গ্রেকোর কাছে প্রতিবেদন : নিকোস কাজানজাকিস; মেয়েদের যুদ্ধ ও অন্যান্য গল্প : চিনুয়া আচেবে; গালিভারের ভ্রমণকাহিনি (কিশোর উপযোগী) : জোনাথন সুইফট। গুণী এই অনুবাদকের মুখোমুখি হয়েছিলেন এহসান হায়দার
- আপনি অনুবাদ শুরু করেছিলেন যখন, তখন বিশেষ কোনো ভাবনা ছিল কি এর পেছনে?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : অবশ্যই আঁটঘাট বেঁধে অনুবাদ করতে নামিনি। মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া শহরের অদূরে পোড়াদহে যে গৃহস্থবাড়িতে মাসখানেক ছিলাম, সেখানে শালোখভের Early Stories বইটা কীভাবে যেন সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় যে টালমাটাল অবস্থা চলছিল তারই প্রেক্ষাপটে লেখা ছ’টি গল্প। সম্ভবত একটা করেছিলাম সে সময়। এরও অনেক বছর পর সবগুলো অনুবাদ করে ‘মুক্তধারা’কে দিই; ওরা ১৯৮৬ সালের দিকে প্রথম জীবনের গল্প শিরোনামে তা বই আকারে বের করে।
- একজন অনুবাদক যখন কোনো অনুবাদ করেন, সেই সময়ে কোন বিষয়গুলোতে বিশেষ খেয়াল রাখেন?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : কর্মরত অবস্থায় মোটা দাগে অনুবাদকের মনস্তত্ত্ব এবং কবিসাহিত্যিকের মনস্তত্ত্বে মনে হয় তেমন পার্থক্য থাকে না। তবে অনুবাদককে একজন লেখকের একটি টেক্সট সামনে রেখে তার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, সংস্কৃতি, ভাষা, চরিত্র সবকিছুকেই টার্গেট পাঠকের জন্য প্রস্তুত করতে হয়। সেক্ষেত্রে কবি বা কথাশিল্পী বা নাট্যকারের স্বাধীনতা অনেক বেশি। তিনি তার সামনে বিস্তৃত সমাজ, সংস্কৃতি, নিসর্গ, চরিত্র ইত্যাদিকে রূপান্তরিত করেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়; সেক্ষেত্রে একজন অনুবাদকের সামনে থাকে একটি টেক্সট এবং সেই টেক্সটের সবকিছুকে অন্য একটি ভাষায় তিনি লক্ষ্য পাঠকের জন্য একটি নতুন টেক্সট-এ প্রস্তুত করেন। এটি করতে গিয়ে তাকে মনে রাখতে হয় যেন মূলগ্রন্থ থেকে বেশি সরে না যান। মূলের প্রতি যতটা বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব তা থেকে নতুন একটা কিছু সৃষ্টি করাই অনুবাদকের সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং কতটুকু রাখবেন, কতটুকু ফেলবেন এই দ্বন্দ্বেই তাঁর সৃজনশীলতার সুযোগ থাকে সবচেয়ে বেশি।
- অনুবাদকের প্রস্তুতি কেমন থাকতে হয়?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : অনুবাদকের প্রস্তুতি বলতে আমি বুঝি তার দীর্ঘদিনের উন্নত শিল্পসাহিত্য পাঠের ফলে সৃষ্ট সাহিত্যবোধ, লক্ষ্য ও মূল ভাষায় খুব ভালো দখল, বিশেষ করে লক্ষ্য ভাষায় দখলটাই থাকতে হয় বেশি। আমি বিশ্বাস করি না একজন ব্যক্তি দুটো ভাষায় সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারে। একাধিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করে ওইসব ভাষার প্রত্যেকটিতেই সমান উৎকর্ষ লাভ করে তাতে সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং সমানভাবে পরিচিতÑবিশ্বসাহিত্যে এমন লেখক কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। যেমন মিল্টন, অস্কার ওয়াইল্ড, স্যামুয়েল বেকেট একাধিক ভাষায় লিখলেও তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যেরই লেখকÑল্যাটিন কিংবা ফরাসি সাহিত্যের নন।
- আপনি যখন কোনো একটা টেক্সট অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেন, তখন কোন বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষভাবে ভাবেন?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ধরলে বলি, যে-বই পড়ে ভালো লাগে এবং মনে করি অনুবাদে সেটা সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারব, সেই বই-ই অনুবাদ করি। আমার কাছে কোনো কোনো লেখকের বই, তাদের প্রকাশভঙ্গি অনুবাদবান্ধব বলে মনে হয়, যেমন চিনুয়া আচেবে, রিচার্ড রাইট, নিকোস কাজানজাকিস। এটাও নির্ভর করে অনুবাদকের মানসিক প্রবণতা, সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাসের ওপর।
- একটা সফল অনুবাদ বলতে পারি কখন আমরা?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : পাঠকপ্রিয়তাকে এক অর্থে সফল বলা চলেÑএমনকি অনুবাদক যদি মূল থেকে কিছুটা সরে গিয়েও তা অর্জন করতে পারেন, তবুও। তাই বলে লক্ষ্য ভাষার পাঠককে সামনে রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে অনুবাদকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি নতুন সৃষ্টিকর্ম করাটাও সমীচীন নয়। এ ধরনের কাজকে ভাবানুবাদ, রূপান্তর ইত্যাদি বলাই ভালো। গ্রিক লেখক কাজানজাকিসের উপন্যাস জোরবা দ্য গ্রিক পঞ্চাশের দশকে ফরাসি অনুবাদ থেকে ইংরেজিতে করেছিলেন কার্ল ওয়াইল্ডম্যান। তিনি অনাবশ্যক স্বাধীনতা নিয়ে যা মূল বইয়ে নেই ধুমসে সেসব যোগ করে অনুবাদ করেন। এবং এই বইটিই দারুণ জনপ্রিয় হয়। এর প্রায় বাষট্টি বছর পর পিটার বিয়েন যখন মূল গ্রিক থেকে অনুবাদ করেন, কেবল তখনই আমরা মূল বইয়ের একটি বিশ্বস্ত অনুবাদ পাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি লক্ষ্য ভাষার পাঠকের দিকে চোখ রেখেই অনুবাদ করি। উদ্দেশ্য তো আমার পাঠক। আমার অনুবাদ পড়ে যদি আমার পাঠকই না বুঝলো তো অনুবাদের ফায়দা কী? এজন্য মূল টেক্সটের প্রতি যতটা পারা যায় বিশ্বস্ত থেকে সূক্ষ্ম ও মোটা দাগের পরিবর্তনগুলো ঘটাতে হয়। মূল লেখার প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে মূলের কতটুকু পরিবর্তন করতে হবে কিংবা লক্ষ্য পাঠকের গ্রহণযোগ্যতার জন্য কতটুকু আপোষ করতে হবে সেটার এখতিয়ার অনুবাদকের। এই দুইয়ের একটা সমঝোতার মধ্যেই নিহিত অনুবাদকের সৃজনশীলতা।
- অনুবাদসাহিত্য বাংলাদেশে আগের তুলানায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, এ বিষয়ে আপনার ভাবনা বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : অনুবাদ খুব প্রাচীন একটি আর্ট ফর্মÑবলতে গেলে সাহিত্যের শুরু থেকেই অনুবাদের যাত্রা। এত আবশ্যকীয় একটি ফর্ম, যেটা ছাড়া এক ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছতই না, এরকম একটি আঙ্গিকের প্রতি কিন্তু এক ধরনের উন্নাসিকতা দেখানো হয়েছে বহু শত বছর, যদিও অনুবাদের মাধ্যমেই ইউরোপ ও আরবের সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানে রেনেসাঁর সূচনা হয়েছে। শেক্সপীয়র যে তাঁর কালজয়ী নাটকগুলো লিখেছেন, সেসবের গল্প তো সবই ইংরেজি অনুবাদেই পড়েছেন। তা সত্ত্বেও অনুবাদকে সম্ভবত ভাষার মতো একটা হাতিয়ার বা টুল হিসেবেই দেখা হয়েছে। এখন সময় এসেছে একে একটি স্বতন্ত্র, সৃজনশীল সাহিত্য আঙ্গিক হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধের মতো একটি সৃজনশীল আঙ্গিকÑপলিসিস্টেম জনরারÑযেখানে সম্মীলন ঘটে, রূপান্তর ঘটে সব আঙ্গিকের। গত শতকের মাঝামাঝি থেকে অনুবাদসাহিত্যকে কেবল মর্যাদাবান আঙ্গিকই শুধু নয়, একটি স্কলারলি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয় হিসেবেও মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে অনুবাদশিল্প কয়েক বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রিÑইংরেজি ভাষা, তুলনামূলক সাহিত্য ইত্যাদির চেয়ে বহুগুণ বড়, রমরমা একটি ইন্ডাস্ট্রি।
- আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মধ্যের পার্থক্যগুলো এবং সুবিধার দিকগুলো বিস্তারিতভাবে জানাবেন…
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : আক্ষরিক অনুবাদ বলতে কিছু নেই। অক্ষর বা শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ করলে তা হবে অপাঠ্য। যেমন বোর্হেস বলেছেন, Literal Translation is not translation. তা সত্ত্বেও অনুবাদকে আমি ভাবানুবাদ বলতে রাজি নই। অনুবাদক কখনো বাক্য ধরে ধরে, কখনো মূল টেক্সটের অর্থ ও ভাব আত্মস্থ করে অন্য ভাষায় তা রূপান্তরিত করেন। বাক্য ধরে অনুবাদ করাই তো দুরূহ, সে ক্ষেত্রে আক্ষরিক? অসম্ভব! বৃহত্তর প্রকৃতিতে, ব্রহ্মাণ্ডে, মহাজাগতিক বিশ্বে সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। সবকিছুই সর্বত্র ক্রমাগতভাবে রূপান্তরিত হয় কিংবা আরেকভাবে বলা যায় অনূদিত হয়। সাহিত্যের অনুবাদও সে ধরনের একটি অতিক্ষুদ্র রূপান্তর প্রক্রিয়া। এবং প্রকৃতিতে যেমন কোনো দুটি জিনিস আইডেন্টিক্যাল জমজ হয় না; পৃথিবীতে এতগুলো মানুষ, পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ারÑএদের কোনো দুইটি কি খুঁজে পাওয়া যাবে যারা হুবহু এক? তেমনি অনুবাদসাহিত্যেও মূল টেক্সট এবং লক্ষ্য টেক্সট কখনোই আইডেন্টিক্যাল নয়; মূল এবং অনুবাদ বড় জোর হতে পারে ফ্র্যাটার্নাল টুইন। এছাড়াও লক্ষ করবেন একটি টেক্সট যদি একাধিক অনুবাদক অনুবাদ করেন তখন ওই অনূদিত বই দুটিতে কী দারুণ পার্থক্য! এটা ঘটে কারণ দুই অনুবাদকই তাঁদের নিজস্ব রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা দক্ষতার ভিত্তিতে কাজ করেন। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনুবাদক নিজের সৃজনশীলতার পরিচয় দেন।
- আপনার হাতে অনূদিত হওয়া গ্রন্থ পাঠ করেছি, যেমনÑরাসোমন (১৯৮২), গালিভারের ভ্রমণকাহিনি (১৯৮৫); মিথের শক্তি (১৯৯৬); পেয়ারার সুবাস (২০০২); গোল্ডেন বাউ, জোবরা দ্য গ্রিক বইগুলো। নতুন কোনো কাজ করছেন কি এই মুহূর্তে?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : ফরমায়েসি কিছু লেখালেখি ছাড়াও দুটো নতুন কাজ করছি কয়েক মাস ধরে। প্রথমটি নিকোস কাজানজাকিসের ঞযব ঙফুংংবু : অ গড়ফবৎহ ঝবয়ঁবষ বা অডিসি : একটি আধুনিক উত্তরকাণ্ড আর মার্কাস অরেলিয়াসের মেডিটেশনস বা ধেয়ান। একটি বিংশ শতাব্দীর, অন্যটি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের। দুটোই ধ্রুপদী সাহিত্য এবং গ্রিক ভাষায় লেখা। অতএব আমাকে ইংরেজি অনুবাদ থেকেই বাংলা করতে হচ্ছে। অরেলিয়াসের বইটি ছাড়া-ছাড়া অনেকগুলো দার্শনিক ভাবনার সমাবেশ। এদেরকে হিতোপদেশও বলা চলে। প্রাচীন রোমের একজন দার্শনিক-সম্রাট দু-হাজার দুশো বছর আগে জীবন, জগৎ, মহাকাল, মহাবিশ্বে মানুষ আর পশুপাখির অবস্থান এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষকে কীভাবে বিশ্বচরাচরের সার্বিক প্রজ্ঞা বা নিয়ামক বা নিত্যকালের বস্তু ও ভাবজগতের মৌলিক বিধান বা লোগোস মেনে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে হবে তারই এক বিশদ পরামর্শ স্টোয়িক দর্শনের আলোকে উপস্থাপন করেছেন। সম্রাটের উন্নত দার্শনিক মননের পরিচয় বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিও আশ্চর্যরকম জটিল। ইংরেজি অনুবাদের কল্যাণেই আমি এই দার্শনিক রাজার মগজের জটিল শিরা-উপশিরা আর কানাগলিতে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারছিÑএজন্য ভালো লাগছে।
- আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক, অনুবাদ নিয়ে ওনার সঙ্গে আপনার কখনও আলোচনা হয়েছিল কি?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : আমার অগ্রজ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অনুবাদ বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাতেন না, যদিও চাইতেন তাঁর লেখাগুলো অনূদিত হোক, এবং বাংলার বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে তা পরিচিত হোক। তবে আমার করা গালিভারের ভ্রমণকাহিনি এবং পেয়ারার সুবাস পড়ে বেশ প্রশংসাই করেছিলেন বলে মনে পড়ে।
- আমরা যখন বিদেশি ভাষার সাহিত্য পাঠ করি সরাসরি সেই ভাষা থেকে তখন মূল যে সাহিত্যের রস তা আস্বাদন করি, অনুবাদের পর সেটি কতটা বদলাতে পারে?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : অনুবাদে মূল টেক্সটের সাহিত্যরস কতটুকু নষ্ট হবে, নাকি আরো বাড়বে, নাকি সমপর্যায়ে থাকবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অনুবাদকের দক্ষতার ওপর। ফ্রস্ট যেমন বলেছেন অনুবাদে কবিতা হারিয়ে যায়। কিংবা যেমন নভোকভ বলেন অনূদিত কবিতা হলো তস্তুরিতে করে কবির বিস্ফারিত চোখযুক্ত কর্তিত মস্তক পরিবেশন। কিন্তু আরো কেউ কেউ যেমন সম্ভবত অক্টাভিও পাজ বলেছেন অনুবাদের ফলে একটি নতুন কবিতার জন্ম হয়। আবার পল ভালেরি যখন ভার্জিল অনুবাদ করছিলেন তখন নাকি তাঁর মনে হচ্ছিলো যে তিনি স্বয়ং ভার্জিল হয়ে গেছেনÑসৃজনশীল প্রেরণা এতোটাই তাঁর অন্তরজুড়ে বসেছিলো। জীবনানন্দ দাশের ‘হায় চিল’ কবিতাটি ইয়েটসের ঐব জবঢ়ৎড়াবং ঃযব ঈঁৎষব-িএর সরাসরি অনুবাদ না হলেও বলা চলে ভাবানুবাদ, এবং তা কতো ঋদ্ধ! অনুবাদকের সক্ষমতার ফলে অনেক সময় একটি অনূদিত টেক্সট মূল গ্রন্থের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হতে পারে। গ্যাব্রিয়েল মার্কেস তো উচ্ছ্বাসের বশে বলেই বসলেন যে তাঁর শতবর্ষের নিঃসঙ্গতার ইংরেজি অনুবাদ ঙহব ঐঁহফৎবফ ণবধৎং ড়ভ ঝড়ষরঃঁফব স্প্যানিশ ভাষায় লেখা মূল উপন্যাসের চেয়ে বেহতর। এসব পড়ে শুনে আমার মনে হয় অনূদিত লেখাকে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র লেখা, একটি সৃজনশীল লেখা হিসেবেই পাঠ করা উচিত।
- বাংলা সাহিত্যেও অনেক রচনা রয়েছে যা বিদেশি ভাষায় অনূদিত হওয়া জরুরি, এ বিষয়ে আপনার ভাবনা কী?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : বাংলা সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ, কিন্তু অন্য ভাষা জানা বিশ্বে এর পরিচয় তেমন একটা আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্য এতটা এগিয়েছে, অথচ আর একজন বাঙালি লেখকও কি জগত সাহিত্যসভায় আলোচিত হন? রবীন্দ্রনাথও তো আজ বিশ্বসাহিত্যে দূরগ্রহের বাসিন্দা। এর একটি কারণ তো অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের বিদেশি ভাষায় অনুবাদের স্বল্পতা এবং সার্থক অনুবাদের অনুপস্থিতি। নিজেদের সাহিত্য বিশ্বদরবারে পরিচিত করতে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদের কোনো বিকল্প নেই। বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে অনুবাদ সেল গঠন করে নিয়মিতভাবে আমাদের বইগুলোকে বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে পারে। এছাড়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কোর্স তো থাকতেই পারে। পুরো একটি ট্রান্সলেশন স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিও হতে পারে অনুবাদচর্চা, অনুবাদ শিক্ষাদান এবং অনুবাদক ও দোভাষী তৈরির পীঠস্থান। চীনে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে অনেক। এছাড়াও মনে রাখতে হবে শিল্পসাহিত্যের বাইরেও এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে অনুবাদচর্চা একটি ক্রমবর্ধমান বিশাল শিল্পÑইন্ডাস্ট্রি অর্থে।
- তরুণ অনুবাদকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান?
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : তরুণ অনুবাদকদের একটা কথাই বলতে চাই যে, ভালো শিল্প ও সাহিত্যবোধ সৃষ্টিতে যেমন প্রচুর ধ্রুপদী সাহিত্য পড়তে হবে, তেমনি লক্ষ্য ভাষায় প্রকাশ সক্ষমতাও বাড়াতে হবে প্রচুর। আসলে অনুবাদ যেকোনো সাহিত্য আঙ্গিকের মতই একটি দুরূহ কাজ; এতে একটা মান অর্জন করতে গেলে সাধনা করতে হয়। বিশ্বসাহিত্যের বড় লেখকদের লেখা খুব মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা, তাঁদের প্রকাশভঙ্গি, ভাষা, সংলাপের সূক্ষ্ম ও জটিল মোচড়গুলো খেয়াল করা, এবং এভাবে নিজের উন্নত শিল্পবোধ সৃষ্টি করে লক্ষ্য ভাষায় সহজ দক্ষতা অর্জন করাÑএসব ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যে সাফল্য অর্জনের অন্য কোনো জাদুমন্ত্র আছে বলে আমার জানা নেই।