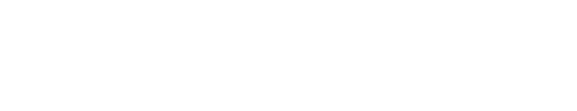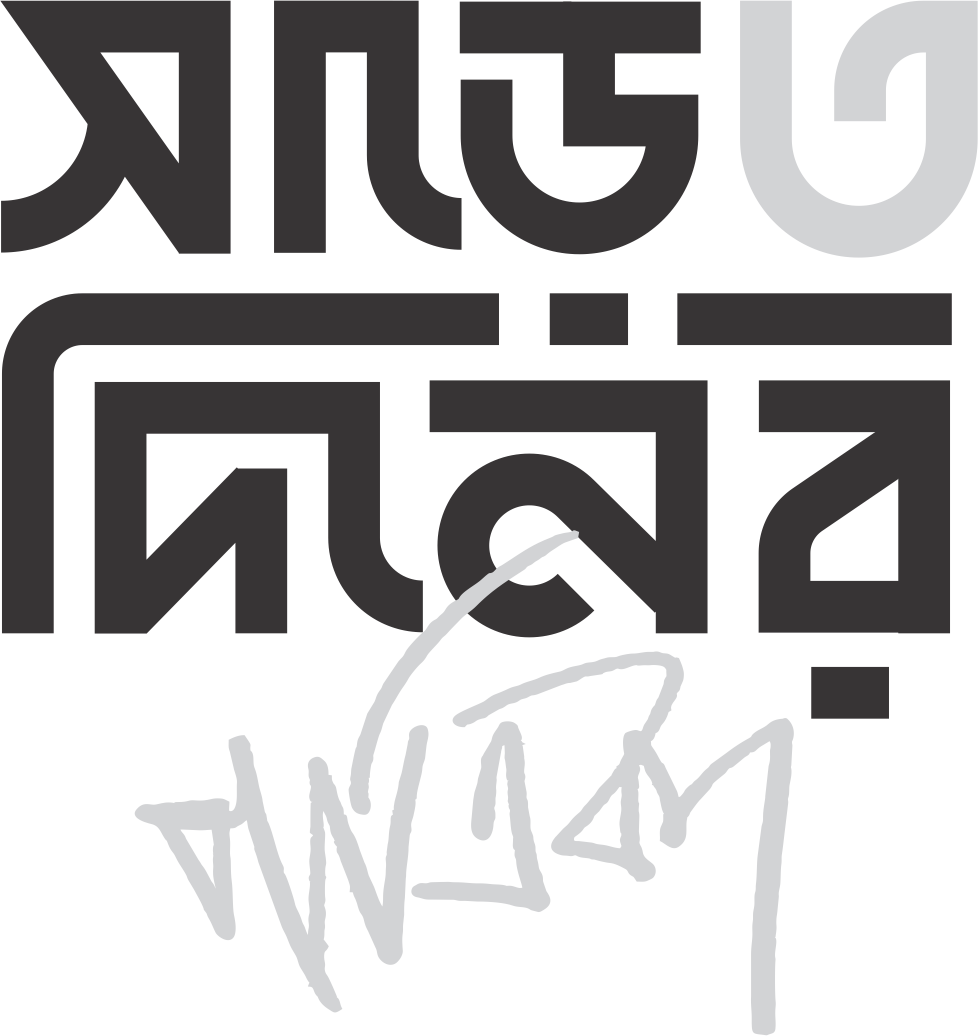রওশন জামিল জন্ম ১৯৫৮ সালে, ঢাকায়। অনুবাদক ও সাংবাদিক। সেবা প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে তাঁর অসংখ্য অনুবাদগ্রন্থ। নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা দপ্তরের অনুবাদ বিভাগে কর্মরত। কাজ করেছেন দ্য নিউ নেশন এবং সংবাদ-এ। লেখাপড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কে। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থÑ আর্নেস্ট হেমিংওয়ের দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি, যুদ্ধের মেয়েরা ও অন্যান্য গল্প । এ ছাড়া জনপ্রিয় ওয়েস্টার্ন সিরিজ ওসমান পরিবারের কল্পকাহিনি। গুণী এই অনুবাদক অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ‘সাড়ে তিন দিনের পত্রিকা’র বিশেষ আয়োজন ওয়েস্টার্ন সিরিজ সংখ্যায় বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহন করেছেনÑ এহসান হায়দার
আপনার লেখালিখির শুরুর সময় কেমন ছিল?
রওশন জামিল : আমার লেখালেখির শুরুর সময়টার কথা বলতে গেলে, আমি লেখালেখি শুরু করেছি ১৯৭৮/৭৯ তে সংবাদপত্রে লেখালেখির মধ্য দিয়ে। শুরুতে আমি খেলাধূলা বিষয়ক লেখা লিখতাম। বিভিন্ন বিদেশি পত্র-পত্রিকায় লেখা পড়তাম, মূলত উৎস সেগুলিই ছিল। আর কিছুটা সাহিত্য নিয়েও লিখেছি। যেটা ১৯৭৯/৮০র দিকে দৈনিক বার্তায় বেরিয়েছিল। কিছু ত্রিশোত্তর কবিদের উপরে, যেহেতু তখন আমি ছাত্র ছিলাম। বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়তাম সেহেতু যেসব বিষয় নিজে জানার ছিল সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। দুইটা বা তিনটা হবে। খেলাধূলার উপরে বেশকিছু কাজ করেছিলাম। পরবর্তী কালে যদি আমি ধরি শুরুটা, আসলে শুরু বলতে যেটা বোঝায় সেটা সেবা প্রকাশনীতে ১৯৮৫ সালে।
- আপনার ছেলেবেলার সময় ঢাকাশহর, ঢাকার পরিপার্শ্ব এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেমন ছিল?
রওশন জামিল : আমাদের বাড়ি ছিল পুরনো ঢাকার ঠাঁটারিবাজারে। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল শিশুসাহিত্যিক আলী ইমামের বাসা, আনিসুজ্জামান সাহেবের বাসা। বাবা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্ডহোল্ডার ছিলেন, আমাদের বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষের প্রচুর যাওয়া-আসা ছিল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদ সাবের থেকে শুরু করে অনেকেই আসতেন। আমি ছোট, সে আসরে নিষিদ্ধ ছিলাম। আমার দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত সমস্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যের বই ছিল, সেগুলো পড়তাম। আমি ছেলেবেলায় খুবই দুষ্টু ছিলাম, আমাদের বাড়িতে একটা ছোট লাইব্রেরি ছিল, শাস্তি হিসেবে সেই ঘরে আমাকে বন্দী রাখা হতো, একেবারে বাইরে থেকে তালা মেরে, খাবারের সময় হলে ঘরে কেবল খাবার দিয়ে যেত। পাশে আলমারিতে তালা দেওয়া থাকতো, সেখানে বড়দের বই ছিল, সেটি আমার জন্য মানা ছিল, ওখানে থাকতে থাকতে চাবি ছাড়া কীভাবে যেন তালা খুলতে শিখে গেলাম। শরৎচন্দ্র, বনফুল, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথসহ আরও লেখকের ক্লাসিক বইপত্র সেখানেই আমি পড়ে নিয়েছি ক্লাস ফাইভ-সিক্সে থাকতে, বুঝি বা না বুঝি তবুও গোগ্রাসে পড়ে নিয়েছি। আর আমি ভাষা শিখেছি বলবো একবাক্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়ে।
- সকলে মৌলিক লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সেদিক থেকে আপনি ভিন্ন, অনুবাদক এবং ওয়েস্টার্ন সিরিজ লেখক হিসেবে আপনার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব ভাবনা কি?
রওশন জামিল : ছেলেবেলায় স্কুলবার্ষিকীতে একটা গল্প লিখেছিলাম। অনেকেই বলেছিল আমার বাবা লিখে দিয়েছেন(বাবা নিজেও তো লেখালিখি করতেন। ১৯৬১ আদমজী পুরষ্কার যখন প্রবর্তন করা হয় তখন বাবার একটি উপন্যাস আদমজী সাহিত্য পুরষ্কার পেয়েছিল, আর তখন সমকাল পত্রিকায় ‘কাঁচপোকা ও তেলাপোকা’ নামে আরেকটি উপন্যাস ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল। ‘কালান্তর’ নামে আরেকটি উপন্যাস দৈনিক বার্তায় প্রকাশ হয় এবং ‘কাঁচপোকা ও তেলাপোকা’ পরবর্তীতে নাম পাল্টে ঢাকা ডাইজেস্টের ঈদ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।), কিন্তু সেটা ঠিক নয়Ñ গল্পটা আমিই লিখেছিলাম। গল্পটার জন্য প্রশংসাও পেয়েছিলাম। আপনি বোধহয় নাম শুনে থাকবেন ফজল করিম, উনি দৈনিক বাংলার নিউজ এডিটর ছিলেন পরে নির্বাহী সম্পাদকও হয়েছিলেন। জনকণ্ঠেও ছিলেন, উনি দেখে বলেছিলেন তোমার লেখালেখি চর্চা করা উচিত। ছাপা হওয়ার পর বাবা ওটা পড়েছিলেন প্রথমবার। পড়ে বলেছিলেন, তোর ওই বয়সে আমি এর চেয়ে দুর্দান্ত লিখতাম। আমি আসলে যখন লিখছি পুরোদস্তুর তখন আমার কিছু করার নেই। বাবা নেই তখন। আয়ের উৎস এইটিই। তখন আর কিছু করার ছিল না। আয়ের জন্য হলেও সত্য যে আমাকে এই দিকেই লক্ষ্যস্থির করতে হয়েছে। তাছাড়া আমি যখন কিছু লিখতে চেয়েছি কম ধৈর্যের কারণে মৌলিক প্লট ভাবতে পারিনি। অনেক পড়ার কারণে হলেও আমার ভাবনায় কেবলই অন্য বইয়ের কোনো না কোনো গল্প-কাঠামো এসে হাজির হয়েছে। ওটাও একটা কারণ বটে।
- আপনার লেখা প্রথম বই নিয়ে বলুন, কেমন ছিল সেই বই প্রকাশের পেছনের কথা?
রওশন জামিল : আমার প্রথম বই ‘দাগী আসামি’। এর একটা মজার ইতিহাস আছে, সেটা হচ্ছে আমি প্রথম চ্যাপ্টার লিখলাম লেখার পর উনি আমাকে বললেন তুমি মোট পাঁচটা চ্যাপ্টার লিখে নিয়ে আসো। একটা করেছি আরও চারটা লিখে আনতে বললেন। আমি লিখে নিয়ে গেলাম। উনি লাল-কালি দিয়ে রক্তাক্ত প্রান্তর করে দিলেন। সরাসরি বললেন, তোমার প্রথম চ্যাপ্টার দেখে আমি খুব আশ্বান্তিত হয়েছিলাম। পয়সা লগ্নী করে ফেলেছি, প্রচ্ছদও করে করা শেষÑএখন আমার ভয় হচ্ছে আদৌ বইটা করা যাবে কি-না। আমার কিছু ব্যবসায়ীক ¶তি হবে, তবে ব্যবসায় তো লাভ-¶তি আছেই। আমি কিছু¶ণ চুপ করে বসে রইলাম। ধাক্কাটা আমার জন্য প্রবল ছিল। আমি উনার থেকে পাণ্ডুলিপির সবটা নিলাম আর বললাম আমি নতুন করে লিখে নিয়ে আসবো। বাসায় ফিরে দুইরাত আমি ঘুমাতে পারিনি। তারপর লেখাটা কাটতে শুরু করলাম এবং ওই পাঁচ চ্যাপ্টারকে আমি তিন চ্যাপ্টারে নামিয়ে নিয়ে আসলাম কাটতে কাটতে। তারপর উনাকে আমি দিলাম আবার উনি দেখলেন এবং বললেন বাকিটা লিখে ফেলো মিয়া। আর এটাই প্রথম এবং শেষ আমার কোনো পাণ্ডুলিপি এডিট করেছেন উনি। যেটা করতেন উনি সব বইয়ের চূড়ান্তটা উনিই পড়তেন এবং প্রিন্ট অর্ডারটা উনিই দিতেন। সেবা প্রকাশনীতে বইতে ওইসময় কিন্তু ভুলের পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল। যত্ন নিয়ে বই করা হতো। এখন বেশ ভুল হয়। ভুল ছিলই না বলতে গেলে। তখন একাধিকবার দেখা হতো। ওইসময় একটা শব্দকে বদলে দেওয়ার হলে উনী জায়গাটার উপরে মার্ক করে কিছু লিখতেনÑতারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেন। আমি কখনও সেগুলো নিতাম আবার নিতামও না। একটা শব্দ অদল-বদল করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে লেখার পুরো চেহারাটাই বদলে যেত। কখনোই একটা লাইন বা বাক্যকে বদলে দেওয়া হতো না। এই জিনিসটা আমি উনার কাছে শিখেছি।
- ওয়েস্টার্ন সিরিজগুলোর বিষয়বস্তুর মূল বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের সময়ের বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের বা আউটলদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াই। কাউবয়দের ওপর নির্মিত এই উপন্যাসগুলি বিদেশি কাহিনী নির্ভর। কাউবয়, আউটল, র্যাঞ্চ, পাঞ্চার, নেস্টরসহ অনেক নতুন বিষয়ের সাথে বাঙালি পাঠকেরা পরিচিত হন। বাংলাদেশে ওয়েস্টার্ন সিরিজ পাঠকের জন্য ১৯৮৩ সালে শুরু করে সেবা প্রকাশনী, আপনি কীভাবে ওয়েস্টার্ন সিরিজের সঙ্গে যুক্ত হলেন, বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলবেন…
রওশন জামিল : ওয়েস্টার্ন সিরিজ শুরু হয়েছে কাজী মাহবুব হোসেনের ‘আলেয়ার পিছে’ বইয়ের মাধ্যমে। উনার হাত ধরে বাংলাদেশে ওয়েস্টার্ন সিরিজের শুরু হলেও এর আগে আমি করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু কাজীদা তাতে রাজী হননি। এরপর উনার পর ৮৪ সালে আমি শুরু করলাম। কাজীদাকে একসময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ওয়েস্টার্ন সিরিজটা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে। উনি বলেছিলেন, কাজী মাহবুব হোসেন হচ্ছেন বাবা এবং আমি(রওশন জামিল) হচ্ছি দাদা। তখন মাহবুব ভাইয়ের বই আমি এডিট করতাম। বিছিন্নভাবে রকিব হাসান লিখেছেন একটা বা দুইটা। আরও কয়েকজন লিখেছেন।
- আপনার লেখা ওয়েস্টার্ন সিরিজের প্রথম বইটি নিয়ে আপনার কনসেপ্ট নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল কতটা?
রওশন জামিল : আমি ভেবেছিলাম প্রথম দিকে যেভাবে সেভাবে হয়নি। কাজী সাহেবকে আমি বেশ আগেই ওয়েস্টার্ন সিরিজ শুরুর এই চিন্তার কথা জানিয়েছিলাম; কিন্তু উনী কোনোভাবে রাজী হননি। ফলে প্রথম দিকে যেভাবে ভেবেছিলাম তা আর সেভাবে হয়নি।
- স্বদেশি কথাসাহিত্য কিংবা ধরুন থৃলারÑ এই দুইয়ের বাইরে পাঠক নতুনভাবে ওয়েস্টার্ন সিরিজে ঝুঁকেছিল কেন বলে মনে হয়Ñ কেবলই কি আখ্যানের প্লটের জন্য না-কি বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি ভালোলাগা থেকে?
রওশন জামিল : তখনকার সময়ে পাঠক নতুনত্বকে নিয়েছিল। কারণ একবারে ভিন্ন ছিল সেই সময়ে ওয়েস্টার্ন উপন্যাসগুলো। নতুন চরিত্র, নতুন গল্প আর ভাষার ব্যাপারও ছিল প্রানবন্ত হওয়ার মতো। প্রচুর গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠেছিল। একেবারে রমরমা অবস্থা। ওয়েস্টার্ন সিরিজ প্রিন্ট আউট হয়ে যেত। আমি সংখ্যা দিয়ে বলতে পারবো। প্রথমে ছাপা হতো ছয় হাজার কপি। এটা অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেড়ে হয়ে গেলো বারো হাজার কপি। এবং আমি যদি ধরি একটা বই চারজন বা তার বেশি লোকে পড়ছে তাহলে সংখ্যাটা কিন্তু বেশ বড়। অবশ্যই সেবা প্রকাশনীর বই আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে রানা ছাড়া সেবা প্রকাশনীর সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক রকিব হাসান এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তিন গোয়েন্দা সিরিজটা। তারপর তো ওয়েস্টার্ন এসেছে। যারা পড়তেন তাদের সংখ্যাটা বেশ বড় বলেই আমার ধারণা।
- আপনি ঘোস্ট রাইটিং বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?
রওশন জামিল : ঘোস্ট রাইটিং, পেশাদার লেখক। এরা এককালিন অর্থ পেতেন। কাজীদা দেখলেন, মাসে দু-তিনটি বই একা লেখা সম্ভব না। ফলে ঘোস্ট রাইটার দরকার হলো। মাসুদ রানা সিরিজের জন্য এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়েছিল। আর কাজীদা কখনও টাকা কম দিতেন না। উনী নিয়মিভাবে টাকা দিয়েছেন।
- একবিংশ শতকে ওয়েস্টার্ন উপন্যাসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছু বলবেন?
রওশন জামিল : এই সময়ে এসে ওয়েস্টার্ন সিরিজ নিয়ে প্রচুর কথা শুনি। একবার ইউপিএল এবং নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির যৌথ আয়োজনে একবার অনুবাদ কর্মশালা হয়েছিল। তখন আমি সেখানে একটা সেশনে গিয়েছিলাম অতিথি হয়ে। অংশগ্রহণকারীরা বলেছে অনেকেই, বাবার কাছে শুনেছে, মায়ের কাছে শুনেছে যে, শিক্ষার্থীরা বলতো ওয়েস্টার্ন সিরিজ অনেক ভালো। এখন নূতন সময়। নূতনদের মধ্যে ওয়েস্টার্ন ওইভাবে আর পড়ার চল নেই।
- আপনার লেখা ওয়েস্টার্ন সিরিজ ‘ওসমান পরিবারের কল্পকাহিনি’ সম্পর্কে বলবেনÑ এটা অধিক জনপ্রিয় কেন হয়েছিল বলে মনে করেন আপনি?
রওশন জামিল : ওসমান পরিবারের কল্পকাহিনি জনপ্রিয় হয়েছিল কেন তা বলতে পারবো না। তবে প্রথম দিকে যখন ওয়েস্টার্ন লিখতে শুরু করি তখন প্রচুর সমালোচনা এসেছে। চাপ তৈরি হয়েছে। ভাষা নিয়ে কথা শুনতে হয়েছে। চিঠিপত্রও পেয়েছি অনেক, আবার অনেক গালমন্দও শুনেছি তখন। কারণ আমি যেটা চাইতাম তা হচ্ছে ওই ধারাটা বাংলার এবং বাঙালীর মানুষের যে গঠনটা তার মধ্যে মিলিয়ে দিতে। ফলে দুই একজন গালমন্দ করতো। আমি যখন লিখেছি, মা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো তখন সেগুলো নিয়ে গালাগাল হতো। বলতো, হিন্দুয়ানী বাংলা এসব। বিরোধীতা করেছিল গল্প নিয়ে, লিখেছিলÑ‘ফাইজলামি করেন’। এছাড়া আরও অকথ্য ভাষায় লিখেছিল, কাজীদা কিছু চিঠির উত্তর দিয়েছিল কড়াভাবে, বাকিটা আর দেননি। ওসমান পরিবারের কাহিনি প্লট ভেবেছিলাম চট্টগ্রাম নিয়ে। আর নাম কি হবে তা নিয়ে ভাবতে বেশ সময় চলে গিয়েছিল। আমি এনসাইক্লোপিডিয়ার নেইম পার্টে গিয়ে খুঁজেছি এমন নাম যা সবখানে যায়। যার দুটো ভূমির আলাদা রূপ। ওসমান ছিল তেমন। ফলে ওটাই বাছাই করি। তারপর বইটা ছাপা হওয়ার পর খুব ভালোভাবে নিলো পাঠক। কাজীদা প্রংশসা করলেন।
- আপনি যখন কোনো একটা ওয়েস্টার্ন আখ্যানের প্লট ভাবেন বা নির্বাচন করেন, তখন কোন কোন বিষয়গুলিতে খেয়াল রাখেন?
রওশন জামিল : আমি কখনও মূল কাঠামো থেকে সরতে চাই না। আমি ভাবি গল্পটা ভিন্ন হওয়া দরকার। কাজীদার থেকে একটা বিষয় শুনেছি খুব খেয়াল করে, উনী বলতেনÑ একটা কথা মনে রাখবে, তা হলো তুমি যদি পাঠকের চোখের জল ফেলে দিতে পারো পড়তে পড়তে, তবে তুমি হৃদয়ে জায়গা করে নিলে। পাঠক তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমি সেই কাজটিই করতে চেষ্টা করেছি।
আপনি সাংবাদিক, লেখকÑ লেখালিখি ছেড়ে দীর্ঘসময় আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাস করেছেন, চাকরি করেছেনÑ ওইসময়টা বলবেন?
রওশন জামিল : আমি আমেরিকা যাওয়ার পর আমি জানতাম না দেশে কী হচ্ছে, আবার এভাবেও বলা যায় দেশে যোগাযোগ একদমই হতো না বললেই চলে। কর্মব্যস্ততার জন্যও লেখারও সময় পেতাম না। আর দ্বিতীয়ত, সেখানকার স্থানীয় লাইব্রেরির মধ্যে আমি ওয়েস্টার্ন বই পেতাম না। ওদের লাইব্রেরি প্রচুর রীচ কিন্তু পাঠক-রুচির উপর সবকিছু নির্ভর করে তো হয়। মনে হতো ওই ধারার কেউ পড়ছে না ওখানে। এভাবে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তারপর ২০১২ বা ২০১৩ সালের দিকে ফেসবুকে রাজীব নূরের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং উনি মূলত তাগাদা দিয়ে নূতন একটা বই বের করে নেন। এরপরে তো আর আমি ওয়েস্টার্নে ছিলাম না। লাস্ট সেবা থেকে আরেকটা বই প্রকাশিত হলো। এরপর আমার আর ওয়েস্টার্নের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। আমার পাঠরুচি বদলে গেছে। এখন একটু সিরিয়াস উপন্যাসের দিকে ঝোঁক হয়েছে। এরপর আমি আমেরিকায় থাকতে দুটো গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছি। একটা চিনুয়া আচেবের বই, আরেকটা মুরাকামির বই। মুরাকামির উপন্যাস আমি বেশ মজা পেয়েছিলাম তারপর দেখলাম সবকিছু কাছাকাছির যারজন্য আমি আর মজা পেলাম না।
একুশে বইমেলায় যান এখন?
রওশন জামিল : না, নূতন বই থাকে নাÑ সে কারণে যাওয়া হয় না।
- তরুণদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চানÑ যারা এখন ওয়েস্টার্ন উপন্যাস লিখতে চান?
রওশন জামিল : সত্যিটা হলো এখন ওয়েস্টার্ন নতুনভাবে হওয়ার সুযোগ নেই। আগের দিনে যেভাবে ছিল সেটা এখন হওয়ার সুযোগ কোথায়? আগের বইগুলোর মতো এখন তো অবস্থা নেই। বেঙ্গল বুকস নতুনভাবে বাজারে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে ওয়েস্টার্ন সিরিজ। এটা ভালো একটা দিক। পুরনো পাঠকেরাই এখনও আগ্রহী।
এখন এক মুহূর্তে তরুনেরা সব পেয়ে যাচ্ছে। কাল যে বইটা হাতে পাচ্ছেন আপনি, সেটি হয়তো মুভিতে চলে এসেছে। তাই নতুন কি রয়েছে তা নিয়ে একালে অতোটা ভাবনার সুযোগ নেই। ভাষার বিষয়টা খুব জরুরি। প্রচুর পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি, এরইমধ্যে দিয়ে ভাষা তৈরি হয়। ফলে গোগ্রাসে গিলে ফেলার প্রবণতা তৈরি করতে হবে।