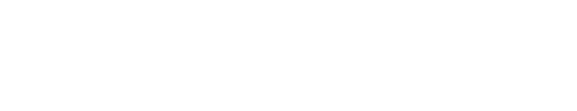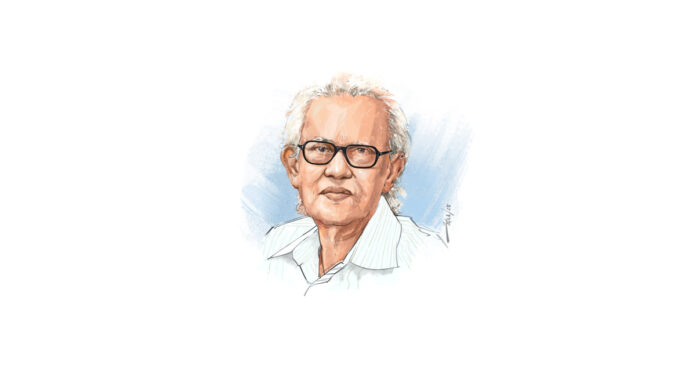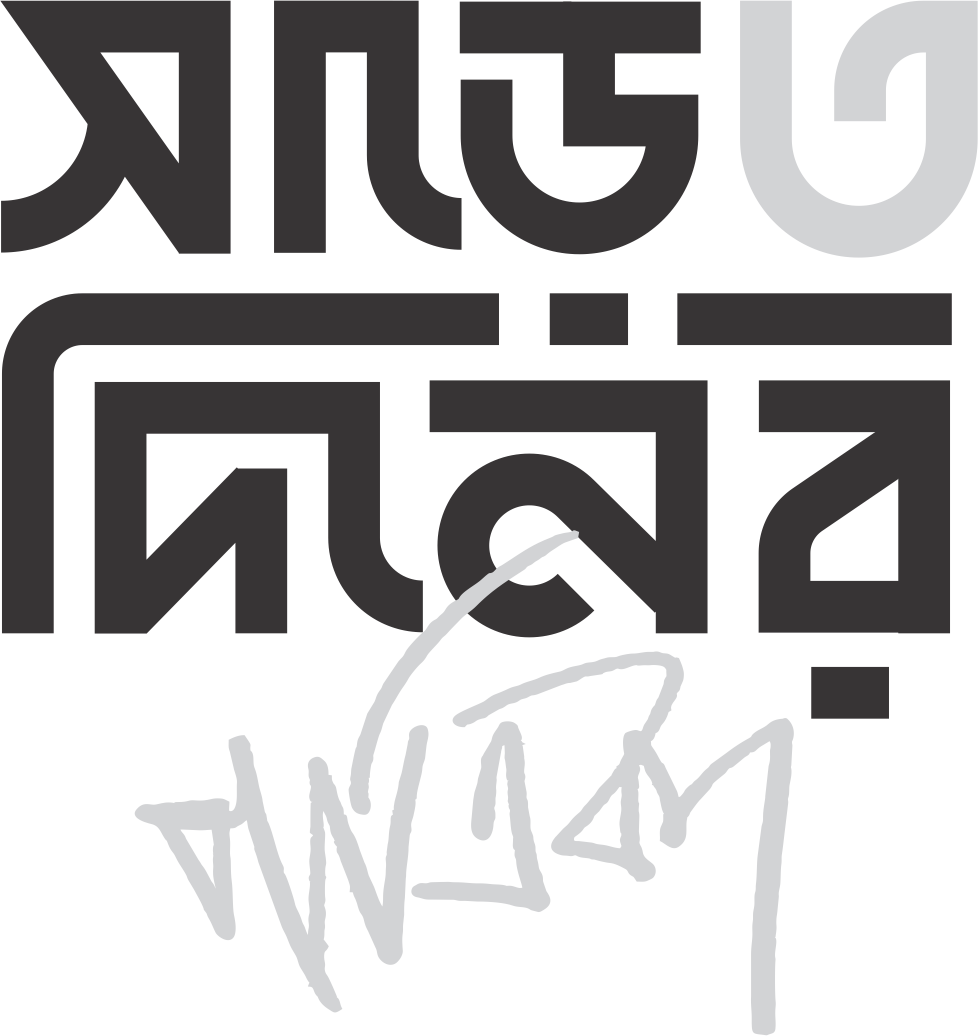ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার সময় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথকে মর্মে ধারণ করেন, রবীন্দ্রচর্চার জন্য তিনি পেয়েছেন ‘রবীন্দ্রাচার্য’ উপাধি। একজন মুক্তমনা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। ছাত্রজীবন শেষে প্রতিবাদী এই মানুষটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন নিজেকে। সমাজ প্রগতির সংগ্রামে কখনো থেমে থাকেননি তিনি; বাংলা ভাষার জন্য যেমন সংগ্রাম করেছেন, তেমনি স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছেন আজও। ভাষা আন্দোলনের নতুন নতুন দিকগুলো তিনি ব্যাখ্যা করেছেন চমৎকাররূপে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, রাষ্ট্রভাষার লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি ভাবনা, রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প প্রভৃতি আহমদ রফিকের প্রকাশিত গ্রন্থ। সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার জন্য তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এহসান হায়দার
- ভাষা আন্দোলনের সময়ে আপনি কীভাবে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন?
আহমদ রফিক : আমি ছেলেবেলা থেকেই রাজনীতিসচেতন ছিলাম, যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকে প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তখনকার দিনে যারা ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন তারা ছিলেন আদর্শিক, নিজের স্বার্থে তাদের রাজনীতি ছিল না। তখনকার মানুষের মাঝে দেশপ্রেম ছিল, সততা ছিল, অনুকরণীয় ছাত্ররাজনীতি মানেই আদর্শের জায়গা। স্কুল ও কলেজ জীবনে প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে আমি মেডিকেল কলেজে এসেও একইভাবে ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছিলাম। ফলে যখন ভাষার প্রশ্ন তৈরি হলো, তখন নিজে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির আড্ডা ছিলÑতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল; সেই সকল আড্ডাতেও আমি যুক্ত ছিলাম। মেডিকেল কলেজের হলে পোস্টার ও লিফলেট দিয়ে ছাত্র জনমত তৈরির কাজে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত ছিলাম। ওই সময়ে প্রতিটি মিছিল, সভা-সমাবেশে অংশ নিয়েছি। ৩১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভাতেও উপস্থিত ছিলাম। আমি বলব, সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনের সময় আমি মেডিকেল কলেজে একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলাম।
- সাতচল্লিশে ভারত ভাগ হলে নতুন দেশ পাকিস্তানে বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষের সূচনার দিকটি ঠিক কীভাবে শুরু হয়েছিল?
আহমদ রফিক : ভাষা আন্দোলনের সূচনা মূলত পাকিস্তান জন্মের পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছিল; কিন্তু এ প্রক্রিয়া চলছিল পাকিস্তান হওয়ার আগে থেকেই। এ প্রসঙ্গে আমি সব সময়ই বলি, বাঙালি মুসলমান পশ্চাদপদ থাকার কারণে তারা ১৯৪৬ সালে চোখ বন্ধ করে মুসলিম লীগের বাক্সে পাকিস্তান হওয়ার পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই হলো অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত করা, বঙ্গভাগ এগুলোর জন্য দায়ী। মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হলেও এর কেন্দ্রীয় দলগত প্রাধান্য ছিল উর্দুভাষীদের হাতে। এমনকি প্রভাবশালী বাঙালি মুসলমান এ কে ফজলুল হক সাহেব চেষ্টা করেও মুসলিম লীগের হাই কমান্ডে ঢুকতে পারেননি, পরে জিন্নাহ কর্তৃক তিনি বহিষ্কৃতও হন সদস্য পদ থেকে। এমন অবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সহিংসতাÑএগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই দেশভাগ নিশ্চিত হয়। তখন ১৭ মে ১৯৪৭, উত্তরপ্রদেশের একজন খ্যাতনামা মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান বলেনÑ পাকিস্তান হতে যাচ্ছে, আর যার রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। ওই সময়ে বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান নিয়ে এতটাই আচ্ছন্ন ছিল যে, কেউ কোনো কথা বলেনি। সেই সময়ে ‘ইত্তেহাদ’ সংবাদপত্রে যারা কাজ করতেন, তারা ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালি মুসলমান; তাদের কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। সামান্য নিঃসঙ্গ কণ্ঠস্বর বলা চলেÑআবদুল হক সাহেব, মাহমুদুল হক জাহেদী প্রমুখ ‘আজাদ’ এবং ‘ইত্তেহাদ’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রতিবাদ করলেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গণ আজাদী লীগ, যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিস বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলতে শুরু করে। এ সময় সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাÑ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ডাক, রেলসহ বিভিন্ন কাগজপত্রে উর্দু ভাষার ব্যবহার শুরু করে। তখন এর প্রতিবাদ করেছিল তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীরা।
- ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পর্যায় সম্পর্কে বলবেন কি?
আহমদ রফিক : ১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছিলেনÑভারত চিন্তা করছে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য, সে হিসেবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু। তখন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব, এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লিখলেন। এই সময়কে অনেকে ভাষা আন্দোলন বলেনÑআমি বলি না, আমি বলিÑএটা ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পর্যায়। ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পর্যায় বলছি, কারণÑশুরুতে বাঙালিরা মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করেছেন, লিখে প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু আন্দোলন করেননি, রাজপথে নামেননি, স্লোগান দেননি। এর ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই সেপ্টেম্বর মাসে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিস একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেÑ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা’। সেখানে ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, ড. আবুল কাশেম প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে ‘কৃষ্টি’ নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ওই পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই ব্যাপারগুলোও আমার কাছে ওই তাত্ত্বিক পর্যায়েরই অংশ।
- ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক যাত্রা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল?
আহমদ রফিক : ভাষা আন্দোলন সাংগঠনিকভাবে শুরু হলো ১৯৪৮ সালে। ভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে যে আন্দোলন রাজপথে সংগঠিত হয়, তা ছিল মূলত ছাত্রদের। সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানের গণপরিষদে। প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটা প্রস্তাব তুলেছিলেনÑগণপরিষদে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করবেন আর ব্যবহারিক ভাষা উর্দু এবং ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা গ্রহণ করা হোক।
- ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা ছিলÑসেটির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?
আহমদ রফিক : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অর্থ শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা নয়; বাঙালি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। সেই অধিকার আদায়ের চিন্তাগুলো এর সঙ্গে জড়িত ছিল। সামগ্রিকভাবে এই তাত্ত্বিক কথার বিচার করলে দেখা যাবেÑযেহেতু রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক স্বার্থরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেহেতু শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না ৫২’র আন্দোলন।
আপনারা একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে কেন প্রতিবাদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন?
আহমদ রফিক : ২১ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিবাদের সিদ্ধান্তের কারণ হলোÑ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম বাজেট অধিবেশনের দিন। উদ্দেশ্য ছিল বাজেট অধিবেশন ঘেরাও করা। এখন যেটা জগন্নাথ হল, সেটা ছিল পরিষদ ভবন। এখানে পরিষদ সদস্যদেরকে ঘেরাও করে ওই প্রস্তাব যেন তারা নেন এবং গণপরিষদে পাস করে এই দায়িত্বটুকু তারা পালন করেন এই বিষয়ে তাদের দিয়ে মুচলেকা নেওয়া।
- ২১ ফেব্রুয়ারির সকালবেলা থেকে সারাদিনে কী কী ঘটেছিল?
আহমদ রফিক : ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ছাত্রসভা হলো, সেখানে ইডেন কলেজ ও কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরা পর্যন্ত অংশ নিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা-সহ সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধি ছিল। বাইরের রাস্তায় খাকি হাফপ্যান্ট পরা পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুড়ল, লাঠিপেটাও হলো অনেক। এরই মধ্যে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য ছাত্রদের মিছিল ব্যাচ হিসেবে বেরোল। ছাত্রছাত্রীদের আলাদা আলাদা খণ্ড খণ্ড দল বের হচ্ছিল, সেখানেও লাঠিপেটা হলো, গ্রেফতারও হলো অনেক। আমার অনেক বন্ধু, যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজের আলি আজমল, ফজলুল হক হলের আনোয়ারুল হক খানÑএরকম আরো বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হলেন। হাবিবুর রহমান শেলী পরে বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনিও গ্রেফতার হলেন।
এই পরিস্থিতিতে সবার একটাই লক্ষ্য ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণটা তখন বিশাল আয়তনের। এখন যেখানে নার্সেস কোয়ার্টার, আউটডোর, তখন সেখানে বিরাট বিরাট ছাউনি ছিল, আমরা বলতাম মেডিকেল ব্যারাক। সেখান থেকে জগন্নাথ হল তো ১০০ গজ দূরে, সুতরাং সবচেয়ে কাছের জায়গাটিতে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই উদ্দেশ্যেই সবাই চেষ্টা করেছে, কেউ রেললাইনের পেছন দিয়ে, কেউ মাঝখানের পাঁচিল ডিঙিয়ে, কেউ পাঁচিলের ইট খুলেÑআমিও ওই পথ দিয়ে গেলাম। বাইরের রাস্তা দিয়ে পুলিশের লাঠির পিটুনিকে উপেক্ষা করে দুপুর ১২টা নাগাদ বেশ ভালোই জমায়েত হলো। পুলিশ তখন তাদের ব্যারিকেড সরিয়ে আমাদের ফুলার রোডে অর্থাৎ সেক্রেটারি রোডে নিয়ে এলো। বেশ শক্ত করেই ব্যারিকেড দিলো, যাতে জগন্নাথ হলের দিকে যেতে না পারে এই জমায়েত থেকে কেউ। এই অবস্থায় যত বেলা গড়াচ্ছিল, ততই সাধারণ মানুষ যোগ দিচ্ছিল। তা না হলে কী করে সালাম এখানে গুলিবিদ্ধ হলেনÑসচিবালয়ের পিয়ন, ময়মনসিংয়ের গফরগাঁওয়ের মানুষ আবদুল জব্বার গুলিবিদ্ধ হলেন?
- শহিদ মিনার তৈরি হলো কখন?
আহমদ রফিক : এই লাল-কালোর সমাহারে ঢাকা সেদিন প্রতিবাদের শহর। মিছিলের শহর। সেদিন ছাত্র আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হলো। যখন সাধারণ মানুষ শুনতে পেল ঢাকায় সাধারণ ছাত্রদের পুলিশ গুলি করে মেরেছে, তখন সারাদেশের মানুষ জাগলো, আন্দোলন বেগবান হলো। এইভাবে আন্দোলন চলল গোটা ফেব্রুয়ারি মাস। এর মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল, সেটা হলো শহিদ মিনার তৈরি। ওই যে দ্বিতীয় দিনে একটা আলাদা স্লোগান তৈরি হয়েছিল, সেটা ছিল ‘শহিদ স্মৃতি অমর হোক’। এই স্লোগানের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে, আমাদের বন্ধুবান্ধবরা এমনি কথা প্রসঙ্গে (এটা কাকতালীয়ও বলা যায়) বললেনÑশহিদস্মৃতি অমর করতে, একটা শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলে কেমন হয়? শহিদ মিনার নয়, তখন কথাটা ছিল ‘শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ’। ২৩ তারিখ রাত, এই এক রাতের শ্রমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে এবং সেখানকার ছাত্রদের চেষ্টায় আবুল বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়া রক্তমাখা স্থানটিতে ১০ ফুট উঁচু, ৬ ফুট চওড়া একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হলো, দু’জন রাজমিস্ত্রির সহায়তা নিয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমা ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে। এই সিমেন্ট সরবরাহে সহায়তা করেছিলেন আমাদের কলেজের সম্প্রসারণ কাজের সাব-কন্ট্রাক্টর, হোসেনি দালানের পিয়ারী সরদার। তার কাছ থেকে চাবি এনে গোডাউন থেকে হাসপাতালের স্ট্রেচারে করে সিমেন্ট এবং বালু হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে হোস্টেল প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হলো। কারফিউয়ের মধ্যে, পুলিশি টহলের মধ্যে রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে একটি শহিদ স্তম্ভ তৈরি করা হলো। সেই সময়ের রেপ্লিকাটি আমার কাছে রয়েছে। পরদিন রবিবার ২৪ তারিখ, সরকারি ছুটির দিন। সেই দিন থেকে শুরু করে সারাক্ষণ ঢাকার মানুষ এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কেউ ফুল দিয়ে, কেউ টাকাপয়সা দিয়ে, কেউ অলঙ্কার দিয়ে।
- এই আন্দোলনের ফলে আমাদের প্রগাঢ় ভাষাপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে আমরা পেলাম শহিদ দিবস আর শহিদ মিনার…
আহমদ রফিক : আমরা কী পেয়েছি? পেয়েছি দু’টি প্রতীক। প্রথমত, একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস, প্রতিবাদ দিবস বা ভাষা দিবস যা-ই বলি। দ্বিতীয়ত, শহিদ মিনার, এটা প্রতিবাদ-আন্দোলনের একটি প্রতীক।
- ভাষা আন্দোলনের ফলাফল যদি বলতে চাইÑআন্দোলনের পূর্বে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে পাকিস্তানি চেতনাটাই ছিল প্রধান। আমাদের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কি একুশে ফেব্রুয়ারির পর একটা নতুন চেতনা জাগ্রত হলো তখন?
আহমদ রফিক : এই আন্দোলনের পরে দেখা গেল, রাজনীতি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এ আন্দোলনের প্রভাবে একটি বাঁক ফেরা পরিবর্তন। পরিবর্তন দুই দিকেÑরাজনীতিক বিচারে দুই ধারায়, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা, সঙ্গে প্রগতিশীল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তা। এই দুই ধারায় পরিবর্তন, যেটা পাকিস্তানি কনসেপ্টের পুরোপুরি বিরোধী। এই দুটোর পরিপ্রেক্ষিতেই ভাষা আন্দোলনের যত তাৎপর্য বলি আর তার প্রতিক্রিয়া বা তার ফলাফল বিশ্লেষণ করিÑএগুলো একুশের মাধ্যমে হয়েছে। তিনটি স্লোগান আমরা ২১ তারিখ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মিছিলে মিছিলে দিয়েছিÑ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, সর্বস্তরে বাংলা চালু কর’। আমাদের রাজনীতিক নেতারা সবাই স্বীকার করেনÑভাষা আন্দোলন আমাদের নতুন রাষ্ট্রের সূতিকাগার।