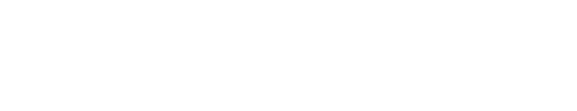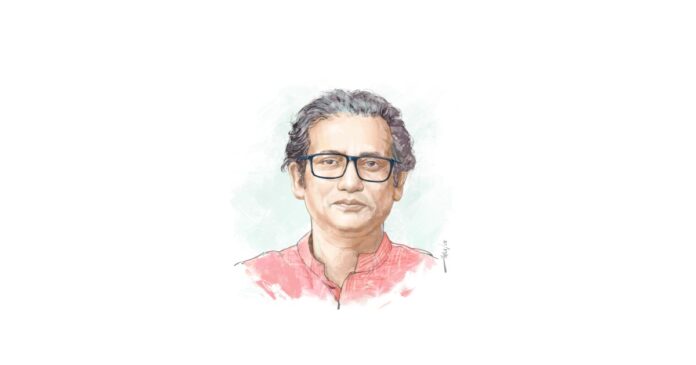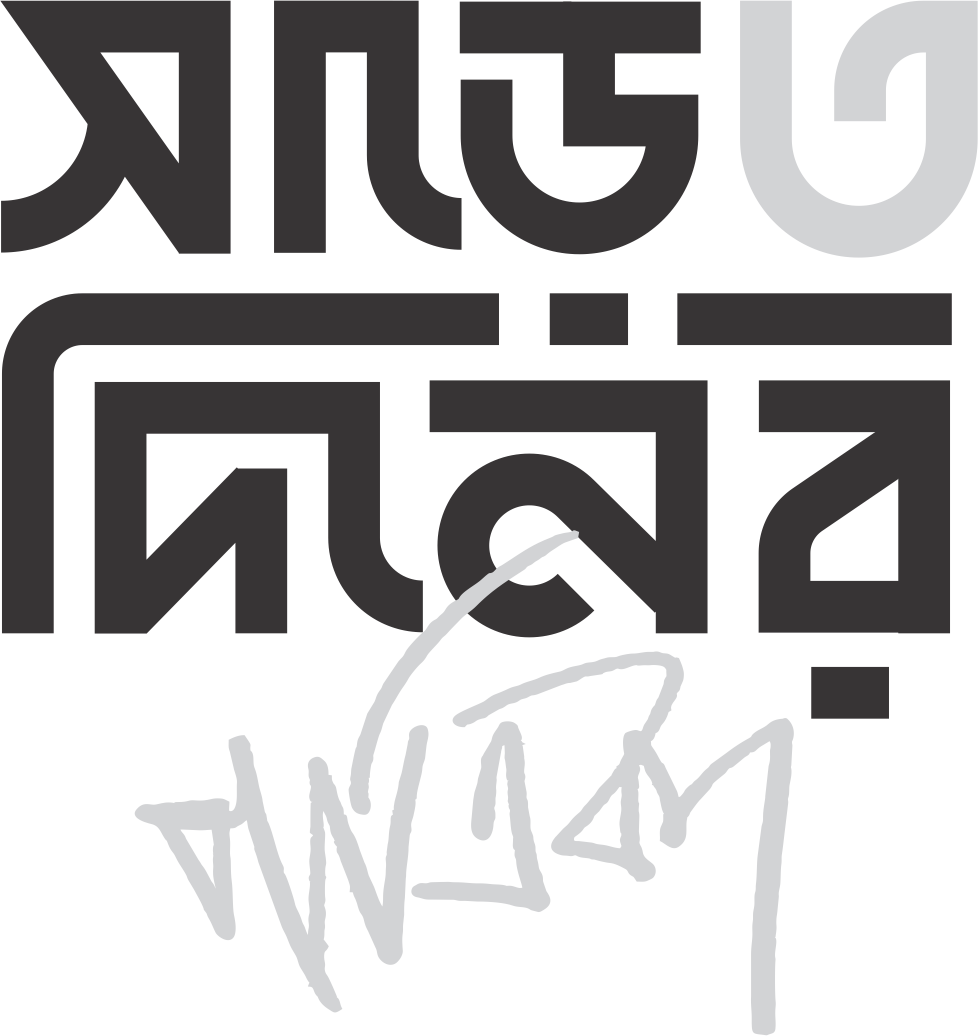আ-আল মামুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ—সিনেমার সাংস্কৃতিক রাজনীতি, অনূদিত গ্রন্থ—সম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি (নোয়াম চমস্কি, এডওয়ার্ড এস. হারম্যান), মানবপ্রকৃতি : ন্যায়নিষ্ঠা বনাম ক্ষমতা (নোয়াম চমস্কি এবং মিশেল ফুকোর আলাপচারিতা)। যৌথভাবে যোগাযোগ পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি আধিপত্যবিরোধী চিন্তা ও কাজে সক্রিয়। সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার জন্য এই লেখকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এহসান হায়দার
- চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী?
আ-আল মামুন : নিঃসন্দেহে চিত্রনাট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বেশ কিছু রিসার্চের কাজে সিনেমার পরিচালক, প্রযোজকের সাথে কথা বলেছিলাম, তখন তারা বলেছিল-ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটারের খুব অভাব। বাংলাদেশে আমার মনে হয় গল্প বলার চলটা কম, নতুন গল্প তৈরি করা, চর্চা করার অভ্যাস নেই। এখানে কল্পনার জগত খুবই শক্তিশালী হতে হয়। ভিজ্যুয়ালে স্টোরি টেলিং যেমন গুরুত্ব রাখে, ঠিক তেমনি গুরুত্ব রাখে ন্যারেটিভ, ন্যারেটিভের ফিকশন এগুলো। এখানে বেশ কিছু শক্তিশালী লেখক তৈরি হয়েছে, কিন্তু এর বাইরে আর কিছু নাই। বইমেলাতে যেসব বই প্রকাশিত হয়, সেগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য বই দুই থেকে তিনটার বেশি পাবেন না। এটা বড় ধরনের একটা সংকট, আমার মনে হয়Ñআমাদের জাতিসত্ত্বার যে প্রধান সংকট তার সাথে এটা যুক্ত করা যায়। আমরা যে সংস্কৃতির চর্চা করে এসেছি, জীবনঘনিষ্ঠ না হয়ে, তা কেবল কৃত্রিম একটা কল্পনার বিষয় হয়ে থেকেছে। এখন যে গল্পগুলো নিয়ে সিনেমা তৈরি হচ্ছে তা আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসে না, বরং তা একধরনের ধার করা। ধার করা মোটিফ, ধার করা কল্পনা, ধার করা চিন্তা। যে কারণে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় যাপনের সাথে তার উপভোগ্য সংস্কৃতির বিপুল পার্থক্য থেকে যায়। এর একটা কারণ এখানে স্টোরি টেলিংয়ের জার্নিটা ঠিকঠাক মতো হয়নি। আমি ঠিক জানি না, উনিশ শতকের আগে ঠিক কেমন ছিল, তবে উনিশ শতকের পর দেখব যে আমাদের দেশের বিশেষত বাঙালি মুসলমানরা আর গল্প বলতে পারছেন না, গল্পের মধ্যেও তারা নাই। এখানে একটা বিশাল পার্থক্য থেকে গেছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য, বাংলাদেশে যদি সব ধরনের মানুষের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে চাইÑযে আমি ধারণ করছি একটা রাষ্ট্রকে, তাহলে অবশ্যই সেটা শুরু হোক লেখালেখির মাধ্যমে, ভিজ্যুয়াল হোক, গল্প বলা হোক। গণ-অভ্যুত্থানের পরে আমরা যদি দেখি, আমাদের চর্চিত এতদিনের সো-কল্ড ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ বড় ধরনের হোঁচট খেয়েছে। তাই নতুন গল্প বলার জন্য একটা খালি জায়গা তৈরি হয়ে আছে এখন। নতুন লেখক, পরিচালক, স্টোরি টেলারদের জন্য এটা একটা ভালো সুযোগ। নতুন গল্প হাজির করা এখন খুব জরুরিও বটে। আশি-নব্বই দশকের গল্পগুলো আমাদের সাথে এখন আর সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারছে না। আবার এখনকার সময়ের চিন্তাভাবনা, গল্পের মাঝে বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে, গল্পের মাঝে টুইস্ট এবং টানটান উত্তেজনা এসব থাকতে হলে প্রচুর চর্চার প্রয়োজন। এই চর্চাটা আমাদের নেই, প্রবল অস্থির এক জাতি আমরা। তবে আমি আশাবাদী যে, এখন প্রচুর বিকল্প পদ্ধতি আছে। একটা মোবাইল ফোন দিয়ে চাইলে একটা সিনেমা তৈরি করা যায়, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আছে, ইউটিউবে চ্যানেল তৈরি করে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এই যে স্টোরি টেলিংয়ের নতুন একটি ধারা তৈরি হয়েছেÑআগে যেটা পাবলিশার ছাড়া সম্ভব ছিল নাÑতা এখন খুব সহজেই দর্শকের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে। আমরা হয়তো এক নতুন সময়ের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমরা নিজেদের গল্প বলতে সাহসী হয়ে উঠছি।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, চলচ্চিত্র নির্মাতা তার চিত্রনাট্য নিজে লেখেন না; পরিচালক একজন চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে তখন চুক্তি করেন, লেখককে হয়তো বিষয় বলা হলো কিংবা গল্প পছন্দ থাকলে গল্প বলে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সংকটও তৈরি হয়, এর সমাধান কীভাবে সম্ভব?
মামুন : ইউরোপ-আমেরিকাতে স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য এজেন্সি আছে, এটা একটা ভালো দিক। তারা গল্প বাছাই করছে, দক্ষ লেখক আছেন যারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন, এগুলো অন্যান্য দেশে ঘটছে। এই বিষয়ে তারা বেশ পেশাদার। তবে একটা খারাপ দিকও আছেÑট্রেন্ড, ধরাবাঁধা একটা কল্পনার ভেতরে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে ফিল্ম আর্কাইভ, জাতীয় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং দেয়, এদের থেকে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সব জায়গায় ফিল্ম ডিপার্টমেন্টগুলোতে স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে ফোকাস করা, আমার মনে হয় জরুরি। হলিউডে একটা সিনেমার সব কিছু প্রস্তুত করার পর তারা একজন পরিচালককে নিয়োগ করে, সিনেমার কিছু কাজ সম্পন্ন হবার পর পরিচালক ও প্রযোজকের মধ্যে কোনো কারণে বনিবনা হলো না, তখন সে জায়গায় অন্য আরেকজনকে নিয়োগ করা হয়। আমাদের দেশে এমনটাই হতে হবে আমি সেটা বলছি না। আমি সম্প্রতি যেটা খেয়াল করেছিÑসিনেমা তৈরিতে আমাদের বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে, ভিজ্যুয়াল স্টোরি টেলিংয়ের যে বিষয়টি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার তারা বেশ ভালো করছে; কলকাতা, মুম্বাই এদের সাথে তুলনা করা যায়। সাউন্ডের কাজ, পোস্ট প্রডাকশনের কাজ করছে দেশে বসে, দশ বছর আগেও সেটা সম্ভব ছিল না। গল্পের যেহেতু খুব দরকার, সেজন্য বাংলা একাডেমি থেকে শুরু করে নানান জায়গায় আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি। যেমনÑবাংলা একাডেমিতে অনেকদিন আগে ‘তরুণ লেখক প্রকল্প’ নামে একটি প্রকল্প ছিল। সেখানে বিশজন লেখক ছিল, এর মধ্যে অনেকেই অন্য পেশায় চলে গেছে, আর লেখালেখি করে না; কিন্তু ওই সময় বাংলা একাডেমি থেকে বিশটা বই প্রকাশিত হয়েছে। অন্তত তাদের মধ্যে পাঁচ-সাতজন শক্তিশালী গল্পকার আমরা পেয়েছিলাম। তাহলে এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি মিলে যায়, তাহলে আমরা হয়তো স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ের সংকট থেকে বের হয়ে আসতে পারব।
কলকাতার ওটিটি কন্টেন্ট মেকার আর বাংলাদেশের ওটিটি কন্টেন্ট মেকারের সাথে তুলনা করিÑকলকাতায় আধুনিকতা আগে এসেছে; গল্প, সিনেমা সব আগে এসেছে। অনেক ভালো ভালো গল্পও তৈরি হয়েছে, ভালো সাহিত্যিক, ভালো পরিচালক পেয়েছে। কিন্তু এখন কী হচ্ছে, ওদের সিনেমায় খেয়াল করবেনÑপুরনো সেই কথা, সেই সেট ডিজাইন, সেই প্রপসের বাইরে তারা আসতে পারেনি। শুধু হইচই ওটিটি যদি খেয়াল করেনÑদেখবেন কলকাতার দুই-তিনটি গল্প হয়তো উতরে গেছে; কিন্তু বাকিগুলো সব একই ধাঁচের, সেই আগের দৃশ্যপট। অন্যদিকে, আমাদের দেশের কাজগুলো দেখেন, প্রতিটি গল্পই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও খুব প্রশংসিত হয়েছে। ফলে গল্প বলার চর্চা শুরু হলে, আরো বেশি সুন্দর কাজ উপহার দেওয়া সম্ভব। তাই এখন স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে আরো বেশি উৎসাহিত করা উচিত, ইন্ডাস্ট্রিটা আরো বেশি পেশাদার হয়ে উঠবে তখন।
- শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র এদেশে একেবারে হয় না বললেই চলে; যারা এখন অব্দি কাজ করেছেন কিছু, তাদের গল্প নির্বাচন আর চিত্রনাট্য নির্মাণও আকর্ষণীয় নয়, এর পেছনের সংকট কোথায় বলে মনে করেন?
মামুন : আমাদের এখানে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি থেকে আট-নয়বার ফেস্টিভ্যাল হলো, কিছু কাজ আমি দেখেছিলামÑআমার কাছে ম্যাচিউর মনে হয়নি। কারণ হচ্ছেÑশিশুকে আমাদের সমাজ কীভাবে দেখে? আপনি খেয়াল করে দেখবেনÑএকটা শিশু রাস্তা পার হবে, কোনো গাড়ি দাঁড়াবে না, একটা বাচ্চা দোকানে কিছু একটা কিনতে গিয়েছে, সেখানে সবাই দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে, বাচ্চাটিকে দেখেও দেখবে না এবং তারা যে আজেবাজে রসাত্মক গল্প করছে সে বিষয়ে সতর্ক হবে না। সহানুভূতি, সমবেদনা নেইÑআমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কীভাবে গড়ে উঠবে? এই যে কল্পনাগুলো কিংবা দায়িত্বশীলতা নিয়ে আমাদের ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টিকে ভাবা দরকার। এদিক দিয়ে আমরা চরমভাবে ব্যর্থ।
আরও অদ্ভুত ব্যাপারÑপাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে কিন্তু দুটো বাচ্চা কথা বলে না, কিংবা বাড়ির লোকজন কথা বলতে দেয় না। রাস্তায় একটা শিশু আরেকটা শিশুকে জড়িয়ে ধরে না। রাস্তায় যখন বাচ্চারা হেঁটে যায় আমরা কেউ তাকে উদ্দেশ করে ‘হ্যালো’ বলি না। সামাজিকভাবে তাদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বাচ্চাদের মা-বাবা এত বেশি গুরুত্ব দেয় যে বাচ্চাকে নার্সিসিস্ট করে গড়ে তোলে। সমাজ যে একটা বাচ্চাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেবে, এটা আমাদের মানসিকতার মধ্যে নেই, আমাদের রুচি, সংস্কৃতির মধ্যে নেই। শহরে বাচ্চাদের খেলার জায়গা নেই, এমন সব পার্ক বানিয়ে রেখেছে যা তাদের জন্য উপযোগী নয়, টাকা এবং ব্যবসায়িক মানসিকতা এখানে চরম আকার ধারণ করেছে। আমরা যে বাচ্চাদের গুরুত্ব দিচ্ছি এটা বোঝার কোনো উপায় নেই। এদেশে শিশু একাডেমিতে কী কাজ হয়Ñআপনি বুঝতে পারবেন না, এখানে শিশুদের আকাঙ্ক্ষাকে মতাদর্শিকভাবে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করা হয়। স্কুলে শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের একজন হিসেবে পারফর্ম করতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক। অন্য কিছু করলে আপনি সেখানে টিকতে পারবেন না, সমাজ আপনাকে গ্রহণ করছে না। শিশুকে আমি বাধ্য করছি, বাবা-মা হিসেবে প্রশংসা পাচ্ছি। আসল বিষয় হচ্ছেÑশিশু কীভাবে সাজবে, কল্পনা করবে সে কন্টেন্টগুলোকে আমরা উন্নত করছি কি না। পরিশেষে এটাই বলবÑআমাদের শিশুদের জন্য যে সাহিত্য হওয়া দরকার, যে সিনেমা হওয়া দরকার সেগুলো হয় না। একটা সিনেমা শিশুটি বারবার দেখতে চাইবে, এমন উদাহরণ আমাদের দেশে গত ২০ বছরে খুব একটা নেই।
আমাদের চ্যানেলগুলোতে ছোটদের জন্য কোনো স্লট বরাদ্দ নেই, ছুটির দিনেও তাদের জন্য কোনো অনুষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকারের উচিত ছিল এসব বিষয় নিয়ে কাজ করা। আজকে আমরা যে তরুণ সমাজকে পাচ্ছি, তারা একসময় শিশু ছিল। শিশু বয়সে তার যেরকম সভ্যতামূলক পরিবেশে বেড়ে ওঠার কথা, তার সামান্যতম সে পায়নি। মানুষ তো একটা পশু হিসেবে জন্ম নেয়। ধীরে ধীরে সে সমাজের সদস্য হয়ে ওঠে, কিন্তু তার পশুত্ব যাচ্ছে না, সীমাবদ্ধ রুচি ও কল্পনার কারণে সভ্য সমাজের দিকে সে যেতে পারে না। তার ছেলেবেলাটা অন্ধত্বের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কেউ যখন বাচ্চাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছে, তখন এমন এক পদ্ধতিতে বলেছে সেখানে খুব বাজে ধরনের অহংবোধ বাচ্চাদের গড়ে উঠছে। এগুলো খুব হতাশাজনক। শিশুদের নিয়ে কাজ করা খুব জরুরি, আমাদেরকে সমস্ত সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিসর থেকে ভাবতে হবে।
- আপনি নিশ্চয় দেখেছেন ‘শুনতে পাও কি’ নামের একটি চলচ্চিত্র, যেটি কামার আহমাদ সাইমন নির্মাণ করেছেন; এটি নিয়ে আপনি প্রশংসাও করেছেন। এ ধরনের চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যকে কখনও কখনও দুর্বল মনে হয়Ñকেননা চলচ্চিত্রটি ‘ওপেন স্ক্রিপ্ট’-এ নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়।
মামুন : পরিচালকের ইচ্ছাকে যদি আমি বুঝে থাকিÑএটা ওপেন না, একটা ঢিলেঢালা স্ক্রিপ্ট; এখানে পরিচালক একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। সে শুধু স্ক্রিপ্ট দেখে করছে না, তার কিছু চরিত্র আছে যা অনুশীলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। হয়তো একজন ব্যক্তির আচরণ ভালো লাগল, তাকে বাছাই করে একটা চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিল। এজন্য ওপেন মনে হবে, একটা চরিত্র এমন স্বভাবগতভাবে কথা বলে যাচ্ছে, সেটা ধারণ করার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলোÑ‘এই দৃশ্যটা নেওয়া হয়েছে, আপনি যদি চান এই অংশ রাখা হবে না হলে ফেলে দেওয়া হবে।’ এটা সিনেমা তৈরির আলাদা একটি ধারা। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায়, আগের চিন্তাধারা ছিল, একটা ধরাবাঁধা স্ক্রিপ্ট আছে এবং সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। কিন্তু আজকাল একজন নৃতাত্ত্বিক বা মেকার নিজে আগে ঘটনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার পর তার চিন্তাভাবনাকে সংশোধন, উন্নত করে কাহিনি উপস্থাপন করছে। প্রকৃতিগতভাবেও এটা খুব কার্যকর। সিনেমা বলতে আমাদের যে একটা ভুল ধারণা, বদ্ধ ধারণা তৈরি করেছে হলিউড ও বলিউড, সিনেমা নিয়ে এরকম ভাবনা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে।
- আমাদের দেশে চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়ানো হয় কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারিভাবেও রয়েছে ইন্সটিটিউট। তবু চলচ্চিত্রশিল্পটি এখন অব্দি উন্নত হতে পারেনিÑএর প্রধান কারণগুলোকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
মামুন : এখানে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়Ñবাংলাদেশ সরকার এটাকে ইন্ডাস্ট্রি ভাবল কি না, সেন্সর বোর্ড কীভাবে কাজ করছে? এবং অন্যান্য আইন কীভাবে কাজ করছে? এগুলো একটা দিক। অন্যটি হলোÑএর যে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা, সেগুলো আমরা কীভাবে দেখলাম? সেটা আমরা দেখতে পাইনি, দেখিনি আসলে। আশির দশকে কলকাতার সিনেমার তুলনায় আমাদের সিনেমা অনেক ভালো, এটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তারপর কেন ছেদ ঘটল? সেন্সর একটা বাধা, সরকারের দিক থেকে সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে প্রণোদনা সেই অর্থে নেই। দেখুন, আশির দশকে ঢালিউড থেকে আলমগীর কবিরসহ ভালো পরিচালকেরা একসাথে বের হয়ে আসেন, তাঁরা বলেনÑ‘আমরা ভালো সিনেমা করতে পারছি না, আমরা স্বাধীনভাবে সিনেমা তৈরি করব।’ কিন্তু পরে যারা ইন্ডাস্ট্রি দখল করল, সেই পরিচালকেরা কিন্তু কাটপিস ব্যবহার করে, মূলত নানাভাবে কাহিনি সাজিয়ে বাজার ধরার চেষ্টা করেছে। আগের গানগুলো যাঁরা লিখেছেন (গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সৈয়দ শামসুল হক), স্ক্রিপ্টগুলোও দুর্দান্ত (সারেং বউ : শহীদুল্লাহ কায়সার)Ñভাবুন কত শক্তিশালী কাজ হয়েছে। পরের প্রজন্ম এই স্ক্রিপ্টগুলো আর তৈরি করতে পারল না।
আরেকটা দিক হচ্ছেÑটেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির উত্থান ঘটছে, আসাদুজ্জামান নূর থেকে শুরু করে একটা বড় অংশ চলচ্চিত্রে প্রবেশ না করে টেলিভিশনে ঝুঁকে পড়লেন। টেলিভিশনে নাটকের মাঝে বিজ্ঞাপনের অংশ থাকছে। তারা বিজ্ঞাপনের ফার্ম খুলে বসলেন। স্ক্রিপ্ট দুর্দান্ত হচ্ছে, এখন যারা চলচ্চিত্র পরিচালক আছেন তারা সবাই বিজ্ঞাপনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কারণ, বিজ্ঞাপন লাভজনক, এতে রিটার্ন ভালো। এতে করে যেটা ঘটল, নাটকের মধ্যে অনেক বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হলো। এই যে টেলিভিশনের দিকে শিফট করে চলে আসা, যারা চলচ্চিত্রে নিজের নাম লেখাতে পারত! এসবের কারণেও এই ইন্ডাস্ট্রিটি বিকশিত হতে পারেনি বলে আমি মনে করি।
- আপনার নিজস্ব একটি চলচ্চিত্র ভাবনা থাকবার কথা, কেননা সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে আপনার চিন্তার নিজস্বতা রয়েছে, সেটি নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন।
মামুন : নিজস্ব কোনো চিন্তাভাবনা আসলে নেই। সিনেমা সংস্কৃতির অংশ। সামাজিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক দিকগুলো থেকে আমি সিনেমার দিকে তাকাই। ভিজ্যুয়াল পাঠ করা আমার একটি ক্ষেত্র, ক্রিয়েটিভ ভিজ্যুয়াল তৈরিতে আমি যাচ্ছি না হয়তো।
- চলচ্চিত্র সমালোচক বা আলোচক কিংবা সমঝদার যেভাবেই নিজেকে অভিহিত করবেন আপনি, আপনার সেই অবস্থান থেকে এদেশে চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থের যে সংকট রয়েছেÑসেই দিকটি কীভাবে নিরসনযোগ্য বলে মনে করেন?
মামুন : এক অর্থে যদি বলিÑআমাদের এখানে গ্রহণযোগ্য বইগুলোর ভালো অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। বাংলা একাডেমি উদ্যোগ নিতে পারত, সেটা আসলে হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ দুই-একটা কাজ করেছেন। যেমনÑ মাহমুদুল হাসান সম্প্রতি আন্দ্রে বাঁজা নিয়ে একটি কাজ করলেন। এরকম কাজ হয়নি খুব। আলমগীর কবিরের কাজও স্মরণীয়Ñ ওনার পরে সে মানের লেখা আমরা পাইনি। সমাজেও সেরকম প্রণোদনা নেই। সিনেমা নিয়ে বেশ কিছু ডিপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে এবং তারা চলচ্চিত্রে পিএইচডি করেছে; কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশের সিনেমার জন্য খুব একটা কাজে আসছে না। আবার কিছু লেখা ইংরেজিতে, সেগুলো তারা বাংলায় লেখেননি, তাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্লোবাল রিডারের কাছে পৌঁছানো, গ্লোবাল অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া, কোনো একটা সার্টিফিকেট পাওয়া, ডিগ্রি পাওয়া। এর বাইরে দেখবেন যে বাংলাদেশের মানুষকে সিনেমাতে আকৃষ্ট করার মতো বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। দুঃখজনক হচ্ছে, যেসব গবেষণা বা বইপত্র তৈরি হয়েছে বেশিভাগের ক্ষেত্রে রিসার্চ কম। সেগুলোকে ঠিক সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চ হিসেবে ভাবা যায় না। সোশ্যাল সায়েন্সের যে একটা এনগেজমেন্ট দরকার, সিনেমার টেক্সটের সাথে সেটা ঘটেনি। বরং আমাদের কাছে অতিপ্রাচীন সাহিত্যপাঠের টুলস ছিল, সেগুলো দিয়ে তারা সিনেমা বিচার করতে গেছেন। এগুলো পড়লে হয়তো আপনি কিছু তথ্য পাবেন, কিন্তু কোনো উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন না।
- স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দ্বারা বিকল্পধারা চলচ্চিত্র আন্দোলন এদেশে হয়ে আসছে দীর্ঘদিনÑএই ধরনের আন্দোলন চলচ্চিত্রশিল্পে নতুন কী যোগ করেছে?
মামুন : স্বাধীন বলতে, আমরা এফডিসির বাইরে সিনেমা করতে পারছি। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ফান্ড কালেক্ট করছি, শুধু এফডিসিতে কাজ করছি নাÑএটাই হচ্ছে আমাদের স্বাধীন চলচ্চিত্রের ধারণা। এ ধারাটা বিকশিত হলো যারা শর্টফিল্ম মুভমেন্ট থেকে বের হয়ে আসলো তাদের মাধ্যমে।
আশির দশকে প্রধান তিনজন পরিচালকÑতানভীর মোকাম্মেল, মোর্শেদুল ইসলাম, তারেক মাসুদ। আপনি এবার খেয়াল করবেনÑতানভীর মোকাম্মেল, মোর্শেদুল ইসলাম কীভাবে সিনেমা বানালেন আর তারেক মাসুদ কীভাবে বানালেন? তারেক মাসুদকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তাঁর শেষ সিনেমা ‘কাগজের ফুল’-এর জন্য ঢাকার একটি জমি বিক্রি করতে হয়েছিল। অন্যদিকে, তানভীর মোকাম্মেল, মোর্শেদুল ইসলামÑনিয়মিত সিনেমা তৈরি করেন এবং প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। এগুলোকে স্বাধীন বলা যায় না, আমি যদি বলি আগেকার আইডিওলজিক্যাল ফ্রেম থেকে স্বাধীন, তাহলে কিন্তু টাকা উপার্জন করা কঠিন এবং খুব ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় হাঁটতে হয়। ওনারা হেঁটেছেন একদম পাকা রাস্তায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদÑএই ফ্রেমের বাইরে তাঁরা যাননি। নিজের মতো একটা ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স সাজাতে পারছি না, তাহলে সেটা কীভাবে স্বাধীন হয়?
শিল্পকলা একাডেমি থেকে চলচ্চিত্র বিষয়টিকে বাদ দেওয়া হয়েছেÑএ নিয়ে স্বাধীন চলচ্চিত্র পরিচালকেরা প্রতিবাদ করেছেন; এটাকে কীভাবে দেখছেন?
মামুন : শিল্পকলায় ফটোগ্রাফির আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকবে কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্য থাকবে না! কেন? এটা একটা বিশেষ কোনো স্টেকহোল্ডারের প্রভাবে হয়েছে বলে আমার অনুমান। বিশেষ বিশেষ স্টেকহোল্ডারের জায়গা থেকে তারা এটা করেছে। শিল্পকলা একাডেমি হচ্ছে একটা শোকেস। একটা জাতি এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে আমার যা কিছু অর্জন করেছিÑতার প্রদর্শন ঘটে শিল্পকলায়। শিল্পকলার অবকাঠামো সারাদেশে আছে। সেখানে কেন চলচ্চিত্র থাকবে না, এর কোনো যুক্তি নেই। তাহলে কি চলচ্চিত্রকে আমরা শিল্পকলা ভাবব নাÑচলচ্চিত্র কি শিল্পকলার মধ্যে পড়ে না? ১৯৭৪ সালে চলচ্চিত্র আলাদা বিভাগ ছিল কিন্তু। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্রকে রাখা হয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এটি একটি ভুল, এটা সংশোধন করতে হবে এবং এসব থেকে বের হয়ে আসতে হবে।
- বাংলাদেশের মফস্বল শহর থেকে শুরু করে খোদ রাজধানী শহরেও সিনেমা হল বন্ধ হচ্ছে; গ্রামে আগে যাত্রাপালা, কবিগান, অপেরাসহ নানামুখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, অধিকাংশ জায়গায় এখন সেগুলোও বন্ধ হয়েছে। মানুষের সমাজে সংস্কৃতি রুচি নির্মাণ করেÑএই ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব চিন্তাটা কী?
মামুন : ছেলেবেলায় আমি লক্ষ করতাম, কৃষকরা যখন মাঠে ধান কাটছে বা চাষ করছে তাদের গানের সুর ভেসে আসত। সন্ধ্যায় তারা যখন বাজার করে ঘরে ফিরছে, গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। আমার নিজের বাড়িতে আমি নিয়মিত দেখেছি যে কবিগান, লালন ফকিরের গান, জারিগান, প্রতি সপ্তাহে গানের অনুষ্ঠান হতো, আর যাত্রাপালা তো ছিলই। নব্বই দশকের পর থেকে এগুলো বন্ধ হতে শুরু করল। কারণ, ইসলামিস্টরা খুব সক্রিয় হয়ে ওঠা শুরু করল। এগুলো হারামÑএরকম শব্দ ব্যবহার হতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, যাত্রাপালা বলতে আজকাল কী বোঝায়? কলেজে পড়ার সময় আমি যখন মধ্যরাত্রিতে গিয়ে বাবাকে বললামÑবন্ধুরা মিলে যাত্রাপালা দেখতে যাব। বাবা বললেনÑআজকাল তো আর যাত্রাপালা হয় না, কীসব আজেবাজে জিনিস দেখায়, ইচ্ছা হলে যাও! বাবার এই কথার ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে আমি আর গেলাম না। আমি বুঝলাম যে, মেয়েদের অশ্লীলভাবে নৃত্যের ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, এগুলো তো গ্রামের সমাজে গ্রহণযোগ্য না; কিন্তু বখাটে ছেলেরা এগুলোই দেখতে শুরু করল। পরিণতিটা কী? ইসলামিস্টরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করল এবং পারস্পরিক ঘৃণার জায়গা তৈরি হতে শুরু করল। আশির পর থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে। কট্টর প্রগতিপনা বনাম ইসলামিস্ট ইন্টারপ্রিটেশন। গত পনেরো-বিশ বছরে, টেরোরিজমের কারণে সংস্কৃতিচর্চার পরিসর আরো কমেছে। আমার ধারণা যে, এখান থেকে আবার পুনরুত্থানের দিকে যেতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতির চর্চা যদি না থাকে তাহলে সমাজ একটা বর্বর সমাজ হয়ে উঠবে।
- আপনার প্রিয় চলচ্চিত্রকারদের কথা জানতে চাই।
মামুন : আইজেনস্টাইন, কোরিয়ান পরিচালক কিম কি দুক, রাশিয়ান পরিচালক ভিত্তোরিও ডি সিকা, ভারতীয় উপমহাদেশের ঋতুপর্ণ ঘোষ খুব প্রিয়; বাংলাদেশের তারেক মাসুদ, জহির রায়হান, আলমগীর কবির এঁদের কাজ ভালো লাগত। তাঁরা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন। নতুনদের মধ্যে কারো কারো কাজ ভালো লাগে, দেখা যাক তারা ভবিষ্যতে কী করে। আরো অনেকে আছেন। আমাদের এখানে বরাবরই একটা ফাঁকা জায়গা থেকে গেছে, জায়গাটা আমরা পূরণ করতে পারিনি।
- জনসংস্কৃতি বলে যে একটি বিষয় রয়েছে, চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে কতটা তা পূরণ হয় বলে মনে করেন?
মামুন : ওয়াল্টার বেঞ্জামিন একরকমভাবে চিন্তা করে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত লেখা ‘দ্য ওয়ার্ক অব আর্ট ইন দ্য এইজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন’, সেখানে তিনি ফটোগ্রাফি এবং সিনেমা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সিনেমার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন। শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, সিনেমার যে ভিজ্যুয়াল ভাষা তা আমাদের গভীরে প্রবেশ করে। সিনেমা রিপ্রোডিউস যখন হচ্ছে তখন তা সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, আর্ট-কালচারে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আগেকার আর্টফর্ম যদি আপনি দেখতে চানÑযেমন ভিঞ্চির ‘মোনালিসা’, তাহলে আপনাকে যেতে হবে লুভর মিউজিয়াম। কিন্তু ‘মোনালিসা’র ছবি যদি আপনি রিপ্রোডিউস করতে পারেন, তাহলে এই ছবি অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে, আমাদের অংশগ্রহণও বাড়িয়ে দেবে। সিনেমা যেহেতু কাঠামোগতভাবেই পুনরুৎপাদনযোগ্য, সেহেতু শুরু থেকেই সিনেমাতে অংশগ্রহণ আরও বেশি করে বাড়ছে। অংশগ্রহণের এই সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়েই বেঞ্জামিন ভাবলেনÑসিনেমার মধ্যে তাহলে মুক্তির সম্ভাবনা আছে, একটা সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা আছে। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ১৯৩৫ সালে যা লিখেছেন, সংস্করণ করেন ১৯৩৯ সালে। নতুন করে ‘অপ্টিক্যাল আনকনসাস’ ধারণা যুক্ত করে তিনি বলেছেনÑ‘আমি খালি চোখে যা দেখতে পাচ্ছি, ক্যামেরার চোখ দিয়ে তার চেয়ে বেশি দেখতে পাচ্ছি।’ ফলে তাঁর মতে, স্থির ও চলমান ইমেজ আমাদের অচেতনে গিয়ে কাজ করে। অচেতন সত্তাকে সক্রিয় করা, নির্দেশনা দেওয়া নানান ক্ষেত্রে ক্যামেরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ভিজ্যুয়াল নিয়ে তাত্ত্বিকরা বলছেনÑনব্বই দশকের পর থেকে আমরা একটা পিকটোরিয়াল টার্নে এসে পৌঁছেছি। এখন সমাজকে দেখার ক্ষেত্রে বা বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিজ্যুয়াল একটা গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট, এটা বাদ দিয়ে কোনো সমাজকেই আর দেখা সম্ভব হয় না। আমি মনে করি যে, ভিজ্যুয়ালের যে ফাংশন, যেমন ফ্রয়েডিয়ান ইন্টাপ্রিটেশনে দেখা যায়, তিনি বারবার ফিল্মের নেগেটিভের সাথে আনকনসাসকে তুলনা করেছেন। আনকনসাসে যেটা থাকছে সেটা ল্যাটেন্ট ইমেজ, এই যে ইমেজ, ফিল্ম এই শব্দগুলো ফ্রয়েড অচেতনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার ব্যবহার করেছেন। ফলে ইমেজের ফাংশনটা আমাদের আনকনসাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই সিনেমার গুরুত্বটাকে আমি ভাবতে চাই যে, যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের বাংলাদেশেকে আমরা কল্পনা করতে পারিÑযেটা উপন্যাসের মাধ্যমে হয়, গল্পের মাধ্যমে হয়; সেটা সিনেমার মাধ্যমে আরো বেশি হতে পারে এবং সেটা হওয়া দরকার। সেখানেই আমি দেখি সিনেমার পটেনশিয়ালিটি; এবং অবশ্যই গৎবাঁধা কাহিনির মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকব না।
- ‘সিনেমার সাংস্কৃতিক রাজনীতি’ নামে আপনার যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে, এই গ্রন্থটিতে মোট পাঁচটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছে, চলচ্চিত্র এবং আমাদের সংস্কৃতির অনেক বিষয় বইটিতে তুলে ধরেছেন ক্রনিকল উপায়ে। ‘চলচ্চিত্রে পুরস্কারের রাজনীতি’, ‘চলচ্চিত্রে বাউল পরিবেশনা’ এবং ‘চলচ্চিত্রে আত্মসত্তার রাজনীতি’Ñবিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করবেন কি?
মামুন : আপনি দেখবেন বইয়ের পুরোটাজুড়ে ‘দিস ইজ আওয়ার কালচার, দিস ইজ ট্রেডিশন, দিস ইজ বাঙালি সংস্কৃতি’Ñযে গল্পগুলো বলা হচ্ছে, আমি সেসব ধারণাকে প্রব্লেমাটাইজ করেছি। যে সংস্কৃতির কল্পনা আমরা করেছিলাম, যে ধরনের ইতিহাস আমাদের কল্পনায় থেকেছে, ভাষার ব্যবহারে থেকেছে সেগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছি। ইতিহাস এবং ভাষা এই দুটোতে আমার বেশি ফোকাস থেকেছে। ভাষা হচ্ছে একটা ডোমেইন, সেখানে আমরা পার্টিসিপেট করি এবং এই ডোমেইনে কে বেশি কথা বলছে, কে জোরে কথা বলছে, কীভাবে কথা বলছেÑসবই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। জঙ্গীদের নিয়ে যে সিনেমাগুলো হলো, জঙ্গীর গল্পটা কী আসলে? বা ফকির লালন কীভাবে বাউল হলো? কোন হিস্টোরিক্যাল প্রসেসে ফকির বাদ দিয়ে বাউল শব্দটা আমাদের সমাজে, সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেয়? বাঙালি শব্দের ইতিহাস কী? শব্দগুলো কোন লেয়ারে, কোন পর্যায়ে কীরকম রূপ নিয়েছে? আমি বাংলাদেশে বসে কীভাবে ভাববÑএই প্রশ্নগুলো আমি এই বইয়ে ডিল করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, শেষ অধ্যায়ে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন যেÑতারেক মাসুদকে নিয়ে আমি কথা বলেছি, আমরা বাঙালি না মুসলমানÑএই প্রশ্নের রেজ্যুলুশন নিয়ে লিখেছি; খুব ভালো লিখতে পেরেছি তা বলা যাবে না। আমরা যে বাইনারি পদ্ধতিতে কাজ করি, যে মডার্নিস্ট ফ্রেমে পাঠ করি, সেসব পদ্ধতির মধ্য দিয়েই তারেক মাসুদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি সেখান থেকে সরে আসতে চেয়েছি। তাহলে তারেককে ব্যাখ্যা করার নতুন পদ্ধতি কী হতে পারে, নতুন চিন্তার ধরন কী হতে পারে? বিয়ন্ড বাইনারি ভাবতে পারা আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হয়ে ওঠে, সেই প্রস্তাবটি যুক্তি হিসেবে শেষের কয়েক পাতায় লেখা আছে। গুরুত্বপূর্ণ ভাববার বিষয় কালচারাল পলিটিক্স কীভাবে ঘটে? এটা একটা পাওয়ার গেম। পাওয়ার গেমের মধ্যে কালচার কীভাবে অপারেট করে, কীভাবে কনটেম্পরারি পলিটিক্স তৈরি করে। ধরুনÑআজকে সারা পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের মানুষ ভায়োলেন্ট না, সাধারণত টলারেন্ট; কিন্তু মুসলমান সম্বন্ধে একটা ধারণা বিশ্বব্যাপি তৈরি হয়েই আছে যে, মুসলমান মানেই ভায়োলেন্ট। যখন মডার্নিটি গড়ে উঠছে তখন থেকেই একটা ওরিয়েন্টালিস্ট ভিউ, সেই ভিউটা কীভাবেÑ ভায়া কলকাতাÑএকটা ফ্রেমওয়ার্কের ভেতর দিয়ে আমাদের ভেতরে এসে উপস্থিত হয়েছে তা ভাববার বিষয়। নিজস্ব সত্তা বিষয়ে ভাবার ক্ষেত্রে একটা বাধা তৈরি করা হয়েছে। বাঙালি মুসলমান, মুসলমান মানেই উদ্ধত, দাম্ভিক, উগ্র, হিংস্র এবং তাদের কোনো কালচার নাই। এসব গৎবাঁধা ধারণা আমাদের ভেতর ভয়ংকর ধরনের পলিটিক্স তৈরি করেছে।
- ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, শহরকেন্দ্রিক মানুষ এই ওয়েব মাধ্যমটিকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করছে; কিন্তু যারা নাকি হলে বসে সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত গ্রামের মানুষ, তাদের কথা ভাবুন…
মামুন : ওটিটি কাদের চাহিদা পূরণ করছে? মধ্যবিত্ত, যাদের কানেক্টিভিটি আছে, অ্যাফ্লুয়েন্স আছে, যারা গ্লোবাল কালচারের সাথে যুক্ত। কিন্তু ভবিষ্যতে ধরুন যেÑসিনেমার কী হবে? যাদের কাছে সিনেমা হল ছিল, যারা গ্রামে-গঞ্জে সিনেমা দেখতে হলে যায়! আশির দশকে ফাঁকা মাঠের মধ্যেও এক একটা সিনেমাহল গড়ে উঠেছিল। আমি মনে করি, এগুলো ভবিষ্যতে আর থাকবে না। কারণ সিনেমাহলে যাওয়ার এই কালচারটা থাকবে না। মানুষের যে ব্যস্ততা, সময়ের যে হিসাব তা দেখে বুঝিÑএখন এই ওটিটি, মোবাইল ফোন, বাড়ির টেলিভিশন এটা মানুষের আত্মিক চাহিদা পূরণ করবে। একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, বড় শহরগুলোতে কমার্শিয়াল ভেঞ্চার হিসেবে সিনেপ্লেক্স গড়ে উঠবে। বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবারের প্রধান বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে, সেখানে মানুষ যাবে, খাবে, এক সিনেমা দেখা শেষ করে আরেক সিনেমা দেখবে। দল বেঁধে এই ব্যাপারগুলো ঘটবে। সিনেপ্লেক্স নতুন টেকনোলজির সুবিধা এবং অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে সোশ্যাল স্পেস হিসেবে অবশ্যই উন্নত হবে। এর সাথে আমাদের আরেকটা জিনিস ভাবা দরকারÑআগে গ্রান্ড সিনেমাহলের কথা ভেবেছি, অনেক বড় পর্দা, অনেক ভালো সাউন্ড এসব নিয়ে ভেবেছি; তার চেয়ে একশ-দুইশ সিটের ছোট ছোট থিয়েটারের কথা ভাবা দরকার। এগুলো জেলা লেভেলে, থানা, গঞ্জ লেভেলে থাকবে। সেটা একটা ভায়াবল অপশন হতে পারে। গত পনেরো থেকে বিশ বছর আগেও আমাদের এক হাজার থেকে দেড় হাজার সিনেমাহল ছিল। কোভিডের সময়ে একশটি হল সিনেমার জন্য চালু ছিল। এগুলো আবার রিভাইভ করবে না। যেখানে ওটিটি কন্টেন্ট দেখানো যাবে, আবার সিনেমার কন্টেন্টও দেখানো যাবে, এরকম মিলিয়ে থিয়েটার সরকারি উদ্যোগে তৈরি হতে পারে। মিনি থিয়েটার থাকলে নানারকম কন্টেন্ট দেখানোর সুবিধা থাকল এবং অল্প ইনভেস্টমেন্টে অল্প এক্সেস আছেÑএমন উৎসাহী অনেক তরুণ পরিচালক আছে, যারা মজার মজার সিনেমা তৈরি করছে। সে হয়তো দুই-তিনটা সিনেমা নিয়ে দেখাতে গেল, একেকটা এলাকায় বা রিজিয়নে দেখাল। সারাদেশেও রিলিজ দিতে পারে।
- নতুন দিনের চলচ্চিত্র কেমন হবে?
মামুন : চলচ্চিত্র তো ইতিহাসের বাইরে তৈরি হয় না, সময় এবং ডিসকোর্সকে মাথায় নিয়েই তৈরি হয়, এর ভেতর দিয়ে তৈরি হয়। নির্ভর করছে আমাদের দেশে সংস্কৃতি কোন দিকে মোড় নেয়, গ্লোবাল কালচার এবং নিজেদের রিপ্রেজেন্টেশনাল পলিটিক্সের জায়গা থেকে সিনেমাকে দেখছি, গুরুত্ব দিচ্ছি আমাদের কালচারে। এগুলোর ওপরে নির্ভর করবে আসলে নতুন দিনের সিনেমা কেমন হবে। একটা বিষয়ে ইঙ্গিত দিইÑঅন্য একটা ডাইমেনশন থেকে দেখলে, আলমগীর কবির থেকে শুরু করে তারেক মাসুদ, তানভীর মোকাম্মেলদের সিনেমার টার্গেট অডিয়েন্স কারা? একটা জাতীয় অ্যানোনিমাস অডিয়েন্সকে তারা টার্গেট করছে এবং তাদের জন্য সিনেমা বানিয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ, নারী থেকে পুরুষ পর্যন্ত সবাই দেখবে। একটা জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক তাদের সিনেমাগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ভালো-মন্দ যেভাবেই বিচার করেন না কেন, তাদের ক্যামেরা, গল্পের ধরন, তাদের প্লট সিলেকশন সবকিছুর মধ্যে এই বিষয়টি আছে। কিন্তু দেখবেন, তারপরের যে সিনেমাÑধরুন মেজবাউর রহমান সুমন ‘হাওয়া’ সিনেমাটি যে করল, গল্পটি কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট ন্যারেটিভের গল্প এবং পারসোনাল, প্রাইভেট এবং লোকালÑএই বিষয়গুলো পরের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। আপনি দেখবেন শট সিলেকশন থেকে শুরু করে ক্যামেরার ল্যাংগুয়েজÑএগুলো চৌদ্দ-পনেরো সাল থেকে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আমাদের ইন্টিমেট, প্রাইভেট, লোকাল কমিউনিটি এই ব্যাপারগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমার কাছে মনে হয় স্টোরির একটা বদল হচ্ছে গত সাত-আট বছর ধরে, এটা সামনের সময়ে আরো স্পষ্ট হবে এবং বেশি ঘটবে।