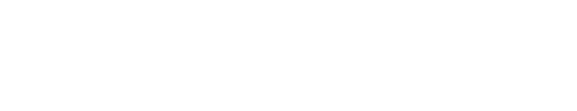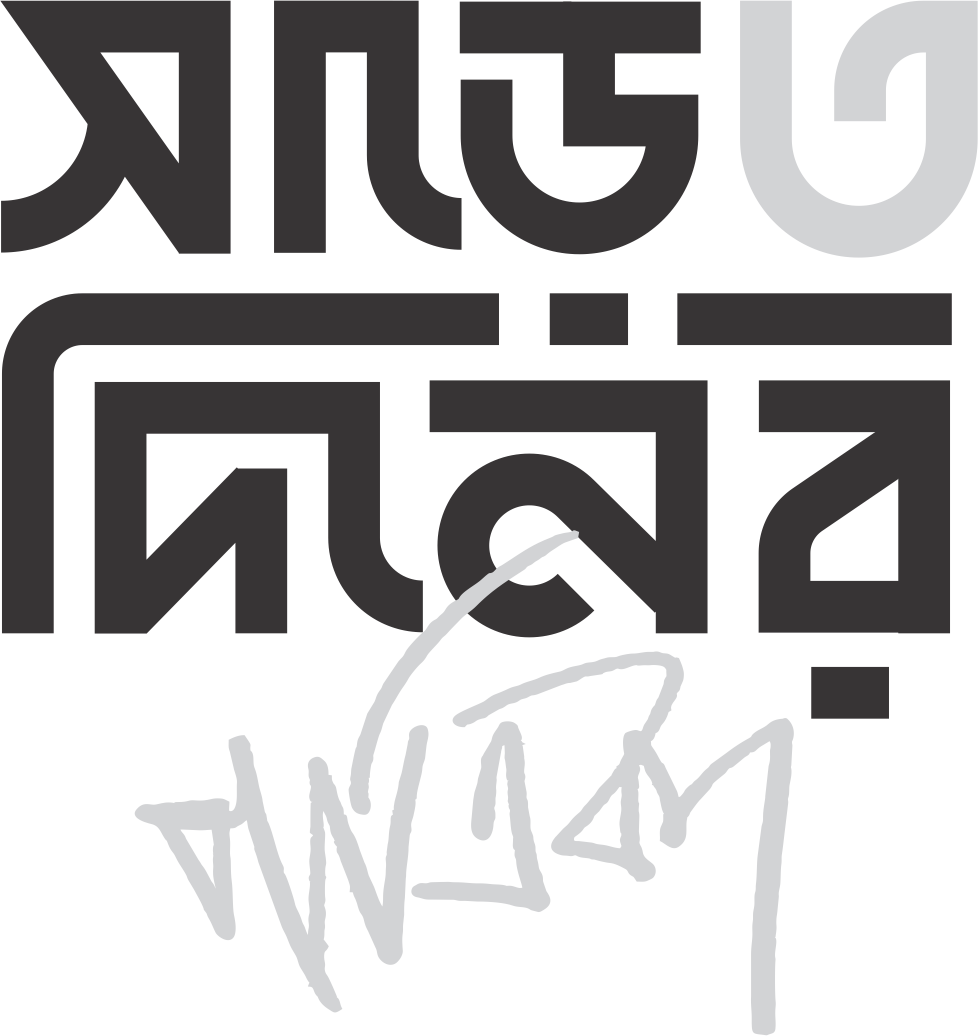অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের জন্ম ১৯৭৫ সালের ২৩ আগস্ট নোয়াখালীর হাতিয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও বিউপনিবেশায়ন নিয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। পরবর্তীতে একই বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। আগ্রহের বিষয় সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন। ড. মোহাম্মদ আজমের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার’, সম্পাদিত গ্রন্থ ‘নির্বাচিত কবিতা: সৈয়দ আলী আহসান’, ‘কবি ও কবিতার সন্ধান’। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্বপালন করছেন। সাড়ে তিন দিনের পত্রিকার জন্য তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এহসান হায়দার।
গত ২০২৪-জুলাইয়ে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনকে আপনি কোন ধরনের আন্দোলন হিসেবে দেখছেন?
মোহাম্মদ আজম : এ কথা আমি অনেকবার বলেছি ও লিখেছি। ২০২৪ সালে সংঘটিত আন্দোলনটিকে আমি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হিসেবেই দেখি। এটিকে আমি কোনোভাবেই বিপ্লব হিসেবে দেখছি না। তবে যে কোনো অভ্যুত্থানেরই বৈপ্লবিক সম্ভাবনা থাকে। এ সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু নানা লক্ষ্মন দেখে মনে হচ্ছে, এ সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমেছে। এ জন্যই আমি মনে করি, এ অভ্যুত্থানকে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি। আমি এটিকে এভাবেই চিহ্নিত করতে চাই। বিশেষত এ অভ্যুত্থান কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি বলে সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কজনিত নানা সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। তাই দেশ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সরকারের প্রকৃত অবস্থা, জনগণের সঙ্গে সরকারের ও রাষ্ট্রকাঠামোর সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয় বুঝতে হলে এই অভ্যুত্থানকে অবশ্যই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে।
বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের ফলে দেশে দেশে নানাবিধ পরিবর্তন হয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আপনি কী কী ধরনের পরিবর্তন দেখছেন?
মোহাম্মদ আজম : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই যে দেশে নানাবিধ পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। আমি এখানে আরেকটি বিষয়ে জোর দিতে চাই। এই অভ্যুত্থানের আগে থেকেই কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। সেগুলো সংগঠিত হচ্ছিল বলেই এ অভ্যুত্থান অনেকদূর এগুতে পেরেছে। আমাদের দেশে ভাবাদর্শিক ও সাংস্কৃতিকÑএ দুটো ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের বৈপরীত্যসূচক অবস্থা জোরালোভাবে বিদ্যমান ছিল। যেমন বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ কিংবা মুসলিম জাতীয়তাবাদের এক ধরনের বিপরীতমুখি অবস্থান থাকায় সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল, সেক্যুলার এমনকি ধর্মীয় মতাদর্শিক ভাবনার যে দ্বান্দ্বিক অবস্থানগুলো ছিল, তা কোনো সমাজের জন্যই ইতিবাচক কিছু হতে পারে না। এ ধরনের অবস্থা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যে মনে হয়, ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের পারস্পারিকতা নেই। বাস্তবে কিন্তু তা রয়েছে। কারণ সারাবিশ্বেই এমন বিভক্তি থাকে। তারপরও তারা একত্রিতভাবে রাষ্ট্র গঠন করে এবং সমাজকে পুননির্মাণ করে থাকেন। তবে এ ধরনের বিভাজন একটি পলিটি বা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী গঠনের জন্য মোটেও ইতিবাচক হতে পারে না। এ ধরনের বিষয় বাস্তবসম্মত নয়। বরং এটি আরোপিত ব্যবস্থা। সমাজে এ আদর্শবাদীতা আরোপিত। বলতে চাচ্ছি, ভিন্নমত থাকবে। কিন্তু পরস্পরের জল-চল থাকবে না, এমনটি হতে পারে না। এ অবস্থাই বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশে বিরাজমান ছিল। বিগত এক দশকে অবশ্য এ অবস্থার বিপরীতে বিভিন্ন ভাবাদর্শের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনার সমন্বয়বাদী প্রক্রিয়া শুরু হয় কিংবা দৃশ্যমান হতে শুরু করে। পারস্পরিক মতাদর্শিক ভিন্নতার পরও যেন এক ধরনের অন্তর্ভূক্তিমূলক সমঝোতার ভিত্তিতে সবক্ষেত্রে কাজ করা যায়, এ প্রচেষ্টা বাড়তে শুরু করে। আমি বলতে চাই, এ চর্চাটারই একটা পরিণতি জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। তাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে এ বিষয়টাকে যদি আমরা জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারি নানাবিধ চর্চার মাধ্যমে, তাহলে অভ্যুত্থানের সুফল আরও বড় পরিমাণে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আমরা ঘরে তুলতে পারব। মতাদর্শিক ভিন্নতা থাকার পরও কীভাবে একত্রিত হয়ে কাজ করা যায়, সে সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা জরুরি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিরোধমূলকতার মধ্যেই আমরা দীর্ঘদিন বাস করায় এ সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও আমরা সব পক্ষের মধ্যে এ বিষয়টি জোরালোভাবে দেখতে পাচ্ছি। এমনটি অতীতে আমাদের জন্য ক্ষতিকর ছিল, আজও অশনীসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই অভ্যুত্থানের পর আমাদের মধ্যে যে প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তার জন্য এমন বিভাজন চূড়ান্তভাবে ক্ষতিকর।
মানুষের মৌলিক চাহিদার সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার সাংস্কৃতিক পরিচয়। দেশ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিকমানস গঠনও সেইজন্য জরুরি। আপনি দীর্ঘদিন এই চর্চার মধ্যে রয়েছেন। বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আপনার দৃষ্টিতে এখন কীভাবে ভাবেন?
মোহাম্মদ আজম : আমাদের মতো দেশের বড় সমস্যা হলো, আঠারো কোটি মানুষকে সম্বোধন করার মতো ভাষা কোনোভাবেই রপ্ত করতে পারেনি। এ সংকটের পেছনে ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে। আমাদের উপনিবেশিক ইতিহাস এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসনামল—এসব প্রেক্ষাপটের কারণে এমনটি হয়েছে। তাছাড়া আমরা দরিদ্র রাষ্ট্র, এটি আরেক বাস্তবতা। অনেকগুলো কঠিন বাস্তবতা এখানে রয়েছে। কিন্তু গুরুতর সমস্যা হলো, দেশের সমগ্র মানুষের জন্য একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। এ জন্য চাই শিক্ষা প্রকল্প। শিক্ষা প্রকল্প দেশের মানুষের মনে এক ধরনের সমরূপতা তৈরি করে। এই সমরূপতা পলিটি কিংবা রাজনৈতিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। তাছাড়া কিছু ক্ষেত্র আছে যেগুলোতে রাষ্ট্র বিনিয়োগ করতে পারে। এ ক্ষেত্র সরাসরি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষায় আমাদের বিনিয়োগ বরাবরই কম। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকারের দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অথচ শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর জিডিপির অনুপাতে সমান করে তোলা উচিত। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ অনেক কম। বরাদ্দের পরিমাণই বলে দেয়, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কৃতির কাজ কী তা একেবারেই বুঝতে পারে না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তর কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তারা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের মানুষকে যথাসম্ভব অন্তর্ভূক্তিমূলক করে তুলবে। আমাদের এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যা প্রধানত ঐক্যমত তৈরি করবে। এমন সংস্কৃতি জরুরি যা যেকোনো মতাদর্শিক লোককে অংশগ্রহনমূলক মনোভাব গড়ে তোলার পাটাতন হিসেবে কাজ করবে। এমন কিছু এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু জনগণেরও এ বিষয়ে দাবি তোলা উচিত এবং সরকারেরও উচিত বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া।
পৃথিবীতে নানান সময়ে আন্দোলন এবং বিপ্লবের ফলে সাহিত্য-চলচ্চিত্র-শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও এসেছে বিপুল পরিবর্তন। আপনার দৃষ্টিতে সেই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন কি?
মোহাম্মদ আজম : আগেই বলেছি, আমাদের এখানে শিল্প-সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইশারাগত কিছু কার্যক্রম গত এক-দেড় দশকে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি আমি বাংলাদেশের নতুন শতকের সাহিত্য শীর্ষক লেখায় আমার আশাবাদ ব্যক্ত করেছি। সেখানে বলেছি, আশাবাদ ব্যক্ত করার মতো ঘটনা ইতোমধ্যেই আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিতে ঘটেছে। ভাষা ও মতাদর্শগত দিক থেকে একটা অর্থকে প্রধান করে তোলা বা আরোপনমূলক কথাকে প্রধান করে তোলা কিংবা নির্দিষ্ট কিছু চিন্তাকেই প্রধান হিসেবে উপস্থাপন করার যে প্রবণতা গত তিন-চার দশকে ব্যাপকভাবে দেখা গেছে, তার মধ্যে বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সত্য নানাবিধ এবং অনেকগুলো সত্য পাশাপাশি অবস্থান করে—এ ধারণা গড়ে তোলা ব্যতীত মহৎ শিল্প-সাহিত্য নির্মাণ সম্ভব নয়। অর্থের মুক্তিই শিল্প-সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য যা দীর্ঘদিন বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে প্রতিবন্ধকতার মুখে ছিল। আমাদের মূলধারার বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ মূলত একটি অর্থকেই সত্য হিসেবে আঁকড়ে থাকে। এই অভ্যুত্থানে অনেক গান ও কবিতা লেখা হয়েছে। এমনকি প্রচুর বইও লেখা হয়েছে যা বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রবন্ধ সংখ্যায় অনেক লেখা হয়েছে। এটাও চলমান ইতিহাস। এগুলো ইতিবাচক লক্ষ্মন। কিন্তু তা এই ইতিবাচকতা আরও বড় জায়গায় যাবে কী না, তা নির্ভর করছে পুরো জনগোষ্ঠীর গঠনগত বাস্তবতা এবং তার পরিণতিতে রাষ্ট্রের গঠনগত বাস্তবতার ওপর নির্ভর করছে। এ বিষয়গুলোই শিল্প-সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।
সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে দেশীয় চিন্তার পূর্ণতা পায়, এই বিষয়টি নিয়ে আপনার ভাবনার জায়গাটি জানাবেন কি?
মোহাম্মদ আজম : জনসমাজ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন যদি পরিপূর্ণ গঠন পায় ও চর্চা চালিয়ে যায় তাহলে তার ফল আমরা সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধতায় পাবো। আর যখন এ চর্চা চলবে তখন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোও তা গ্রহন করবে। তারা সে ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিতে শুরু করবে। তৃণমূল অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে যা উঠে আসবে, সেটিকেই রাজনৈতিক দলের অবলম্বন ভাবতে হবে। এমনটি পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটে। উল্টোটা কখনই ঘটে না। রাজনৈতিক দল তা আরোপ করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণ এর বিরোধিতা করে। দেশীয় চিন্তা বলে আলাদা কিছু নেই। সারা পৃথিবীতে যেভাবে চিন্তাভাবনা হয়, এগুলো সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা যেন আমাদের দেশের অগ্রসর মানুষরা নিতে পারে সে দায় রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে। এগুলো যদি আমাদের স্থানিক বাস্তবতা ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে চর্চা করা হয়, তাহলে দেশের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবেই।
সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটতে যে সকল আয়োজন প্রয়োজন, সেটি এদেশে কেমনভাবে বিদ্যমান রয়েছে?
মোহাম্মদ আজম : বিপ্লব একটি ভিন্ন ধারণা। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবী নই এবং পরিকল্পিত বিপ্লব অর্থাৎ বিপ্লবের পরিকল্পনাকে আমি ভালো ধারণা মনে করি না। তবে যারা করেন, তাদের জন্য শুভকামনা। আমি মনে করি, যে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিকল্পনার মাধ্যমে হবে না। দেশের মানুষই তা করবে। বরং রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যারা মুখ্যত কাজ করেন, তারা এমন এক ধরনের কাঠামো তৈরি করবেন যেখানে জনগণ কোনোভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে। এই কাঠামো থেকেই এক সময় বড় প্রতিভা তৈরি হবে। তাই পরিকল্পিত কর্মসূচি দিয়ে সংস্কৃতির প্রাঞ্জলতা আনা যায় না। এ জন্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এগুতে হয়।
আমাদের এখানে আন্দোলনের ফলে মানুষের মধ্যে যে মৌলিক যোগাযোগগুলো ছিল তা ভেঙে পড়েছে। এই ভেঙে পড়া যোগাযোগের সেতু কীভাবে পুনর্র্নিমাণ সম্ভব বলে মনে করেন?
মোহাম্মদ আজম : উত্তরটা সহজ। আগেই বলেছি, আমাদের আগেও যে সেতুগুলো ছিল তা ভাঙা ছিল। আমাদের এখানকার বৈশিষ্ট্যই হলো, চল-অচলের মধ্যে আটকে থাকা। তা ভেঙে যাওয়া ইতিবাচক বলে ভাবি। নতুন সেতু নির্মাণ করা খুবই সহজ। শুধু আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হলো, মতপার্থক্য মানেই পরস্পরকে ধ্বংস করার ছাড়পত্র নয়। বরং মতপার্থক্যসহ অন্তর্ভূক্তিমূলক কাজ করার পাটাতন গড়ে তোলার সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে গুরুত্ব বাড়াতে হবে।