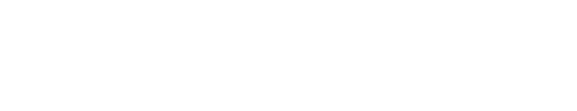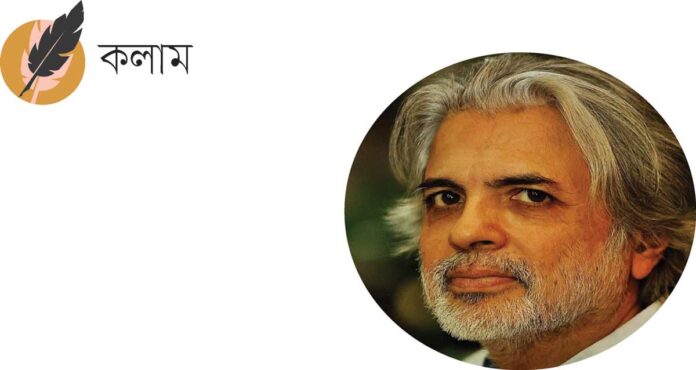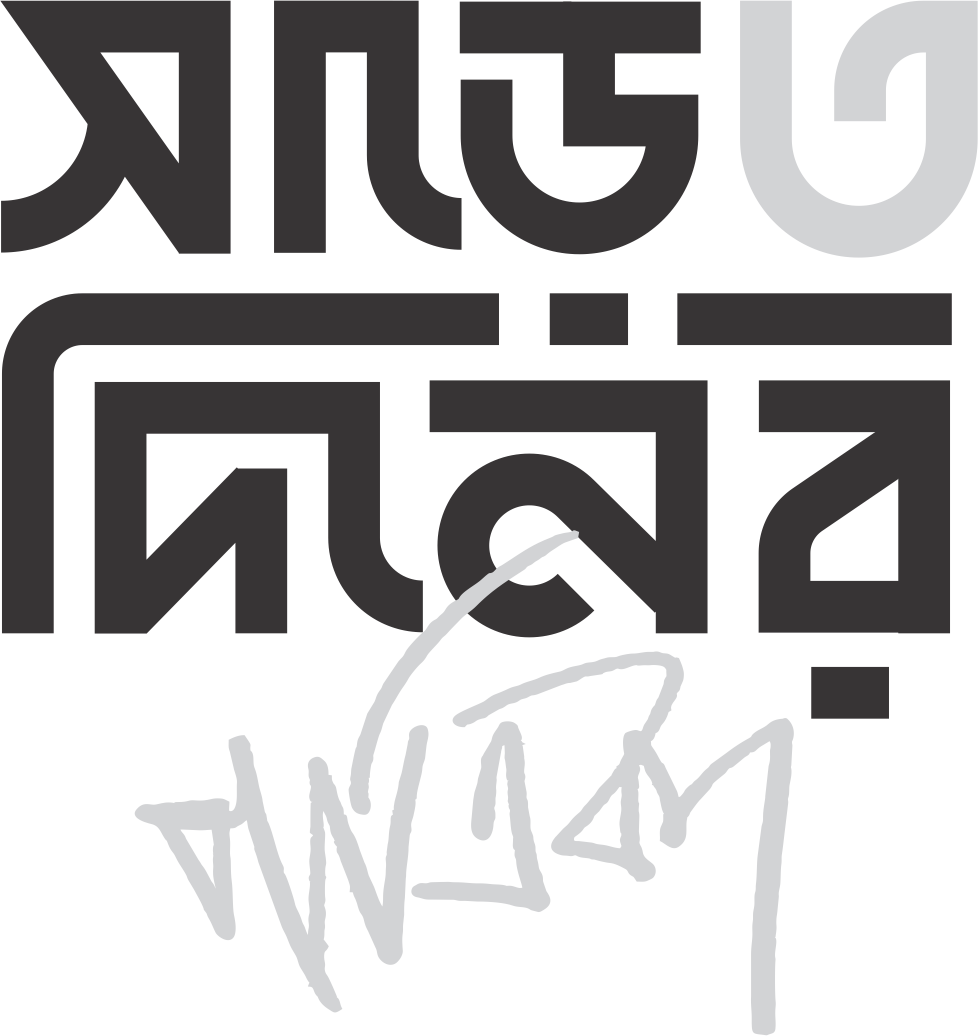আমি অনুবাদ করছি চল্লিশ বছরেরও অধিককাল ধরে। শুরু হয়েছিল সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে, যখন আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যদিও আমার প্রধান আগ্রহটা ছিল সাহিত্যের প্রতি। তখন মূলত কবিতা, গল্পই লিখতাম; মাঝে-মধ্যে গ্রন্থালোচনা কিংবা সাহিত্য বিষয়ক টুকটাক নিবন্ধ। সেগুলো ছাপা হতো দেশের প্রধান দৈনিকগুলোর সাহিত্যপাতাতে। তো সেইসব সাহিত্যপাতারই কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, বিশেষ করে দৈনিক বাংলার কবি আহসান হাবীব, দৈনিক ইত্তেফাকের আল মুজাহিদী এবং দৈনিক সংবাদের আবুল হাসনাত, বিশ্বসাহিত্যের প্রতি আমরা তুমুল আগ্রহ লক্ষ করে আমাকে তখন মাঝে-মধ্যে অনুবাদেরও পরামর্শ দেন। বস্তুত তাঁদের সুপরামর্শেই ক্রমে আমার অনুবাদক হয়ে ওঠার প্রাথমিক অভিযাত্রার শুরু। পরে, আশির দশকের শেষপাদে উচ্চশিক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে সেটি তার সত্যিকার অভিমুখ খুঁজে পায় এবং আমি অনুবাদকর্মকেই আমার সাহিত্যজীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করি।
আর সেই কাজে আমার অন্যতম প্রেরণা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পেয়ে যাই এই সময়ের অন্যতম প্রধান চিন্তক, আলোচক, লেখক, শিক্ষক ও অনুবাদক সলিমুল্লাহ খানকে। আমরা তখন নিউ ইয়র্কে একসঙ্গেই থাকতাম, এক বাড়িতেই।
আমি তখন নানাধরনের পাঁচমিশালি অনুবাদ করে যাচ্ছিলাম, একের পর এক নানারকম অনুবাদ-প্রকল্প হাতে নিচ্ছিলাম, সেসব কাজ করতে গিয়ে আমার মনে যেকোনো প্রশ্নের উদয় হলেই আমি তাঁর শরণাপন্ন হতাম এবং নির্দ্বিধায় তাঁর সহযোগিতা নিতাম। আগে হয়তো তেমনটা করার মতো যোগ্য মানুষও পাইনি জীবনে বা নিজের মধ্যে সেরকম তাগিদ বোধ করতাম না। কিন্তু সলিমুল্লাহ খানের সংস্পর্শে এসে শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাকার বিষয়ে তাঁর ভেতরে সিরিয়াসনেস, তাঁর পাঠের বিস্তৃতি, সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক কাজের প্রতি তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ করে আমার মনে হয়েছিল আমি হয়তো তাঁর কাছ থেকে কিছু সত্যিকার ও অর্থবহ দিকনির্দেশনা পেতে পারি। আমার মনে পড়ছে, তাঁর কাছ থেকে অনুবাদ বিষয়ে নানা ধরনের পরামর্শ, উপদেশ আমি পেয়েছিলাম জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। এবং অনুবাদ যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা যে একটা খুব পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ, এটার জন্য যে যথেষ্ট অভিনিবেশ দিতে হয়, সেই বোধটা আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। সেটাকেই হয়তোবা পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি, যাকে একধরনের পেশাদারত্ব বা দায়বদ্ধতার নিদর্শন বলা যেতে পারে। আর আমার নিজের মধ্যে সবসময় একটা জিনিস কাজ করতো; সেটা হচ্ছে কোথাও ফাঁকি না দেওয়ার চেষ্টা, নিজের সঙ্গে প্রতারণা না করার প্রতিজ্ঞা। এটা তো আসলে নিজে নিজেই বুঝতে পারা যায়, একটি কাজ আমি ঠিক করছি কি ভুল করছি। কিন্তু অনেক সময় হয়তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য চলে আসে। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে আমি সবসময়ই একটা ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলাম যে, কোথাও যেন ফাঁক না পড়ে এবং যতদূর সম্ভব আমার অনুবাদটি যেন মূলানুগ হয়, আবার যেন সেটা আমাদের বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
আমাদের যে উদ্দিষ্ট পাঠকশ্রেণি, সেটা যেন তাদের কাছে একইসঙ্গে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হয়। সেই লক্ষ্যটা সবসময় ছিল। আর পাশাপাশি উন্নত বিশ্বে থাকার কারণে, তাদের সাহিত্য পরিমণ্ডলের যে একটা পেশাদারত্ব, সেটার প্রভাবে সব মিলিয়ে আমার মধ্যে এক ধরনের নিবেদন ও নিষ্ঠার মনোভাবও গড়ে উঠেছিল।
অবশ্য, ছাত্রাবস্থায় বা তরুণ বয়সে আমি যেসব অনুবাদ করতাম সেটা তেমন কোনো বৌদ্ধিক তাগিদ থেকে নয়। ওটা একটা আবেগ থেকেই করা; একটা লেখা পড়লাম, ভালো লাগল, তখন ইচ্ছে করত আমাদের দেশের পাঠকদের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিতে। কোনো কোনো পত্রিকাও আমার কাছে অনুবাদ চাইত। যেহেতু ইংরেজিতে মোটামুটি দখল ছিল, বাংলাটাও ভালোই জানা ছিল, ফলে ঝটপট সেটা করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু একপর্যায়ে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠলাম, অনুবাদকে সাহিত্যের বড় একটা বিষয় হিসেবে দেখতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম। তখন আমার মনে হতে লাগল বাংলাদেশে অনুবাদের নামে আসলেই বেশ একটা নৈরাজ্য, যথেচ্ছাচার এবং বাজারিয়ানা আমাদের অনুবাদের পরিমণ্ডলটিকে দূষিত করে তুলছে। সেই থেকেই একটা ভাবনা আসে আমার মনোজগতের গভীরে, অনুবাদচর্চার ক্ষেত্রে গভীর দায় ও দায়িত্ব নিয়ে একধরনের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় কি না। সেটা লেখা নির্বাচন থেকে শুরু করে তার উপস্থাপনা, সম্পাদনা, লেখক-পরিচিতি রচনা, ভূমিকা, টীকা সংযোজন এইসব কিছু মিলিয়েই। এভাবে ধীরে ধীরে নিজের মতো করে একটা দিকনির্দেশনা, একটা পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। ফলে অনুবাদটা এখন খুব সচেতন হয়েই করি। যতদিন না নিজে সন্তুষ্ট হচ্ছি ততদিন ছাপানোর বা প্রকাশের কোনো তাগিদ কাজ করে না। এখন বলা যেতে পারে যে, আমি অনুবাদটা সত্যিকারভাবেই খুব সিরিয়াসলি করি। বাস্তব চর্চার দিক থেকে যেমন, তাত্ত্বিকভাবেও সেটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা ও পড়ালেখা করি, যেন অনুবাদটাকে একটা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে আমরা এদেশের সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, যা আমাদের সামগ্রিক সাহিত্য-পরিমণ্ডলকে আরও ঋদ্ধ করবে।
এছাড়া অনুবাদকর্ম, তা সেটা বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় কিংবা বাংলা ভাষা থেকে বিদেশি ভাষাতেই হোক না কেন, একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, তার সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ, সার্বিক উন্নয়ন ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম চালিকাশক্তি। অথচ আমাদের দেশে, স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর পরেও এটা নিয়ে নেই কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতা। যতটুকু কাজ হচ্ছে তার প্রায় পুরোটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বেসরকারি পরিসরে। সেখানেও নেই কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য, শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের চর্চা। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যকে সুষ্ঠু অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে ও বৈশ্বিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা তো এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। বছর দুয়েক আগে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের পঞ্চাশজন নারীকবির কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংকলন অৎরংব ড়ঁঃ ড়ভ ঃযব খড়পশ সম্পাদনা করতে গিয়ে এই সত্যটি আরও প্রবলভাবে অনুভব করেছি আমি। বিদেশে বাংলা সাহিত্য ও দক্ষিণ এশীয় সাহিত্যের বেশ ভালোরকম চাহিদা ও একটি সম্ভাবনাময় বাজার থাকা সত্ত্বেও আমরা যে সেটাকে কাজে লাগাতে পারছি না কিছুতেই, এটি একটি জাতিগত লজ্জার বিষয়। এই ব্যর্থতার অপনোদন আর শূন্যতা মোচনে আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অবদান রাখতে চাই। নিজে সাধ্যমতো বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি, অন্যদেরকেও এই কাজে উৎসাহিত করা এবং তাঁদের অনূদিত মানসম্পন্ন রচনাকে দেশে-বিদেশে প্রকাশ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের ষোলো আনা ইচ্ছা ও আগ্রহ রয়েছে আমার।
এরই সূত্র ধরে প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। এই তো কিছুদিন আগেই ঘোষিত হলো সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার কথাসাহিত্যিক হান কাং-এর নাম। তার আগে বিশ্বজুড়েই চলেছে এন্তার জল্পনাকল্পনা, এ বছর কে পাচ্ছেন এই পুরস্কার তা নিয়ে। বাজি ধরাধরিও চলেছে রীতিমতো বলে-কয়েই। সেই উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা গ্রাস করেছে এদেশের বিদ্বৎজনদেরও। পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে নিবন্ধাদি প্রকাশের হিড়িক পড়ে গেছে প্রতিবছরের মতোই; সামাজিক মাধ্যমেও সম্ভাব্য পুরস্কারপ্রাপক সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণী করে স্ট্যাটাস ভূমিষ্ঠ হয়েছে মুহুর্মুহু। কেউ কেউ সাহস করে সঙ্গে এই প্রশ্নটিও জুড়ে দিয়েছেন যে, সাহিত্যে আমরা কবে নোবেল পাব আবার? সবেধন নীলমণি যে-একটিমাত্র পুরস্কার জুটেছিল বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যে, তার বয়সই তো এখন একশ এগারো! বস্তুত এই প্রশ্নটিকেই আরেকটু তলিয়ে দেখা এবং এর একটা সন্তোষজনক উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টাই এই নিবন্ধের উদ্দিষ্ট।
এই প্রশ্নের পিঠে আরো একটি প্রশ্ন উঠে আসে : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কি নোবেল পুরস্কার পাবার মতো লেখক কিংবা সাহিত্যকর্ম আছে আদৌ? এর উত্তর : আলবৎ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে অন্তত আরও এক ডজন সাহিত্যিকের নাম এই মুহূর্তেই করা যায়, যেকোনো মানদণ্ডেই যাঁরা নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যের বিখ্যাত তিন বন্দ্যোপাধ্যায় তো রয়েছেনই, সেইসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, শঙ্খ ঘোষ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, এমনকি সৈয়দ শামসুল হকের নামও উঠে আসতে পারে এই তালিকায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাঁরা কেউই এই পুরস্কারের মুখ দেখে যেতে পারেননি। এর প্রধান কারণ : জীবদ্দশায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মসমূহের বিদেশি তথা ইংরেজি ভাষায় ঠিকঠাকমতো অনুবাদ না হওয়া। খোদ রবীন্দ্রনাথও এই পুরস্কার আদৌ পেতেন কি না সন্দেহ, যদি তিনি নিজেই নিজের কিছু কবিতা অনুবাদ করার উদ্যোগ না নিতেন এবং যদি ঘটনাচক্রে বিখ্যাত বিলেতি চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রদেনস্টাইনের সঙ্গে পূর্বপরিচয় না থাকত তাঁর। কেননা এই রদেনস্টাইনই প্রখ্যাত আইরিশ কবি ইয়েটসের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতার পাণ্ডুলিপিখানি। ইয়েটস সেগুলো পড়ে ও কবির কণ্ঠে সেসবের অপূর্ব আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রকাশিতব্য গীতাঞ্জলি গ্রন্থের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেন, যা আমরা জেনেছি, কবির নোবেল পুরস্কারলাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ধান ভানতে এই রবির গীত গাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য : অনুবাদ ও বৈশ্বিক যোগাযোগের ওপর জোর দেওয়া, যে-দুটোর অভাবে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের আর কারো ভাগ্যে, যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, এই নোবেলের শিকেটুকু ছিঁড়ল না। প্রথমে আসা যাক অনুবাদের বিষয়টিতে। নোবেল পুরস্কারটি যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার, যার পরিসর বিশ্বজুড়েই বিস্তৃত, সেহেতু এর যাবতীয় কার্যকলাপ একটি মোটামুটি সর্বজনবোধ্য আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়; বলাই বাহুল্য সে-ভাষাটি ইংরেজি। ফলত নোবেল পুরস্কারের জন্য আমাদের কোনো সাহিত্যিককে প্রাথমিকভাবে বিবেচিত হতে হলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মসমূহকে ইংরেজিতে এবং সম্ভব হলে আরো দুয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বভাষাতেও অনূদিত হওয়া আবশ্যক। তবে এই অনুবাদ যার-তার দ্বারা, যেন-তেন প্রকারে সংঘটিত হলে চলবে না; তাকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত ন্যূনতম ভাষামান ও প্রকাশরীতির নিরিখে প্রকাশক, সম্পাদক, সমালোচক সম্প্রদায়, সর্বোপরি বৃহত্তর বোদ্ধা পাঠকশ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
তেমন অনুবাদক, যার বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই রয়েছে সমান দখল ও দক্ষতা, বিশেষ করে সমকালীন ও সৃজনশীল ইংরেজিতে লিখবার সহজাত ক্ষমতা, খুব বেশি নেই এখনকার বাংলাদেশেÑএই কথাটি আমাদের সর্বাগ্রে স্বীকার করে নেওয়াটাই তাই মঙ্গলজনক। তাহলে করণীয় কী? করণীয় এই যে, আমাদেরকে এজন্য শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও তাকাতে হবে। ঐতিহাসিক কারণেই পাশের দেশ ভারতে উল্লিখিত মান ও যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদকের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে আমাদের নজরটা সেদিকেও প্রসারিত করতে হবে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের অনুবাদকেরাই আমাদের সাহিত্যের অনুবাদ করছেন অনেক বেশি এবং সেগুলো বিশ্বের বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত, প্রশংসিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে পুরস্কৃতও হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে দুজন অনুবাদক অরুণাভ সিনহা ও ভেঙ্কটেশ রামাস্বামীর কথা বলতেই হয়, যাঁদের দক্ষ হাতে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী, শহীদুল জহির, শাহাদুজ্জামান, মশিউল আলম, মাসরুর আরেফিনের মতো আমাদের অনেক মেধাবী লেখক অনূদিত হয়ে চলেছেন। এর বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও অনেকে রয়েছেন যাঁরা এই কাজের যোগ্যতা রাখেন এবং তাঁদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা করেও চলেছেন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী শবনম নাদিয়া, মাহমুদ রহমান প্রমুখ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের একাধিক শক্তিমান লেখকের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। এছাড়া ক্লিন্টন বুথ সিলি, উইলিয়াম রাদিচে, হান্স হার্ডারের মতো আরো অনেক বিদেশিও রয়েছেন যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেমে পড়ে এই ভাষাটাকে রপ্ত করেছেন খুব যত্ন করে, যা কাজে লাগিয়ে তাঁরা আমাদের অনেক মূল্যবান সাহিত্য ইতোমধ্যেই ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এঁদের সবাইকে উপযুক্ত সম্মান ও সম্মানীর বিনিময়ে যদি সুপরিকল্পিতভাবে, সত্যিকার পেশাদারত্বের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি অনুবাদ প্রকল্পে যুক্ত করার কথা ভাবা যায়, তাহলে অবশ্যই সেটি আমাদের সাহিত্যের জন্য সুনাম ও সুফল বয়ে আনবে।
তবে বলাই বাহুল্য এটি কোনো ব্যক্তির কাজ নয়। এর পেছনে অবশ্যই রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগকে ক্রিয়াশীল হতে হবে। আমাদের দেশে বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থাসমূহ ইত্যাদির সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগেই কেবল এ-ধরনের একটি সুদূরপ্রসারী প্রকল্প গ্রহণ ও তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এর জন্য সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন করে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির তত্ত্বাবধানে সেটি পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকাশনাসংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, যোগাযোগ রক্ষা ও বৈশ্বিক বিধিবিধানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্তিও থাকা দরকার এই প্রকল্পের সঙ্গে। বিশেষত ফিবছর অনুষ্ঠিত ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় অংশগ্রহণের সময় আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত বিদেশি প্রকাশক, সম্পাদক, সাহিত্যের এজেন্ট প্রমুখের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে তোলা, এবং তাদের কাছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও তাদের সৃষ্টিকর্মকে সম্যকভাবে তুলে ধরা। এছাড়া বিশ্বের বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকদেরকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন, উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। পাশাপাশি নিজেরাও, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে নানাবিধ সাহিত্য উৎসব, সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত লেখক, প্রকাশক, অনুবাদক, সমালোচক, সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে তাঁদের সঙ্গে ভাববিনিময় ও কার্যকর সৃজন-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
মোদ্দা কথা এ-ই যে, আমরা সবাই জানি আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে, রয়েছে গর্ব করার মতো অনেক অর্জনও। কিন্তু সেই ঐতিহ্য ও অর্জনকে শুধু পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায় নয়, সাধারণভাবেই বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানো, বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা বিশাল ও উৎসুক ভোক্তাশ্রেণির কাছে পৌঁছানো আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বের অংশ। বিশ্বসাহিত্য ও তার বিপুল জ্ঞানকাণ্ডের নিয়মিত অনুবাদের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার সমৃদ্ধি ঘটাব, তেমনি নিজেদের গৌরবময় সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে মানসম্পন্ন অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির করাটাও আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বই কি। এইভাবে জগৎকে আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি, মূল্যবান মানস-ঐশ্বর্যের সন্ধান দেওয়া এবং বহির্বিশ্বে দেশের বৌদ্ধিক ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুবাদসংশ্লিষ্ট বহুবিধ কর্মযজ্ঞ শুরু করা এখন সময়ের দাবি।