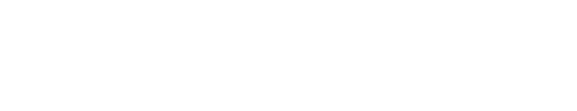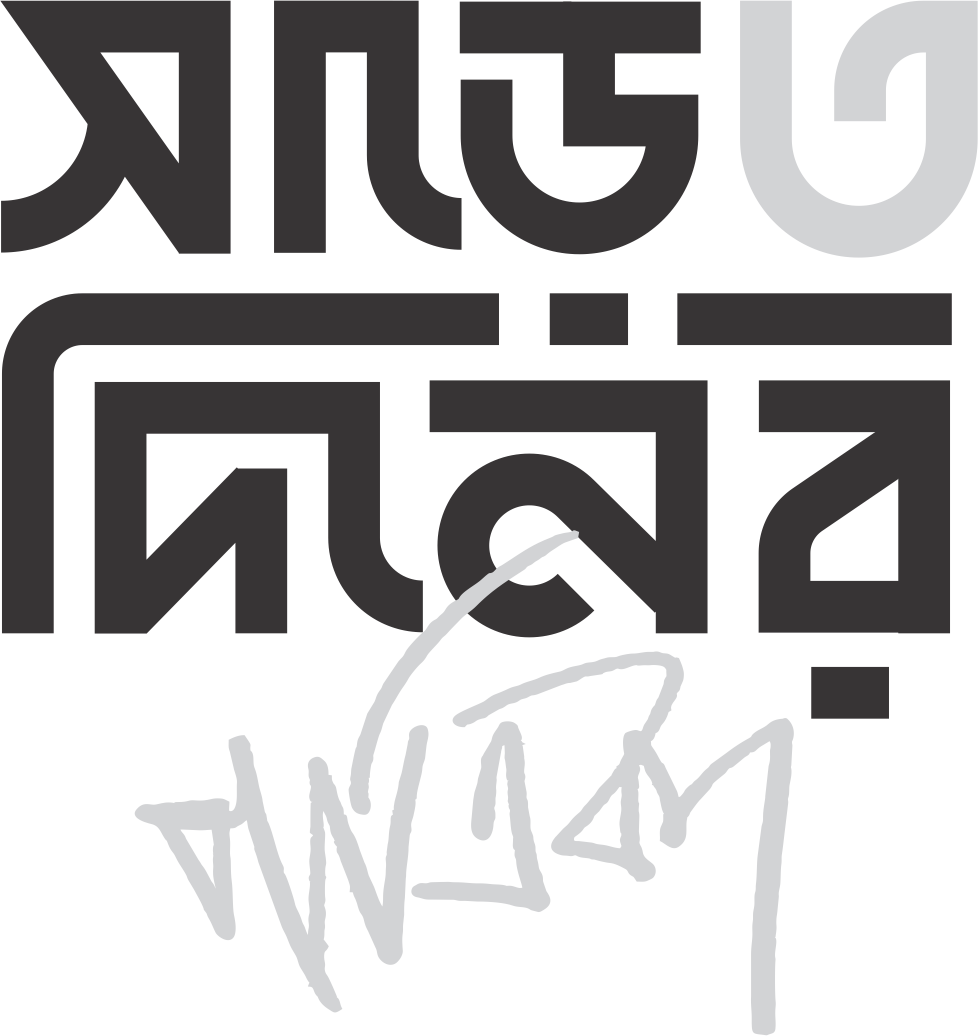আনু মুহাম্মদের জন্ম ১৯৫৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। পুরো নাম আনু মুহাম্মদ আনিসুর রহমান হলেও আনু মুহাম্মদ নামেই অধিক পরিচিত। মার্কসীয় অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষক বলে ইতোমধ্যে তিনি ব্যাপক পরিচিত। আনু মুহাম্মদ নাম নিয়ে ১৯৭৩ সাল থেকে শাহাদৎ চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’য় নিয়মিত লিখতে থাকার মধ্য দিয়ে তিনি লেখক হিসেবে বাংলাদেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করেন ১৯৮২ সালে এবং ২০২৩ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর নেন। অর্থনীতি বাদেও নৃতত্ব বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পড়িয়েছেন। অধ্যাপনা বাদেও তিনি একাধিক গ্রন্থের লেখক। অনুবাদ করেছেন ওরিয়ানা ফালাচ্চির ‘হাত বাড়িয়ে দাও’। এছাড়া ‘সর্বজনকথা’ নামে একটি সাময়িকির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করছেন। সাড়ে তিন দিনের পত্রিকার জন্য তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমিরুল আবেদিন।
২০২৪-জুলাইয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ফলে সরকারের পতন ঘটেছে, এটাকে গণঅভ্যুত্থান বলবেন না-কি বিপ্লব বলে সংজ্ঞায়িত করবেন?
আনু মুহাম্মদ : চব্বিশের জুলাই-আগস্ট সরকারের পতন মূলত ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফল। এটিকে অভ্যুত্থান বলছি কারণ, কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাত ধরে এ আন্দোলন শুরু হয়নি। সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই আন্দোলন। আমরা দেখেছি, আন্দোলন দমনের জন্য শেখ হাসিনা যে হিংস্র পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা-ই এ আন্দোলনকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ দেয়। আমরা জানি, সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের পরিপত্র আদালত বাতিল করে দেওয়ার পরপরই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দাবিটি নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ছিল। ২০১৮ সালেও কোটা সংস্কারের আন্দোলন হয়েছিল। তখনও তারা কোটা বাতিল চায়নি। এবারও তারা কোটার যৌক্তিক সংস্কার চেয়েছিল। শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলন জনগণের সহানুভূতিও অর্জন করে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমেই আন্দোলনকে সৃজনশীলতায় রূপ দেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ছ্যাত্র সংগঠন ও অন্য অঙ্গ সংগঠনের কর্মীদের দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ চালায়। শিক্ষার্থীদের অবজ্ঞা এবং অপমান করেও শেখ হাসিনা বক্তব্য দেন। শুধু তা-ই নয়, পুলিশও শিক্ষার্থী-জনতার ওপর আক্রমণ শুরু করে। ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদসহ সাতজন নিহত হওয়ার পর জনরোষ আর দমানোর মতো পরিস্থিতিতে থাকেনি। আন্দোলনের একপর্যায়ে যোগ দেয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাও। সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।
আমরা দেখেছি, প্রথম দিকে সরকার শিক্ষার্থীদের আদালতের পথ দেখাল। আদালতের ওপর সরকারেরও হাত নেই—এই অজুহাত এলো তাদের তরফে। কিন্তু আন্দোলন তীব্র হলে আদালতের রায়ের তারিখ এগিয়ে আনা হলো। অর্থাৎ এই আন্দোলনকে সরকার শুরু থেকেই খেলাচ্ছলে সামাল দিতে চাচ্ছিল। তত দিনে দেশের সবাই বুঝে গেছে, এসবই আসলে ভাঁওতাবাজি। এই খেলাচ্ছলে তত দিনে ২০০ তাজা প্রাণ ঝরে গেছে। এর আগেও বাংলাদেশে অনেক গণআন্দোলন হয়েছে। এত অল্প সময়ে এত প্রাণ ঝরে যায়নি কখনও। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি নিম্ন আয় ও সাধারণ জনতাও নিহত হতে থাকলেন। বিদ্রোহ থামেনি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসার আশ্বাস দেওয়া হলো। অন্যদিকে আটক করা হলো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সমন্বয়কদের। আবারও শুরু হলো দমন-পীড়নের মাধ্যমে আন্দোলনকে থামানোর চেষ্টা। ২ আগস্ট আইনজীবী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ডাক্তার, শ্রমজীবী মানুষ, রিকশাচালক সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন দ্রোহযাত্রায়। তখন থেকে সরকার পতনের ১ দফা দাবি সর্বজনের প্রবল দাবি হিসেবে দ্রুত আরও বিস্তৃত হতে শুরু করে। ইন্টারনেট পরিষেবা বিঘ্নিত থাকায় অনেক তথ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধু জানা গেছে, তত দিনে আরও ৫০০-৬০০ মানুষ নিহত হয়েছে। সরকার পরিস্থিতি সামলাতে আরও নির্মম হয়ে ওঠে। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। স্বৈরাচারের ট্র্যাজেডি, তারা বুঝতে পারে না তাদের পতন অনিবার্য কখন হয়ে ওঠে। অবশেষে সেনাবাহিনীও সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে তাল মেলাতে অস্বীকৃতি জানালে শেখ হাসিনাকে ভারত পালাতে হলো। এসব কিছুই সফল হয়নি। কারণ জনগণই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসের পূর্বতন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, দেশের মানুষই বরাবর রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য রাজপথে নেমেছে। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।
বিপ্লব বা আন্দোলনের পরে দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন কি?
আনু মুহাম্মদ : দেশে একেক সময় একেক আন্দোলন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আগেও আন্দোলন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে আমরা দেখেছি, ধর্মীয় দলগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তারা প্রায়ই বিপ্লবের কথা বলতো। অনেক দল সমাজতন্ত্রের কথা বলতো এবং বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতো। একাত্তরের পর সশস্ত্র সংগ্রামের চেতনা পরবর্তীতে সামরিক শাসনের অধীনে দুর্বল হয়ে যায়। আমরা আশির দশকের সময় এরশাদবিরোধী আন্দোলন দেখেছি। আমার ধারণা, আশির দশকের আন্দোলন অনেক বেশি পরিপক্ব ও সম্ভাবনাময় ছিল। ওই আন্দোলন শুধু স্বৈরাচারের পতন নয়, সামাজিক পরিবর্তনের বা রূপান্তরের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। ওই সময় শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়, নারী জাগরণ দৃশ্যমান হতে শুরু করে। এমনকি দলীয় ভিত্তিতে কিছু ভাগ হয়নি। আন্দোলনের জনভিত্তি অনেক শক্তিশালী ছিল। তবে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগেনি। পরে যখন সবকিছু বাদ দিয়ে এক দফার আন্দোলন শুরু হয়। তখন তিন দলীয় জোটের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে সেটার বাস্তবায়ন হলে বর্তমানে যে সংকট সেটা আর হত না। একানব্বই থেকে নতুন ধারা তৈরী হয়। তখন বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হয়েছিল। সেই থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়েই আন্দোলন হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোও সেদিকেই ঝুঁকে আছে। এবার আসা যায় শিল্প-সংস্কৃতির কথায়। মানুষের যাপিত জীবনই সংস্কৃতির অংশ। তাই শিল্প সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের ভিত্তিতে। কিন্তু এ মুহূর্তে গোটা দেশে মতাদর্শিক বিভাজন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চলছে। সমস্যা হলো, জননিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিবাচক প্রভাব ছড়াতে পারছে না। আশার কথা হলো, সাহিত্যের মাধ্যমে কিছুটা হলেও তা পূরণ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছা ব্যাতীত বাস্তবে আমরা সমাধান পাবো না।
পৃথিবীতে বিগত দিনে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে নানান দেশে, এই বিপ্লবের ফলে সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নানাভাবে পরিবর্তন এসেছিল- আপনার দৃষ্টিতে সেইসকল বিপ্লব বা অভ্যুত্থানকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন- বিস্তারিতভাবে বলবেন কি?
আনু মুহাম্মদ : বিপ্লবের ক্ষেত্রে মূলত নেতৃত্ব থাকে। পৃথিবীতে বিগত দিনে নানা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে এবং তা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিপ্লবের প্রভাব শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বড় বদল এনেছে। যেমন রুশ বিপ্লবের পর সিনেমার যে জাগরণ এবং ফরাসি বিপ্লবের পর অস্তিত্ববাদি দর্শনের চর্চার ব্যবহার বেড়েছে। বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা নামে আমার একটি বই রয়েছে। সেখানে আমি দেখিয়েছি কীভাবে কিউবা আমাদের কাছে অনেক প্রাসঙ্গিক। ভৌগোলিকভাবে অনেক দূরে থাকা কিউবার প্রাসঙ্গিকতা আমি সেখানে তুলে ধরেছি। রুশ বিপ্লবের যে রূপ, কিউবার বিপ্লবের একই রূপ ছিল এমনটি বলা যাবে না। একেকটি বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ওই ভৌগোলিক চিত্র বা রুচির নিরিখে মতাদর্শ গড়ে তোলে। মতাদর্শিক আবহ একসময় দর্শনে রূপ নেয় এবং তা শিল্প-সাহিত্যে বিচ্ছুরিত হয়। সাহিত্যে ও শিল্পের জাগরণ ঘটে কারণ সাংস্কৃতিক অর্থনীতির একটি বড় প্রভাব রয়েছে বিপ্লবকে সফল করার ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে এখনও বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে অনেকে জানছে, পড়তে শুরু করেছে ইতিহাস। এ জানার চর্চাটুকু পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকলেই ইতিবাচক ফল মিলবে।
বিপ্লব একটা দেশের মানুষের মনজগতে কিরকম প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন?
আনু মুহাম্মদ : যে কোনো বিপ্লব যদি সফল হয় তাহলে নতুন করে স্বপ্নের জাল বিস্তার করে দেশের মানুষের মনে। মানুষের মধ্যে নতুন করে আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। এমনটি সবখানেই। উপনিবেশ থেকে মুক্তির বিপ্লব থেকেই তো বিউপনিবেশায়ন। তবে এ বিউপনিবেশায়ন অঞ্চলভেদে আর শোষণের রূপভেদে আলাদা। আফ্রিকায় দাসপ্রথা ছিল উপনিবেশের শোষনপ্রক্রিয়া। উপমহাদেশে তা ছিল সম্পদ লুটের মাধ্যমে। ফলে দুই অঞ্চলের বিউপনিবেশায়ন আলাদা। তবে বিপ্লব পৃথিবীর যে প্রান্তেই ঘটুক না কেন, সবসময় মানুষের শোষিত থাকার ফলে যে চাহিদা ছিল তা পূরণ করার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নটা সবার প্রত্যাশার অগ্রভাগে থাকে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিশ্চিত হবে জেনে মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জননিরাপত্তা—এ তিনটি বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিতে পারে। প্রতিটি বিপ্লবই ক্ষণস্থায়ী। এ জন্যই বলা হয়, বিপ্লব তুমি দীর্ঘজীবী হও। অভ্যুত্থানের পর বিপ্লবের ধারাবাহিকতা টেনে নিয়ে যেতে হয় রাজনৈতিকভাবে। মানুষের রাষ্ট্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে অনেক। তা পূরণের জন্য তাদের অবশ্যই নির্ভর করতে হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি। অভ্যুত্থানে মানুষ যুক্ত হয় কারণ তারা জানে, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য তাদের সড়কে নামতে হবে। এ জন্যই অভ্যুত্থানের পর সমাজের মানুষ বিপ্লবী নেতাদের রাজনৈতিক পরিপক্বতার ওপর আস্থা রাখতে চায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ ধারাবাহিকতা ও পরিপক্বতা ধরে রাখতে না পারায় অনেক বিপ্লব বেহাত হয়েছে।
পুরনো সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা থেকে বিপ্লব সংঘটিত হওয়া দেশকে কতটা নতুন দিকে ধাবিত করে বলে মনে করেন?
আনু মুহাম্মদ : পুরোনো সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা বলে কিছু নেই। কারণ সংস্কৃতি চিরবহমান। সময়ের নিরিখেই সংস্কৃতির বদল ঘটে। এই বদলটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা জরুরি। শিল্প-সাহিত্যের এক ধরনের প্রভাব এক সময় ছিল যখন যোগাযোগের এত মাধ্যম ছিল না। এখন টিভি, অনলাইন প্লাটফর্ম এগুলো চলে আসায় সচরাচর অনেক ধরনের চিন্তাধারা দেখা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না থাকায় মতাদর্শিক বিভাজন বেড়েই চলেছে। বিভাজন বেড়ে যাওয়ার কারণে ভালো উদ্যোগগুলোও অনেক ক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছে। কারণ পদে পদে প্রশ্ন এবং বিতর্ক সংস্কার কিংবা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ তারা পুরোনোর সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন করে নিজ ঐতিহ্যকে ধারণ করতে পারে।
মানুষের বুদ্ধির মুক্তিতে বিপ্লবের ভূমিকা কতখানি?
আনু মুহাম্মদ : বুদ্ধির মুক্তিতে সংক্রান্তি মেলে। আসলে বিপ্লবকে সবসময় রাজনৈতিক আঙ্গিকে দেখা হয়। যে কোনো উদ্ভাবনই এক ধরনের বিপ্লব। মানুষের সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে সম্ভাবনা তৈরি করা এক ধরনের বিপ্লব। আমরা দেখেছি, বিগত শতকে অধিকাংশ সাহিত্যিক আন্দোলন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। রাজনীতিতে সৃজনশীলতা যুক্ত করেছে শিল্প-সাহিত্য। এ মিথস্ক্রিয়া রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যই ইতিবাচক।
সোভিয়েত বিপ্লবের যেমন দার্শনিক ভিত ছিল, একইভাবে ফরাসী বিল্পবেরও ছিল- এই দুই বিপ্লব সারা পৃথিবীতে নানানভাবে প্রভাব ফেলেছিল- এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বলবেন কি?
আনু মুহাম্মদ : এ বিষয়ে আমার সম্পাদিত সর্বজনকথার ২০১৭ সালের আগস্ট-অক্টোবর সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। রুশ বিপ্লবের ফলে ইতিবাচক-নেতিবাচক দুটো দিকই দেখা গিয়েছিল। এ বিপ্লবের দার্শনিক ভিত ছিল বলেই কৃষি, শিল্পখাত, কর্মসংস্থান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংবিধান এমনকি সাহিত্যের ধারায়ও প্রভাব পড়েছিল। ফরাসি বিপ্লব অন্যদিকে স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রচার-প্রসারে মানুষ আবার নিজেকে নতুন আঙ্গিকে ভাবতে শুরু করে। এসব ইতিবাচকতা আজও গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করে। এ জন্য পৃথিবীর কোথাও বিপ্লব হলে এ দুটো বিপ্লবের সঙ্গে প্রায়শই তুলনা দেওয়ার চেষ্টা হয়। এমনটা হয় কারণ এ দুটো বিপ্লব সর্বব্যাপী হয়েছে। এমনকি কিউবার বিপ্লবটিতেও এ বিপ্লবের ধারাবাহিকতা ও সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি দেশে পটপরিবর্তনের পরও রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।
তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে বিপ্লব বা অভ্যুত্থান কতটা পরিবর্তন করে সেই দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতিতে?
আনু মুহাম্মদ : যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুসংহত করা যায় তাহলে বিপ্লব বা অভ্যুত্থান অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তবে অশান্তি বা সহিংসতাই যে পরির্তন আনতে পারে তা কিন্তু নয়। আন্দোলনে মানুষ কতটা জমায়েত হবে বা মানুষকে কতটা আকর্ষণ করতে পারবে সেটার উপরই নির্ভর করে এর সাফল্য বা পরিবর্তন। পাকিস্তান আমলে যেটা হয়েছিল, মানুষকে অনেক বেশি সম্পৃক্ত করা গেছে বলেই গণঅভ্যুত্থান করা গেছে। এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও কিন্তু মানুষকে অনেক বেশি আকর্ষণ করা গেছে। সেখানে হরতাল একটা মাধ্যম হতে পারে। মূল কথা হল, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ আন্দোলনে কতটা যুক্ত হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করে কতটা সফল হবে বিপ্লব পরবর্তী পরিবর্তন। মূলত রাষ্ট্রে বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের বাইরে আনতে পারলে এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিতের পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেই বড় পরিবর্তন আসবে।
বিপ্লবের সাহিত্য কতটা জনমুখি হতে পারে- যা চর্চায় মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়?
আনু মুহাম্মদ : বিপ্লবের সাহিত্য তো আসলে হয় না। সাহিত্য বিপ্লবের প্রচারপত্র হয়ে ওঠে। সময়ের তাগিদেই তা রূপ নিতে পারে। মূলত মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভাবনার চর্চাকে গুরুত্ব দিতে পারলেই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।