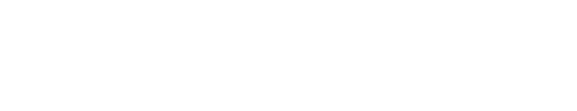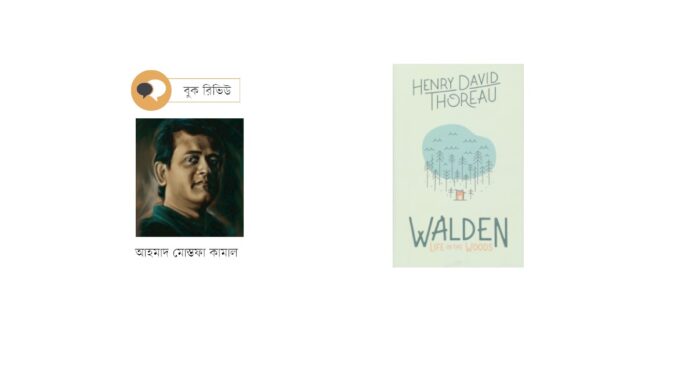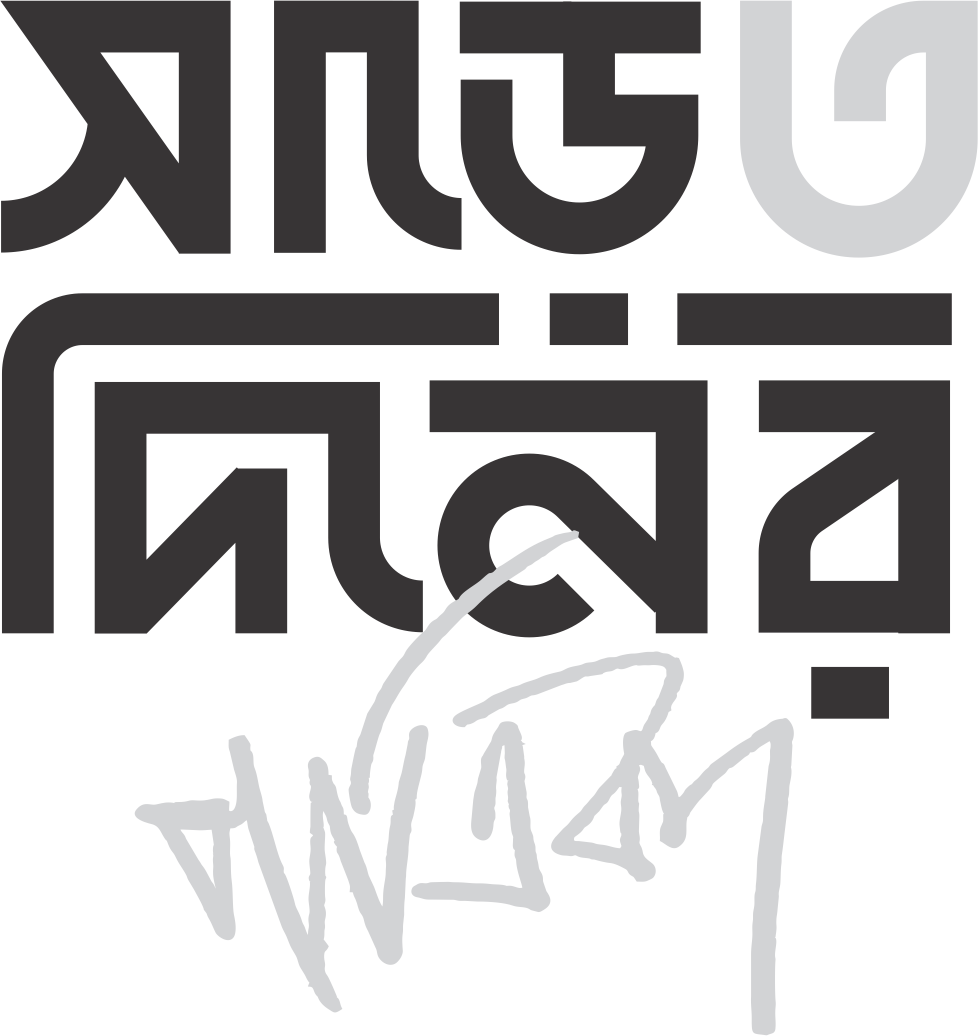সম্প্রতি হেনরি ডেভিড থরোর বিশ্ববিখ্যাত বই ‘ওয়াল্ডেন’ পড়ছিলাম। পড়ছিলাম । গত এক মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে শুরু করে ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড় বাঁকবদল ঘটে গেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আমরা একটি স্বৈরাচারী সরকার কাঠামোকে উৎখাত করতে পেরেছি। এজন্য বহু মানুষ শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন অনেকে। আমাদের অবকাঠামোগত ক্ষয়-ক্ষতিও কম হয়নি। অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। অর্থাৎ তাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের এমন পরিস্থিতিতে আসলে বই পড়ার মতো মানসিকতা ছিল না। আমি নিজে একজন শিক্ষক। আমার অনেক শিক্ষার্থী রাস্তায় আন্দোলন-সংগ্রামে নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছিল। আমার ছেলেও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আমিও নানাভাবে আন্দোলনে অবদান রাখার চেষ্টা করেছি। ওই সময়টার কথা ভাবলেও আমি হিমশিম খাই। সারারাত একফোঁটা ঘুম হতো না। সারাদিন আমি ওদের কথাই চিন্তা করতাম। আন্দোলনে যারা এখন লড়াই-সংগ্রামে ব্যস্ত তারা সবাই কি জীবন্ত ফিরে আসবে? যে যার মায়ের কোলে কি ফিরে আসতে পারবে? এমনটিই ছিলো আমার ভাবনা। সংগত কারণেই ওই সময় বই পড়ার মতো মানসিকতা আমার ছিলো না। যাহোক, জুলাই আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে আমি ‘ওয়াল্ডেন’ বইটা পড়ছিলাম।
বইটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে থরো সম্পর্কে জানা দরকার। থরো একজন আমেরিকান। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে তিনি ‘ওয়াল্ডেন’ বইটা লিখেছিলেন। হার্ভার্ডে গ্র্যাজুয়েশন শেষে তাঁর মনে হলো, নাগরিক জীবনের মধ্যে জীবনের সত্যিকার অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই অর্থ খুঁজতে হলে প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হবে। ভাবনা অনুযায়ী তিনি ওয়াল্ডেন নামে একটি জায়গায় গেলেন। জায়গাটিকে ঠিক ঘন অরণ্য-ছায়াবৃত মনে হলেও আদপে তা অরণ্য ছিলো না। থরো সেখানে অবকাঠামো নির্মাণের রসদ নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো ব্যবহার করে গাছপালা কেটে এক রুমের একটা ছোট বাড়ি নির্মাণ করেন। ওয়াল্ডেনে তিনি দুই বছর ছিলেন। ওই দুই বছরের অভিজ্ঞতাই তিনি বইটিতে লিপিবদ্ধ করেন। এই দুই বছরে তাঁর জীবন কীভাবে কেটেছে তা নিয়েই লিখেছেন।
বইটিতে তিনি অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ করতে চাননি; বরং জীবনের অর্থকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আমারও মনে হয়েছে, নাগরিক জীবন আসলে আমাদের এক ধরনের ধন্দে ফেলে রাখে। এই যেমন আমরা ঢাকায় বাস করি। ইট-পাথরের শহর বলে পরিচিত ঢাকায় শত চেষ্টায়ও আপনি একটা গাছ কিংবা পাখি দেখতে পাবেন না। বন্যপ্রাণী কেন সামান্য কাকই এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নাগরিক জীবন আমাদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে। তাই আমরা প্রকৃতির সম্পৃক্ততা কিংবা জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। এর কারণটি একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি। এ বিষয়ে বইটিতেই লেখা আছে। কিন্তু আমি কেন এ কথা বলছি তা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।
খেয়াল করলে দেখবেন, অন্যান্য জীব যে ধরনের জীবনযাপন করে তা সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ধারিত। প্রকৃতির নির্ধারিত নিয়মের গণ্ডিতেই তারা জীবনযাপন করে। অন্য কোনো জীব মানুষের মতো শস্য ফলায় না। হ্যাঁ, অন্য প্রাণীও নিজেদের ঘর বানায়। কিন্তু তার রসদ তারা প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করে। খাদ্যের জন্য তাদের বাড়তি চিন্তা করতে হয় না। কালকের দিনের কথা ভেবে তাদের সঞ্চয় করতে হয় না। অর্থাৎ প্রকৃতি তাদের খাবার, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। প্রকৃতির নির্মমতার মধ্যেই কীভাবে তাকে বাঁচতে হবে তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং প্রাণিজগত তা মেনে নিয়েছে।
এখানে তো একটা প্রশ্ন আসেই। পিঁপড়া কিন্তু খাবার সঞ্চয় করে রাখে।
এটাও আসলে প্রকৃতিই নির্ধারণ করেছে। পিঁপড়ারা জানে তাদের অস্তিত্বের তাগিদে খাদ্য সঞ্চয় করতে হবে। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনও চলমান এবং তাদের এই সঞ্চয়ী প্রবণতার পেছনে অবশ্যই কারণ রয়েছে। তবে এটুকু নিশ্চিত, তারা যদি খাদ্য সঞ্চয় না করে তাহলে বিশেষ কোনো ঋতুতে তাদের না খেয়েই থাকতে হবে। এমনটা অন্য প্রাণীর উদাহরণ টেনে জীববৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করা যায়। বাবুই পাখি বাসা বানায়। বাঘ কিন্তু তা করে না। এই যে প্রকৃতির নির্বাচিত জীবনপ্রণালী, এমনটি প্রাণিজগত মেনে নিয়েছে।
মানুষও প্রাণী। তবে প্রজাতির নিরিখে তারা অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। এই প্রাণী প্রকৃতি নির্ধারিত জীবনকে মেনে নিতে রাজি ছিলো না। তারা ভাবলো, এভাবে আসলে টিকে থাকা সম্ভব নয়। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একদম প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতি থেকেই তারা খাদ্য সংগ্রহ করত। গাছের ফলমূল তো বটেই, অনেক সময় তারা শিকারও করত। আগুন আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত তাদের কাচা মাংসই খেতে হয়েছে। এগুলো প্রকৃতিই তাদের জন্য নির্ধারণ করেছে। একসময় তাদের মনে হলো, এভাবে চলতে পারে না। তাই তারা শস্য উৎপাদনে মনোযোগী হলো। ‘সেপিয়েন্স’ নামে একটি বইয়ে বলা হয়েছে, ‘মানুষ প্রথমে কাউকে পোষ মানায়নি।’ আমরা তো বলি, মানুষ বন্যপ্রাণীকে প্রয়োজনভেদে পোষ মানিয়েছে। কিন্তু আদপে লেখক বলছেন, মানুষকে প্রথম পোষ মানিয়েছে খাদ্যশস্য। তাঁর মতে, আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদন না করলে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। তখন থেকেই গমচাষ শুরু। তবে ফসল এমন এক জিনিস যে শুধু বীজ বুনলেই হয় না। ফসলের পরিচর্যা প্রয়োজন হয়। ফসলের পরিচর্যা শেষে তা আরোহন করে প্রস্তুত করতে হয় এবং অবশেষে তা খাদ্যে রূপ নেয়। আর এজন্যই খাদ্যরসদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দিলো।
মানুষের যাযাবরবৃত্তি বন্ধ হলো যখন থেকে তারা শস্য ফলাতে শুরু করলো। গম মানুষকে পোষ মানালো। তোমরা বসত করো এবং নিজেদের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করো। আসলে প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত জীবন থেকে মানুষ বেরিয়ে এসেছে। মানুষের চাহিদা বেড়েছে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর এভাবেই মানুষের বিবর্তন ঘটেছে।
আজ আমরা সামান্য ফোনের কাছে বন্দি। সম্প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়। তখন অনেকেরই দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট আসেনি। ইন্টারনেট শব্দটাও শুনিনি। পরবর্তীতে শব্দটা শুনলেও জিনিসটা কী তা বুঝে উঠতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার আগে ইমেইল বলে একটা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেটাও পঁচানব্বই কি ছিয়ানব্বই সালের কথা। অথচ এখন ইন্টারনেট ছাড়া কিছু করার কথা ভাবতে গেলেও লোকে পাগল ঠাউরাবে। যোগাযোগের এত সহজ মাধ্যম না থাকার পরও কি মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি? থরো মূলত এই জায়গাটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা আসলে বন্দি হয়ে গেছি সভ্যতার পালাবদলে। এখন মুক্তির জন্য তার মতে নিসর্গের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে নিজেই ফসল ফলাতে হবে। তিনি বলেছেন, ‘আমি অরণ্যের গভীরে যাব, জলের পরিধি মাপবো।’ মূলত এই অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি বইটি লিখেছেন। বইটা এখনও পড়া শেষ হয়নি। পড়ার মধ্যেই রয়েছি।
প্রশ্ন : বইটি পড়ার সময় কি আপনার মনে হয়েছে যে আমিও এমন একটা জীবনযাপন করতে চাই?
আহমাদ মোস্তফা কামাল : জীবনে দীর্ঘ একটি পথ তো পাড়ি দিয়েছি। অনেকের জীবনী পড়ার সুযোগ হয়েছে। অনেকের জীবনের কথা দর্শন জানতে পেরেছি। এখন বয়স বেড়েছে। আর এই বয়সে একটা বিষয় বুঝেছি, একটা মানুষ অন্য কারো ভাবনার অনুকৃতি করতে পারেন না। অনুকৃতি তো করতে পারেননই না, নিজের জীবনেও তা প্রয়োগ করতে পারেন না। থরো আসলে নিজের স্বতস্ফূর্ত ভাবনা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি তো আসলে পড়তে চেয়েছি। তার মতো কিছু করার কথা ভেবে বইটি পড়িনি। তাই স্বতস্ফূর্ততা এখানে নেই। আমি বুঝতে পেরেছি তার এই ভাবনা আমি কপি করতে পারবো না। কিন্তু পড়তে ভালো লাগছে। থরো একটি জায়গায় লিখেছেন, ‘মৃত্যুর সময় অন্তত আমার যেন মনে না হয়, আমি বাঁচতে পারিনি।’ এইযে আমরা বেঁচে আছি তা যদি একবার ভেবে দেখি তাহলে কি আসলেই বেঁচে আছি? এইযে আমাদের ক্ষুদ্র জীবন, এই জীবনটাকে নিয়ে আমরা কি করলাম? বেঁচেই তো ছিলাম। উনি আসলে বলতে চেয়েছেন, ‘আমার যেন মনে না হয় আমি বাঁচিনি। আর এজন্যই আমি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ নিজের ভাবনার বিষয়ে তিনি স্বচ্ছ ছিলেন।
থরোর বই পড়ার আগে আমি তলস্তয়ের ‘কনফেশন’ পড়ছিলাম। এর আগেও তলস্তয়ের গল্প উপন্যাস পড়া। কিন্তু এই উপন্যাসটি আচমকাই পেয়ে গেলাম। আমি আসলে দেখছিলাম, কনফেশন নামে কারা কারা লিখছেন। আচমকা আবিষ্কার করি, তলস্তয় কনফেশন নামে লিখছেন। দেখে ভীষণ অবাক হলাম। এখন তো ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই বই পাওয়া যায়। বইটা আমি ইন্টারনেট থেকেই ডাউনলোড দিয়ে পড়তে শুরু করলাম। স্ক্রিনে অবশ্য আমার পড়তে অসুবিধা হয়। তাও পড়তে শুরু করলাম। বইটিতে আমি প্রায় ডুবে গেলাম।
তলস্তয়ের বয়স যখন পঞ্চাশ ততদিনে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ লেখা হয়ে গেছে। ততদিনে তিনি প্রতিথযশা এক রুশ লেখক। জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়ায় জমিদারিও পেয়েছেন। একজন মানুষের সমাজে যা কিছু দরকার তার সবকিছুই তলস্তয়ের ছিল। এমন সময় তিনি একজন লেখকের মৃত্যুদণ্ড প্রত্য¶ করলেন। ঐ লেখক রাষ্ট্রদ্রোহী সাহিত্যচর্চা করেছিলেন। এই শাস্তি কার্যকর হতে দেখার পর তলস্তয়ের ভাবনার জগত গেল পালটে। তলস্তয়রা তিন ভাই ছিলেন। এক ভাই আটাশ বছর বয়সে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। আরেকজন সম্ভবত চৌত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। এই দুটো মৃত্যু তাকে এতটাও স্পর্শ করেনি। কিন্তু ওই লেখকের মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে। তাত্বিক জায়গা থেকে জীবন এতটাই সম্ভাবনার বাইরে যে মানুষের আয়ুর নিশ্চয়তা নেই। আমার নিজের জীবনেরই তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাহলে কেন আমরা এতসব করছি? এই চিন্তা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এই ভাবনার কারণে তিনি দ্রুত আত্নহত্যার কাছাকাছি চলে গেলেন। তার মনে হলো, আত্নহত্যা ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায় নেই।
প্রশ্ন : অর্থাৎ তিনি তার জীবনের কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে এমনটি ভাবছিলেন?
আহমাদ মোস্তফা কামাল : হ্যা। তখন তিনি নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি তখন বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বাণী পড়ছেন। তারও বিস্তারিত বর্ণনা তিনি ‘কনফেশন’ বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জানান, আমি এখনও বেঁচে থাকার সহজ কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিনা। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য খুঁজে না পেলেও তিনি বাঁচতে চান। কিন্তু বিবেকের তাড়নায় তিনি আত্নহত্যারও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তলস্তয়ের দুটো শ্রেণী ছিল। একটি হলো তিনি জমিদার শ্রেনীর এবং দ্বিতীয়টিতে তিনি লেখক শ্রেনীর। এই দুই শ্রেণীর কোনোটিতেই তিনি এমন কিছু খুঁজে পেতেন না যা দেখে মনে হতে পারে যে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ আছে। এরপর তিনি সাধারন মানুষের কাছে গেলেন।
তলস্তয় ল¶্য করলেন সাধারন আটপৌড়ে মানুষ ধর্ম, দর্শন, সমাজকে যতটা সহজভাবে দেখে অতটা সহজভাবে কেউ দেখে না। আর ঈশ্বরকে সহজভাবে ব্যখ্যা করতে পারলেই বেঁচে থাকার সম্ভব ও অর্থবহ। সাধারন মানুষ কি ভাবে তা নিয়েও লিখলেন। তিনি ল¶্য করলেন, একজন যাজক যেভাবে ধর্মকে উপস্থাপন করেন তা আসলে আত্নার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেনা। অথচ একজন সাধারন মানুষ যেভাবে সরলভাবে বিষয়টিকে দেখে তা চমৎকার। আমাদের দেশের প্রে¶াপটে বিচার করলেই বোঝা যায়, একজন ধর্মীয় খতিব যেভাবে ধর্মকে বিশ্লেষণ করেন তার বিপরীতে গ্রামের একজন কৃষকের ব্যখ্যা একদমই সোজাসাপ্টা ও সরল। তার উত্তর সবসময় তার নিজের ভাবনার মতোই হয়। সেখানে ভণিতা থাকে কম। প্রতিটি মানুষেরই আসলে আধ্যাত্নিক জগত রয়েছে যা তলস্তয় খুঁজে পেয়েছিলেন। বইয়ের শেষে তিনি লিখেছেন, ‘এই বইয়ের প্রাথমিক অনেককিছুই তিন বছর আগে লেখা। আমি তখনও জানতাম না এই লেখাটি প্রকাশিত আদৌ হবে কি-না ৃ’ মানে কনফেশন লিখেই হয়তো তিনি আত্নহত্যার কথা ভাবছিলেন। তারপর তিনি লিখছেন, ‘কিন্তু এই সাধারন মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমার একসময় বোধোদয় হলো, একবার দেখে নেওয়া যাক এতদিনে ব্যতিক্রম কি জেনেছি বা শুনেছি।’ আর এই খোঁজ করতে গিয়ে তিনি মূল্যবান কিছুরই সন্ধান পেয়েছিলেন। তার কনফেশনও প্রকাশিত হয়েছিল।
তলস্তয় পরবর্তীতে আরেকটি বই লিখেছিলেন। বইটার নাম এখন মনে পড়ছে না। তবে বইটা আর প্রকাশ করা যায়নি। তার মৃত্যুর পর বইটি প্রকাশিত হয়। তলস্তয়ের আরেকটি নন-ফিকশন আছে ‘দ্য গসপেল ইন ব্রিফ’। যিশুকে পাওয়া নিয়ে বাইবেলের চারজনের বর্ণনা এখানে তুলে ধরেন। তিনি বাইবেলের এই চারজনের বর্ণনা পড়ে নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন। বইটিতে তিনি যিশুর পুনরুত্থানকে আ¶রিক অর্থেই চিহ্নিত করেছেন। তবে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে যে আখ্যা দেওয়া হয় তা বলতে আসলে কি বোঝায় তার একটি ব্যখ্যা দেন। তিনি বলছেন, ‘যিশু রক্তমাংসের সন্তান নয়, বরং ঈশ্বরের আত্নার সন্তান।’ অর্থাৎ যিশুকে তিনি ঈশ্বরের স্পিরিটের অংশ হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। এ কথাই তো আসলে ধর্মে বলা হচ্ছে। ঈশ্বর নিরাকার, তিনি এক। যাজকরা কখনই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। দিতে পেরেছেন লেখকরা। কারণ তারা একটু আলাদা।
প্রশ্ন : খ্রিষ্টানরা কি এই ভাবনাটিকে আদৌ বিশ্বাস করে?
আহমাদ মোস্তফা কামাল : নাহ। করেনা বলেই তো তলস্তয়কে ব্যখ্যা করতে হলো। এজন্য তাকে নাস্তিক আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। আসলে সত্যি কথা বলে দিলে তো ধর্ম ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যেতো। তলস্তয়কে ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য অনেক কথাই শুনতে হয়েছে। কিন্তু তলস্তয় যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে নিজস্ব ব্যখ্যা ঠিকই উপস্থাপন করেছেন। আসলে তিনি কি বলতে চেয়েছেন? তিনি বলেছেন, যিশুর পুনরুত্থান আ¶রিক নয়। যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আবার সশরীরে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরবেন এমনটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে কোনটা হবে? তলস্তয় বলছেন, হৃদয়ে যিশুর অধিষ্ঠান ঘটবে। আমি নিজেও বাইবেল পড়েছি। আর বাইবেলের সারমর্মে আমি তিনটি উপাদান পেয়েছি। প্রথমটি হলো অনুতাপ, দুই ¶মা এবং সবশেষে ভালোবাসা। অনুতাপ বলতে আসলে কি বোঝায়? মানুষ ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। ইচ্ছেকৃত ভুল যেমন মানুষ করে তেমনি অনিচ্ছাকৃতভাবেও অনেক ভুল হয়ে যায়। অনিচ্ছাকৃত ভুল কেমন? আপনি পথ দিয়ে হাটছেন। সামনে পিঁপড়ার সারি। আপনার চোখে পড়েনি। পা দিয়ে তাদের মাড়িয়ে চলে গেলেন। অন্য জীবের ওপর হামলার পাপ কিন্তু আপনি করলেন। আপনার জন্য ক্ষুদ্র হলেও প্রাণ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এগুলোই অনিচ্ছাকৃত ভুল। আবার তেলাপোকা দেখলেই অনেকে আতকে ওঠেন। ঘৃণায় অনেকে তেলাপোকাকে পিষে মেরে ফেলেন। এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়।
এখানেই উপলব্ধি করতে হবে। যে জীবন আমি সৃষ্টি করতে পারিনা তা ধ্বংসের অধিকারও আমার নেই। ঠিক এ কারণেই আমি শেখ হাসিনাকে আর নিতে পারিনা। অথচ এককালে তাকেই আমি ভোট দিয়েছিলাম। যাহোক, ছোটখাটো অনেক জিনিসকে আমরা ভাবনায় নিতে পারিনা। পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীরই প্রাণের মূল্য আছে। একটা প্রজাপতি থেকে শুরু করে সামান্য পিপড়ার জীবনেরও মূল্য আছে। কিন্তু নিজের অজান্তেই আমরা হন্তারক হয়ে উঠি। আবার আমাদের জীবনের প্রয়োজনেই মাছ-মাংস খেতে হয়। হয়তো আমি নিজে মাংস না খেতে পারি কিন্তু আমার পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য ঠিকই কিনতে হয়। আসলে আমি প্রত্য¶ বা পরো¶ভাবে অন্যের জন্য তো কিছু করছি। নিরুপায় হয়ে কিংবা নিজের অজান্তে আমরা যে ভুল করি তারজন্য অনুতাপ করা জরুরি।
দ্বিতীয়ত, আপনাকে যত ব্যক্তি অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতন, বঞ্ছনা করেছেন তাদের সকলকে ¶মা করবেন। ¶মা করা ও ¶মা চাওয়া—এই দুটো গুণ জরুরি। ভালোবাসা হলো তৃতীয় বিষয়। আত্নীয়স্বজন থেকে শুরু করে কাছে মানুষ সকলকেই ভালোবাসতে হয়। এর বাইরেও সত্যকে ভালোবাসতে হবে। এ¶েত্রে যিশু বলছেন, তোমায় যদি কেউ এক গালে চড় মারে তাহলে আরেকটি গাল পেতে দাও।
প্রশ্ন : তার মানে সব ধরনের সহনশীলতার শি¶াই দেওয়া হচ্ছে?
আহমাদ মোস্তফা কামাল : হ্যা। আমি যে তিন সত্যের কথা বললাম এগুলোকেই বাইবেলের সারমর্ম বলা যায়। যাহোক, তলস্তয় বলছেন, মানুষের মনে যিশু অধিষ্ঠিত হয়। আপনার হৃদয়ে যখন অনুতাপ জাগে তখন আপনি ¶মাপ্রার্থণা করবেন কিংবা ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার চেষ্টা করবেন তখন আপনার নিকটাত্নীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব তো বটেই আপনার অচেনা মানুষকেও ভালোবাসবেন। এই উপলব্ধি নিয়েই তলস্তয় ‘রেজারেকশন’ নামে একটি উপন্যাস লিখে ফেললেন। ‘দ্য গসপেল ইন ব্রিফ’ যদি না পড়তাম তাহলে তলস্তয়ের এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রকে বুঝতে পারতাম না। উপন্যাসটির দার্শনিক ভিত্তিভূমকেও আন্দাজ করা কঠিন হয়ে পড়তো। শেষে কি হলো? সে একজন মহাপাপিষ্ঠ। জমিদারের সন্তান। ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গৃহপরিচারিকা এক মেয়ে কাতিউশার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এজন্য মেয়েটিকে পরবর্তীতে অনেক ভুগতে হয়েছে। নেখলিউদভ ফুফুর বাড়ি থেকে ফেরার পর মেয়েটির কথা ভুলে যায়। জমিদারের মতোই জীবনযাপন করতে থাকে। তারপর একদিন এক ফৌজদারি মামলায় সে জুরি হিসেবে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে অনেক বছর পর কাতিউশাকে দেখে সে চমকে ওঠে। কাতিউশার পরিণতি দেখে তার অনুতাপ জাগে মনে। কাতিউশা ততদিনে পতিতাবৃত্তি করছিল। আর পতিতাবৃত্তির কারণেই তাকে ঘটনাচক্রে আদালতে আসতে হয়। নেখলিউদভের মনে হয় কাতিউশার এই পরিণতির জন্য তার দায় রয়েছে। এরপর নেখলিউদভের জীবনের একটি বড় যাত্রা শুরু হয়। অনুতাপ থেকে কাতিউশার কাছে মার্জনা ভি¶া এবং তাকে ভালোবাসা। এমনকি তার প্রজাদের কাছেও তিনি ¶মাপ্রার্থণা করেন এবং নিজের জমিজমা প্রজাদের অকাতরে বিলিয়ে দেন। নেখলিউদভের মধ্যে ভালোবাসা জাগে। যারা তাকে অপছন্দ করে তাদেরও সে ভালোবাসে। উপন্যাসটির শেষে নেখলিউদভকে যিশুর মতোই মনে হয়। মহাপাপিষ্ঠ একজন ব্যক্তি এই তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমেই পুনরুত্থান ঘটায় নিজের মধ্যে। আপনার প্রথম প্রশ্নেই আবার ফিরে আসতে হয়। আসলে একটি বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। কিন্তু একটা বই থেকে তো আরও অসংখ্য বইয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। একটা বইয়ে স্থির থাকা যায়না। একটা বই থেকে অন্য আরেকটা বইয়ে চলে যেতে হয়।
আজকের কথায় এত¶ণ আমি বিদেশি বিজাতীয় সাহিত্যের কথাই বলেছি। তা বলে ভাববেন না আমি বাংলা সাহিত্যের পাঠক নই। বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠক বলে নিজেকে দাবি করতে পারি। বয়স এখন পঞ্চান্ন। বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক বা ধ্রুপদী বইগুলো অনেক আগেই পড়া হয়ে গেছে। পাঠক জীবনটা তো দীর্ঘ। আবার এখনও অনেক বই পড়া হয়। কিছু কিছু বই পিডিএফে পড়তে হয়। যাহোক, সমসাময়িক অনেক বই তো পড়াই হয়। তবে আমি আসলে কি বই পড়ছি তার উত্তরে এই কটা বইয়ের নাম বললাম। হেনরি ডেভিস থরোর ‘ওয়াল্ডেন’ পড়ার আগেও আমি তার আরেকটি বই পড়েছিলাম। বইটির নাম ‘অন দ্য ডিউটি অব সিভিল ডিসোবেডিয়েন্স’। নাগরিককে সবসময় বাধ্য থাকা উচিত না। বইটিতে তিনি বলছেন, যে আইন ন্যায়সঙ্গত নয় তা যদি কেউ মানে তাহলে তিনি অপরাধ করছেন।
প্রশ্ন : সাম্প্রতিক আমাদের সময়ের সঙ্গে তো এই কথা বেশ মিলে যায়।
আহমাদ মোস্তফা কামাল : হ্যা, এজন্যই তো বলা। থরো একজন শক্তিমান দার্শনিক ছিলেন। তার প্রতিটি কথার মধ্যেই জোস ছিল। থরোর দুটো বই পরপর পড়েছি। তারপর তলস্তয়ের কনফেশন। মানে একটার পর একটা ধারাবাহিকতা থাকেই। তবে সবসময় আমার সঙ্গে জোসেফ ক্যাম্পবেলের ‘পাওয়ার অব মিথ’ বা ‘মিথের শক্তি’ বইটা থাকে। আমার সবচেয়ে প্রিয় বই সাঁতন দ্য হেক্সোকুরির ‘দ্য লিটল প্রিন্স’। বইটা ছোটদের বই হলেও এটিকে আসলে ছোটদের বই বলাও চলে না। আমার জীবনে নানা দুঃসময় এসেছে। বইটি আমি প্রতিবারই পড়েছি। দ্বারস্থ হয়েছি বইটির কাছে। আমাকে যদি কেউ একটি নির্দিষ্ট বই পড়ার পরামর্শ চায় তাহলে আমি এই বইটির কথাই বলবো।
বিগত পঁচিশ বছর ধরে শি¶কতা করছি। আমার অনেক শি¶ার্থীই আমাকে এই প্রশ্ন করেছে। আমি দ্বিধাহীনভাবে তাদের এই একটি কথাই বলেছি। ‘দ্য লিটল প্রিন্স’ বইটির নামই বলেছি এবং বলবো। আসলে আমার এই সা¶াৎকারে আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তাটা পৌছে দিতে চাই আমার অজানা পাঠকদের কাছে। জীবনে যদি অন্তত একটা বই পড়েন তাহলে এই বইটা অবশ্যই পড়বেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বরং বইটি পড়া উচিত। শৈশবে একবার, কৈশোরে আবার এবং পরিণত বয়সেও একবার। এরমধ্যে প্রৌঢ় বয়সেও পড়া উচিত আবার বৃদ্ধ বয়সে একবার পড়া উচিত।
প্রশ্ন : আসলে এই বইটির প্রতিই আপনার এত আগ্রহের কারণ কি?
আহমাদ মোস্তফা কামাল : বইটি একটি ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে লেখা। ছোট ছেলেটি একাই একটি ঘরে বাস করে। তার ঘরে বীজ থেকে অঙ্কুরিত গাছটি বেয়ে সে আকাশে পৌছাতে পারে। আসলে সে একটি গোলাপ গাছের বীজ রোপন করে। ওই বীজ আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। গোলাপ ফুল ফোটার সময় তার সঙ্গে একজন দেবির সা¶াৎ হয়। ঐ সময় গোলাপের সঙ্গে অভিমান করে সে বেড়িয়ে পড়ে। রাগ করে যে অন্য একটা অরণ্যে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে অন্য কেউ বাস করে। এভাবে সে সাতটি গ্রোভ বা বনভূমি পার করে। অনেকগুলো গ্রোভ পার হওয়ার পর সে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং নামে সাহারাতে। সেখানে একজন বৈমানিক অবতরণ করেছেন। তার বিমানে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেওয়ায় তাকে নামতে হয়েছে। পাইলটও একা। একা অবস্থাতেই রাজপুত্রের সঙ্গে পাইলটের দেখা। মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তার দেখা হয় এই ব্যক্তির সঙ্গে। তার আগে দেখা হয় এক সাপের সঙ্গে। সাপ, শেয়াল ও ফুল ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছে। ওই বৈমানিকের বর্ণনায় গল্পটি লেখা। ছোট রাজকুমার আসলে কি করে তা আমরা জানতে পারি।
এই গল্পটির কিছু বিষয় ল¶্য করা দরকার। শিয়াল রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আমায় পোষ মানাবে? কিন্তু রাজপুত্র তো একা থাকে। সে জানেনা কিভাবে কোনো প্রাণীকে পোষ মানাতে হয়। রাজপুত্র অবশ্য শিয়ালকে জিজ্ঞেস করে, পোষ মানালে আসলে কি হবে। শেয়াল উত্তর দেয়, এখন তোমার সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের ফারাক নেই। অন্য যে কারো সঙ্গে তুলনায় আমি তোমাকে একই দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু যখন তুমি আমাকে পোষ মানাবে তখন তুমি আমার কাছে স্পেশাল হয়ে যাবে। এইযে কোনো ব্যক্তি বিশেষ কেউ হয়ে ওঠা এই শি¶াটি শেয়াল থেকে রাজপুত্র পায়। তো সে শেয়ালকে পোষ মানায়।
তারপর পৃথিবীতে আসার পর একটি বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে অনেকগুলো গোলাপ ফুঁটে আছে। তার বাড়িতে একটি গোলাপের ওপর রাগ করে সে চলে এসেছে। কিন্তু এখানে অগণিত গোলাপ। সে মনে মনে ভাবে, এক গোলাপ নিয়ে আমি এতকিছু করলাম অথচ এখানে এতগুলো গোলাপ ফুটে আছে। তাহলে এই যাত্রা বৃথাই গেল! কিন্তু শেয়াল তাকে বোঝায়। যখন তুমি কাউকে পোষ মানাবে কিংবা কারও অনুগত হয়ে উঠবে তখন তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য। এ কথা শোনার পর সে বাড়ি ফিরে যায়। সে ভাবে, এখানে অনেক গোলাপ আছে। তাতে কি, আমার বাড়িতে একটি গোলাপ আছে। সেটি আমাকে পোষ মানিয়েছে। এভাবেই উপন্যাসটি এগিয়ে গিয়েছে।
উপন্যাস কখনই বর্ণনা করা যায়না। উপন্যাস পড়তেই হয়। এই উপন্যাসটিতে একজন শিশু এমনকি একজন বয়োজ্যেষ্ঠকেও তার করণীয় শিখিয়ে দেয়।
প্রশ্ন : বলতে চাচ্ছেন এটি একটি অ্যালিগোরিক্যাল ফিকশন।
আহমাদ মোস্তফা কামাল : অবশ্যই। রূপকথার ছলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শি¶া উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে। এটাকে অবশ্য আমরা শি¶ণীয় উপন্যাসও বলতে পারবো না। একটা বাচ্চা ছেলের এডভেঞ্চার বলা যেতে পারে। বাচ্চাদের কাছে বইটি নিছক আনন্দের বস্তু। কিন্তু বড় হওয়ার পর এর আরেকটা অর্থ চলে আসে। আমি আসলে আপনাদের মাধ্যমে পাঠকদের বলতে চাই, আপনারা জীবনে অন্তত একটা হলেও বই পড়ুন। আর পড়লে এই বইটাই পড়ুন।
সাহিত্যের নানা ফর্ম রয়েছে। উপন্যাস, গল্প, নন-ফিকশন, আত্নজীবনী, স্মৃতিচারণা, ম্যাগাজিন, নভেলা—ইত্যাদি নানা ফর্মের ¶েত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে, এগুলো মানুষের হৃদয়ের গড়নের জন্য লেখা হয়েছে। মানুষের হৃদয়ে নন্দনভাবনা তৈরি করার জন্যই এই বইটা পড়া জরুরি। যারা হাজারটা বই পড়েছেন বা ঝানু পাঠক বলে আত্নতৃপ্তি পান তাদেরকেও বলবো এটি পড়ে দেখেন। বাংলায় এই বইটির অনেকগুলো অনুবাদ হয়েছে। আমি আনন্দ মজুমদারের অনুবাদটি পড়তে বলবো। আমি ইংরেজিতে পড়েছি যেহেতু মূল ফরাসি জানিনা। এই বইটির অনুবাদগুলোর কয়েক পৃষ্ঠা নেড়েচেড়ে দেখেছি। একমাত্র আনন্দ মজুমদারের অনুবাদটিকেই আমার মনে হয়েছে মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখার মতো। তো আজ এ পর্যন্তই তাহলে থাকুক…