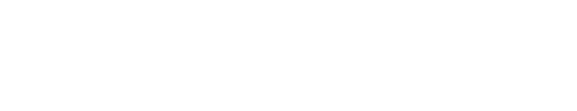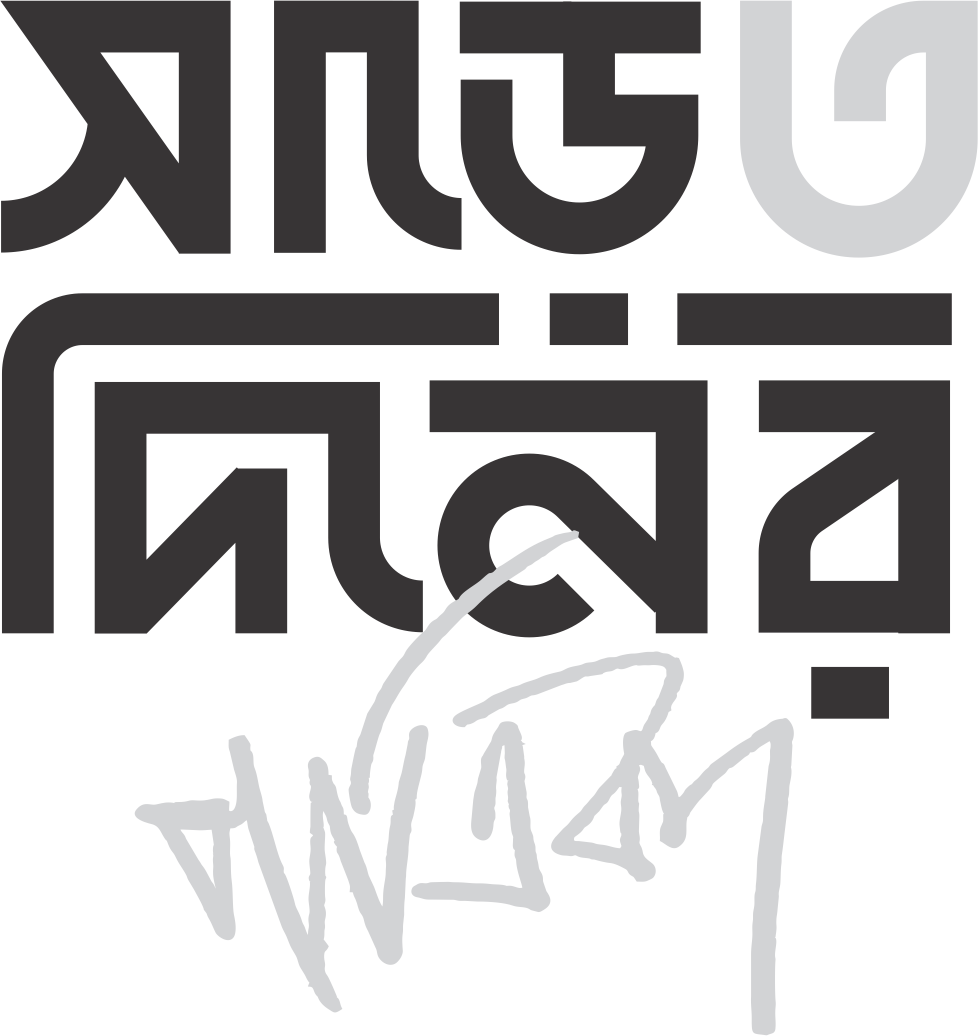খুব ছোটবেলায় একবার চিটাগাং বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানে তখন আমার বড় বোন আর খালা থাকতেন। খালাম্মার বাসা ছিল রেলওয়ের সিআরবির পাহাড়চূড়ায় টি-২ ভবনে। বিরাট আলিশান বাড়ি, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে উঠলেই দিগন্তজোড়া আকাশ, দূরে সাগরের ঝিলিমিলি চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে বেশ খোলামেলা প্রশস্ত জায়গা। চারপাশে গাছগাছালির ছড়াছড়ি। সন্ধ্যা ঘনালেই সীমানার কড়ই গাছে তক্ষকের ‘তোর ঠ্যাং, তোর ঠ্যাং’ ডাক শোনা যেতো। এমনি একদিন বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির এক পাশের একটা কামরার দেয়াল আলমারি ঠাসা বইয়ের দিকে চোখ গেল। কিছু না ভেবেই একটা বই বের করে নিলাম। সেটি ছিল কাজী আনোয়ার হোসেনের কুয়াশা সিরিজের ২৬ নম্বর বই। তখন অবশ্য সিরিজের মানে জানতাম না। বইয়ের প্রচ্ছদে দানবীয় একটা অবয়বের প্রতিকৃতি। দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বইটা নিয়ে বাইরে এসে টানা বারান্দার সিঁড়িতে বসে পড়তে শুরু করলাম। পড়ছি আর একটু পরপর কেমন কেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। দুষ্টু বিজ্ঞানীর ফ্র্যাঙ্কেন্টাইনের মতো দানবটা বুঝি এখুনি পেছনে এসে দাঁড়াবে, তপ্ত শ্বাস ফেলবে ঘাড়ের উপর। পড়তে পড়তে কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে টেরও পাইনি। হঠাৎ তক্ষকের অপার্থিব ডাক কানে যেতেই সচকিত হয়ে উঠলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চট করে ফিরে গেলাম বাড়ির ভেতর। সেটাই ছিল কাজী আনোয়ার হোসেন আর সেবা প্রকাশনীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। গা ছমছম করা সেই গল্পের কথা অনেক দিন মনে ছিল।
যাহোক, সেবার চিটাগাং থেকে চলে আসার পর অবশ্য বহুদিন আর সেবার বই খেয়াল করিনি। ভালো কথা, তখন আব্বার চাকরীর সুবাদে আমরাথাকতাম সিলেটে। এরপর আব্বা বদলী হয়ে এলেন ময়মনসিংহে অতিরিক্ত জেলা জজের দায়িত্ব নিয়ে। প্রথমে আমাদের আবাস হলো ব্রহ্মপুত্রের তীরে সার্কিট হাউসে, এর কিছুদিন পর কলেজ রোডে, আনন্দমোহন কলেজের মাঠের একপাশে একটা দোতলা বাড়িতে। তখন আবার সেবার বইয়ের দেখা পেলাম। ময়মনসিংহের তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আনোয়ার চাচার দুই ছেলে মুর্শিদ ভাই ও রাশেদ যথাক্রমে আমাদের দুই ভাইয়ের বন্ধু ছিল। আমাদের দুই পরিবারের বাড়িতে ছিল অবাধ যাতায়াত। বড় ভাইয়ের বন্ধু, মোরশেদ ভাই তখন প্রায়ই সাইকেল চালিয়ে আমাদের বাসায় হাজির হতেন, সাথে কাজী আনোয়ার হোসেনের আরেকটি যুগান্তকারী সিরিজ মাসুদ রানার কোনও সদ্য প্রকাশিত বা পুরেনো বই। আমার আম্মা বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসতেন। যখন যেখানে গেছেন, তার প্রথম কাজ ছিল স্থানীয় লাইব্রেরির সদস্য হওয়া, সেখান থেকে নিয়মিত বই এনে গোগ্রাসে গেলা। মোরশেদ ভাইয়ের দিয়ে যাওয়া বইও ছিল আম্মার অন্তহীন পাঠ-নেশার খোরাক। মোর্শেদ ভাইয়ের দেওয়া একটা বইয়ের কথা এখনও মনে আছে, সাগর সঙ্গম, কোন খণ্ড সেটা এখন আর মনে নেই। আম্মাকে এভাবে বই পড়তে দেখে আমিও বইয়ের প্রতি ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যখন দুঃসহ এক পর্ব অতিক্রম করছি, তখন কিছু কিছু দুর্বৃত্ত লুটপাটের নেশায় মেতে উঠেছিল, যেকোনও প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে যেমন হয়। সেই সময় ফেরিআলার কাছ থেকে আমাকে দুটো বই কিনে দেওয়া হয়েছিল, একেবারে পানির দরে। তার একটা ছিল রাবেয়া খাতুনের কিশোর উপন্যাস ডানপিটে ছেলে, পরে এই উপন্যাস অবলম্বনে দ্য প্রেসিডেন্ট’স মেন বা এরকম কোনও নামে চলচিত্র নির্মিত হয়েছিল বলে শুনেছি। অন্যটি ‘পুবালী হাওয়া’ নামে ভারতের দেশ সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত একটি পূজা বার্ষিকী। বই দুটো যেন চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গেল। ডানপিটে ছেলের কিশোর নায়কের সাহসিকতা আর পূজা বার্ষিকীর বিভিন্ন গল্প, কমিক্স, কার্টুন আমার ভেতর বইয়ের প্রতি এক দুনির্বার আকর্ষণ তৈরি করলেও সেভাবে আর বই হাতে পাইনি। তখন বই এতো সহজলভ্য ছিলও না।
এরপর ফরিদপুরে পাড়ি জমাই আমরা। ফরিদপুরে আমাদের অবস্থান অবশ্য স্বল্পায়ু ছিল। তবে ওখানে ভিন্ন নেশা পেয়ে বসে আমাকে। আমাদের বাসার সামনে বেশ সুপ্রশস্ত জায়গা ছিল, সেখানে নেহাত শখের বশে আব্বা বিভিন্ন মৌসুমী সব্জির চাষ করতেন। আমি তখন বাগান নিয়ে মেতে উঠেছিলাম। আমাদের বাসার চারপাশে ছিল বিভিন্ন ফল গাছের ছড়াছড়ি, আমি আর আমার ছোট বোন স্কুল বাদে বা ছুটির দিনগুলো হয় বাগানে কাটাতাম নয়তো সারাদিন আমগাছ, জামগাছে চড়ে বসে থাকতাম। আবার কোনও কোনওদিন চলে যেতাম নদীর পাড়ে। সাথে অবশ্য আব্বা আমাদের দিকে খেয়াল রাখার জন্যে একজন পিয়নকেও পাঠাতেন। পিয়ন ভাইরা আমাদের খুব ¯্নহে করতেন। তাদের কারও কাছে আমরা ছবি আঁকা শিখেছি, কেউ আবার পুরোনো দিনের গান গেয়ে শোনাতেন।
আব্বা অবসর গ্রহণের পর আমরা ফরিদপুর থেকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসি। প্রথমে আমাদের অবস্থান ছিল ঢাকার হাটখোলার টিকাটুলির নানা বাড়ীতে। ওখানে কিছুদিন থাকার পর সিদ্ধেশ্বরীতে ভাড়া বাড়িতে এসে উঠি, ভর্তি হই সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ স্কুলে। জুটল বেশ কয়েকজন নতুন সহপাঠী আর বন্ধু। সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় হঠাৎ একদিন আমার বড় ভাই কুয়াশা সিরিজের সদ্য প্রকাশিত ৩৫ ও ৩৬ নম্বর বই দুটো এনে আমার হাতে দিলেন। তখন আবার চট্টগ্রামের পড়া কুয়াশা ২৬-এর কথা মনে পড়ল। কুয়াশা ৩৫-৩৬ ছিল মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দুই খণ্ডের কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি তখনও চাঙা, বই দুটো যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল। এরপর শুরু হলো সত্যিকার অর্থে যাকে বলে বইয়ের নেশা। কুয়াশা সিরিেিজর বাকি বইয়ের খোঁজে উঠে-পড়ে লাগলাম। কিন্তু খোঁজ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে সিরিজের প্রথম দিকের বইগুলো তখন আউট অভ প্রিন্ট। আবার নতুন বই বেরুনোর গতিও মন্থর। মুক্তিযুদ্ধের পরপর প্রকাশনা কেন, সব ক্ষেত্রেই ভীষণ নাজুক অবস্থা চলছিল। অল্প সময়ে সেবা প্রকাশনী যে গুছিয়ে উঠতে পেরেছিল সেজন্যে তাদের ধন্যবাদ জানাতেই হয়। অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে সিরিজের বেশ কিছু বই যোগাড় করা গেলেও বেশির ভাগ বইই তখনও নাগালের বাইরে। মনে আছে বন্ধু খোকনের কাছে কাকরাইলের একজন কুয়াশা সিরিজের তিনটি বই বিক্রি করবে শুনে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সোজা হাজির হয়েছিলাম তার বাড়িতে, বইগুলো তখনকার মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দামে কিনে নিয়েছি। এছাড়া, হন্যে হয়ে বায়তুল মোকাররম, পুরানা পল্টনের বইয়ের দোকানগুলোতেও খোঁজাখুঁজি কম করিনি, ঢুঁড়ে বেরিয়েছি বাংলাবাজারের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোয়ও। কিন্তু হাহতোম্মি! এক সময় আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, আমার দুই সহপাঠী-বন্ধু, খোকন আর জীবনকে নিয়ে সেবা প্রকাশনীর ঠিকানা খুঁজে বের করে একদিন বিকেলে চলে গেলাম ১১৩, সেগুন বাগিচায় (এখন ২৪/৪) সেবা প্রকাশনীতে। সেবা তখন কিন্তু এখনকার মতো অট্টালিকায় ছিল না, বেশ বড়সড় একটা জায়গা জুড়ে টিনের ঘরমতো ছিল। ওখানেই কম্পোজ, ছাপা, বাঁধাই, বাজরজাতকরণের মতো সব কাজ সারা হতো। প্রচ্ছদও করা হতো ব্লক করে। সেবায় গেলে প্রায়ই কৈশোরিক মুগ্ধ চোখে এসব দেখতাম। জুস বাইন্ডিং, স্টিচ বাইন্ডিংয়ের কায়দা সেবাতেই শিখেছিলাম। নিজের হাতে বাসায় কয়েকটা বই বাঁধাইও করেছিলাম। বই বাঁধাইয়ের পর মেশিনে ঘ্যাঁঘ্যাঁচ করে কাটা হতো, দারুণ ছিল সেই দৃশ্য!
সেবা প্রকাশনীতে গিয়ে প্রথমেই কাঙ্ক্ষিত বইগুলো পাওয়ার কোনও আশা আছে কিনা তার খোঁজ করলাম। তখন সেবার ম্যানেজার ছিলেন প্রবীণ কুদ্দুস সাহেব। আমাদের মতো কিশোরদের এভাবে বইয়ের খোঁজে হাজির হতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন, কিছুটা মায়াও জেগেছিল বোধ হয়। তিনি বললেন, পুরোনো বই তো নেই, আবার কবে ছাপা হবে তারও ঠিকঠিকানা নেই। তবে তার কাছে কিছু বইয়ের অফিস কপি আছে, সেগুলো দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা তো তখন নাছোড়বান্দা। গোঁ ধরে বসলাম। অফিস কপি তো একটা থাকলেই চলে, আমাকে একটা করে কপি দিলে ক্ষতি কি? তিনি একটু যেন ভাবলেন বা ভাববার ভঙ্গি করলেন, তারপর অলৌকিকভাবে সায় দিলন আমাদের আবদারে। মহানন্দে কুয়াশা সিরিজের ২১ থেকে ৩১ পর্যন্ত বইগুলোর (সম্ভবত) একটা করে কপি হাতে বিজয়ীর বেশে সেদিন বাসায় ফিরে আসি। এরপর থেকে আমি জীবন কিংবা খোকন অথবা ছোট বোন শারমিনকে (এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক) নিয়ে প্রায়ই সেবায় হাজির হতাম। খামোকা এদিক-ওদিক ঘুরতাম যদি এক নজর কাজীদার দেখা মেলে। বিকেলের দিকে জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে দেখতাম বাড়ির সামনের তার নাতী বালক টিংকুকে নিয়ে বা একাকী বৈকালিক ভ্রমণ করছেন। বিরাট মানুষ হয়েও তিনি অবলীলায় আমাদের সালাম দিতেন। আমরা কখনও তাকে আগে সালাম দিতে পেরেছি কিনা মনে পড়ে না। বরাবরের মতো কাজীদা তখনও রহস্য পুরুষই ছিলেন। আমরা অনেক কসরত করেও তার মুখ দর্শন করতে পারিনি। তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতাম সেবার কোনও কর্মচারী ভাই মারফত তার লেখা বইয়ে অটোগ্রাফ নিয়ে। এভাবেই রানা সিরিজের আমিই রানা দ্বিতীয় খণ্ডে তার অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম। সেবা যাওয়া-আসার সুবাদে একদিন আবার কুয়াশা সিরিজ বের হওয়ার কথা জানতে পেলাম। এর আগে ৪১ নম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে সিরিজটি থমকে গিয়েছিল। এমনি সুখবরে আমরা তো খুশিতে আটখানা। অপেক্ষার প্রহর যেন আর ফুরোতে চায় না। সেবায় গেলেই কুদ্দুস সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, কবে বের হবে কুয়াশার পরের বই। এমনি একদিন সেবায় গেছি, দেখি তিনি লম্বা কাগজের একটা বান্ডিল নিয়ে কাটাকুটিতে ব্যস্ত। জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কি? তিনি হেসে বললেন, এটাকে প্রূফ বলে, তিনি ভুল দেখিয়ে দেওয়ার পর শুদ্ধ করে টাইপ বসানো হবেÑতখন লেটার প্রেসে হাতে বই কম্পোজ করা হতো, এখনকার মতো কম্পিউটারে নয়; ভীষণ কঠিন কাজ ছিল!Ñতারপর লেখক ঠিক আছে, নিশ্চিত করলে ছাপাঘরে যাবে বাকি কাজ শেষ করার জন্যে। কি বই ওটা? কুয়াশার নতুন বই ৪২! জানতে চাইলাম, কিভাবে দেখতে হয় প্রূফ? তিনি কায়দা বাতলে দিলেন, কোন চিহ্নের অর্থ কি, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিলেন। আমি গোঁ ধরে বসলাম, প্রূফটা আমাকে দেখতে দিতে হবে, আমি দেখে দেবো। তিনি সাফ না করে দিলেন, এসব ছেলেমানুষের কাজ নয়। তাছাড়া সাহেব (কাজীদা) জানতে পারলে রক্ষা থাকবে না। কিন্তু আমি তখন যাকে বলে অবস্থান ধর্মঘট করার মতো। প্রূফ আমাকে দেখতে দিতেই হবে। অবশেষে পরাজয় মানলেন কুদ্দুস সাহেব। বললেন, এক শর্তে প্রূফ আমার হাতে দিতে পারেন, কিছুতেই এর ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না, আর পরদিন বিকেলের মধ্যে অবশ্যই তার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে; একথা কাউকে জানানো যাবে না। বিনা বাক্যব্যয়ে তার শর্ত মেনে নাচতে নাচতে প্রূফ হাতে বাড়িতে ফিরলাম। সন্ধ্যা হতেই স্কুলের পড়া তুলে রেখে বসে গেলাম ‘প্রূফ দেখতে’। বলা যত সহজ, করা ততই কঠিন। বারবার আম্মার কাছ থেকে শুদ্ধ বানান জেনে নিতে হচ্ছে। খেয়াল রাখতে হচ্ছে, কম্পোজ করার সময় মূল লেখার কোনও অংশ বাদ পড়ে গেছে কিনা। কুয়াশা তখন শেখ আব্দুল হাকিম (হাকিম ভাই) লিখতেন (পরে জেনেছি, মাসুদ রানাসহ কাজীদার নামে প্রকাশিত সেবার বেশির ভাগ রোমাঞ্চোপন্যাসও তার লেখা)। তিনি হাতে না লিখে টাইপ করতেন, তাই হাতের লেখা বোঝার ঝামেলা ছিল না। যাহোক, অনেক কষ্টে প্রূফ দেখে পরদিন সময়মতো সেবায় গিয়ে কুদ্দুস সাহেবের হাতে তুলে দিলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। আমার দেখা প্রূফ উল্টেপাল্টে পরখ করে মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বোধহয় তখন আমার উপর আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। কারণ এরপর প্রায় পুরো বই প্রকাশের আগেই প্রূফ দেখার ছলে পড়ে ফেলেছিলাম। প্রূফ দেখার হাতেখড়ি আমার এভাবেই। এমনিভাবেই একদিন হাকিম ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তার আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা ছোট বলে তিনি আমাদের এতটুকু তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করেননি। আমরা বয়সে অনেক ছোট হলেও তিনি আমাদের সাথে খোলামনে কথা বলেছেন। অনেক পরে সেবায় লেখালেখি শুরু করার পর হাকিম ভাইয়ের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সেটা তার আকস্মিক মৃত্যু অবধি জারি ছিল।
সেই সময় কুয়াশার পাশাপাশি ধীরে ধীরে সেবার অন্যান্য বই আর বিশেষ করে মাসুদ রানা সিরিজের সাথেও পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। শান্তিনগরে আমার বড় মামা থাকতেন, বড়মামার বাসা থেকেও মুখোশ, দস্যু বাহরাম, দস্যু শাহজাহান, ইত্যকার নানা সিরিজের বই এনে পড়েছি। তাছাড়া, এই সময় অন্যান্য দেশিবিদেশী লেখকদের বইও পড়তে শুরু করছিলাম। রিজিয়া রহমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, মাহমুদুল হক, রাহাত খান, মির্যা আব্দুল হাই, সেলিনা হোসেন, হাসনাত আব্দুল হাই, কৃষণ চন্দর, সাদত হোসাইন মান্টো, ইসমত চুগতাই, এমনি কত লেখক। হাটখোলার টিকুটুলিতে নানাবাড়ীতে আমার মেঝমামীর ভারতীয় লেখকদের বইয়ের বিরাট সংগ্রহ ছিল। তার কাছ থেকে নীহার রঞ্জন, নিমাই ভট্রাচার্য, সমরেশ বসুর মতো লেখকদের বই এনে পড়তাম। সোজা কথা, পড়ার বেলায় আমি ছিলাম সর্বভূক, যা হাতের কাছে পেয়েছি, গোগ্রাসে গিলেছি, এমনকি এমনও সময় গেছে যে বাজারের ঠোঙার লেখাও পড়তে কসুর করিনি। এত কিছুর পরেও কুয়াশা, মাসুদ রানা, আর সেবার অন্যান্য বইয়ের প্রতি টানটা ছিল অন্যরকম। বইয়ের খোঁজে কত জায়গায় গেছি ইয়ত্তা নেই। ঢাকা স্টেডিয়াম মার্কেটের দোতালায় আইডিয়াস ও ম্যারিয়েটা নামে দুটি দোকান ছিল পাশাপাশি, এই দোকানগুলোয় প্রচুর বিদেশী বই পাওয়া যেতো। বিশেষ করে ভারতীয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দের বই। বিভিন্ন কম্ক্সিও ছিল আগ্রহের বিষয়। এসব দোকানে তখন প্রায়ই একজন তরুণকে দেখতাম। তিনি সাইকেল নিয়ে আসতেন। প্রচুর বই কিনতেন। দোকানীর সাথে তার ভালোই সখ্যতা থাকার কথা সমনে হয়েছে। একদিন সেবাতেও তাকে দেখে বেশ অবাক হই। পরে তার পরিচয় জেনেছি, তিনি ছিলেন তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান। রকিব হাসান তখন ছদ্মনামে সেবায় বেশ কিছু বই লিখে ফেলেছেন।
শান্তিনগরের সবুজ লাইব্রেরিতে আমাদের দুই ভাই বোনের অবাধ যাতায়াত ছিল। লাইব্রেরির মালিক আমাদের ভীষণ ¯্নহে করতেন। আমরা প্রায়ই বিকেলে সবুজ লাইব্রেরিতে গিয়ে ভেতরে বসে আরামসে পছন্দমতো বই পড়তাম। নতুন বইয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে বেশ জ্বালাতন করতাম ভদ্রলোককে। তিনি বলতেন, ‘আমি কোত্থেকে রোজ তোমাদের জন্যে নতুন বই যোগাড় করবো, বলো!’ সবুজ লাইব্রেরির পাশেই ছিল হাসি প্রকাশনী, হারামনি-খ্যাত মনসুরউদ্দিনের ছেলে ওই দোকানে বসতেন। তিনি প্রায়ই আমাদের তার লাইব্রেরিতেও যেতে বলতেন।
সেই সময় মুক্তধারা নিয়মিত প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন বই বের করতো। বিচিত্রায় সেসব বইয়ের খবর পাওয়া যেতো। সেই সুবাদে অনেক বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। এই মুক্তধারাই সম্ভবত বাংলাদেশের প্রকাশকদের ভেতর প্রথম পুরানা পল্টনে, এখন যেখানে সোয়াশের শোরুম তার পেছন দিকে একটা জায়গায়, তাদের শোরুম স্থাপন করেছিল। অনেক সময় ওই শোরুম থেকেও বই কিনেছি। পুরানা পল্টনের তখন বেশ কয়েকটা পুরোনো বইয়ের দোকান ছিল। আখতার ভাই, কাদের ভাই আর আলমগীরের দোকান থেকে অনেক ইংরেজি বই কেনার কথা মনে আছে। দোকানগুলো এখন উঠে গেছে।
একদিন বিকেলে সেবায় গেছি, দেখি থরে থরে বই রাখা। প্রচ্ছদ দেখে চোখ ছানাবড়া: ড্রাকুলা, অনুবাদ করেছেন রকিব হাসান। বিক্রি হবে কিনা জানতে চাইলাম, ইতিবাচক উত্তর পেয়ে দেরি না করে বই কিনে বাড়ি ফিরলাম। সম্ভবত আমিই ছিলাম ড্রাকুলার সৌভাগ্যবান প্রথম ক্রেতা। এর পর রকিব হাসান শিকার কাহিনী, আজব সিরিজের কিছু চমৎকার বই আর ড্রাগস, মৃত্যুচুম্বন, বিদেশ যাত্রার মতো অনেকগুলো দুর্দান্ত উপন্যাসও লিখেছেন।
এইচএসসি পরীক্ষার পর আমি চলে যাই চিটাগাংয়ে, পড়াশোনার জন্যে। তাই বহুদিন আর সেবায় যাওয়া হয়নি। যদিও সেবার বইয়ের সাথে যোগাযোগ ছিল নিরন্তর। ছুটিছাটায় ঢাকায় এলেও সেগুনবাগিচা মুখো হইনি। তাছাড়া ততদিনে আমরা সিদ্ধেশ্বরীর বাসা ছেড়ে মগবাজার অয়্যারলেসে চলে গেছি। তখন মোড়ের একটা লাইব্রেরি থেকে নিযমিত সেবার বই কেনা হতো।
চিটাগাংয়ে আমার এক চাচাত বোন থাকতেন। তার ছেলে নূরানী প্রায় আমার সমবয়সী। প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাওয়া হতো। নূরানী আবার তখন ইংরেজি গল্পের বইয়ের নেশায় মেতেছিল। জেমস হেডলি চেজ, লুই লা’মুর, অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, ডেসমন্ড বেগলি, ফ্রেডেরিক ফোরসাইদের বই পড়ে তার উন্মাদ-প্রায় দশা। আমাকে একদিন বলল, ‘মামা, অনেক তো রানা-কুয়াশা পড়লে, এবার দু-একটা ইংরেজি বইও পড়ো, মজা পাও কিনা দেখ।’ আমি বললাম, ‘পাগল নাকি, আমি কখনও ওসব পড়েছি! মাথার দশ ফুট উপর দিয়ে যাবে না!’ নূরানীর উত্তর, ‘আরে বাবা চেষ্টা তো করে দেখ!’ অগত্যা ওর কাছ থেকে দুটি বই নিয়ে ফিরে এলাম: আর্থার হেইলীর রানওয়ে জিরো-এইট আর অন্যটি জেমস হেডলি চেজের ‘লেডি, ইয়ার ইজ ইউর রিদ’, দুটিই রোমাঞ্চোপন্যাস। শেষ করার পর ওর কাছ থেকে আরও বই এনে পড়েছি। সত্যি, অন্যরকম একটা মজা আছে তাতে।
আমি তখন বি.কম. অনার্স পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। দেশে এরশাদের সামরিক শাসন আর তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগ ছাত্রবিক্ষোভ চলছিল। আমার অনার্স পরীক্ষার ঠিক আগে ছাত্র বিক্ষোভের মুখে এরশাদ দেশের সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করে বসলেন। আমিই তখন এই অনির্দিষ্ট কাল মেয়াদী বন্ধের নাম দিয়েছিলাম ‘এরশাদ ভ্যাকেশন’। পরীক্ষার পড়া মাথায় উঠল। কি করবো ভাবছি। ঢাকায় আসবো নাকি, চিটাগাংয়েই রয়ে যাবো? কারণ কখন আবার সব খুলে যাবে, ঠিক নেই; ঢাকায় গিয়ে আটকে পড়লে বিপদ হবে শেষে। এমনি দোনোমোনা অবস্থায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। আচ্ছা, যেকোনও একটা বই অনুবাদ করলে কেমন হয়? যদিও আগে সেভাবে কখনও লেখালেখির চেষ্টা করিনি। বেশ ছোট বেলায় একবার কুয়াশা আর একটা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম বটে, কিন্তু সুবিধা করতে পারিনি। লেখালেখি বলতে স্কুলে রচনা লেখা আর সেবার আলোচনা বিভাগে চিঠি পাঠানো (সেও স্বনামে নয়)। অভিজ্ঞতা নেই তো কি হয়েছে? চেষ্টা করতে নিষেধ করছে কে? ব্যস, কাউকে কিছু না বলে আর্থার হেইলীর রোমাঞ্চোপন্যাস রানওয়ে জিরো এইট অনুবাদে হাত দিয়ে বসলাম। শুরু করলাম বটে, কিন্তু কাজটা তো আর অত সোজা না! প্রতি পদে পদে বিভিন্ন শব্দের জুৎসই অর্থ/প্রতিশব্দের খোঁজে অভিধান হাতড়ে মরা, আর মাথার চুল ছেঁড়া নিত্য দিনের দোসরে পরিণত হলো। এভাবে এক পাতা দুই পাতা করে এক সময় শেষ করলাম গোটা বই। এবার? কোথায়, কাকে দেবো প্রকাশের জন্যে? আমাদের মতো পাঠকের কাছে সেবা তখন সব সেরা প্রকাশনী। বইটা সেবায় পাঠিয়ে দেওয়ারই মনস্থির করলাম। কিন্তু তার আগে এটাকে মানুষ করতে হবে। বেশ কেয়কবার পড়ে, বহু কাটা-ছেঁড়া শেষে মোটামুটি একটা খসড়া দাঁড় করালাম। তারপর সেবায় পাঠাতে পাণ্ডুলিপিও তৈরি করলাম। ঢাকায় এসে সবার আগে আমার মেন্টর আম্মাকে দিলাম পড়তে। তিনি বললেন, চলে। এরপর ছোট বোন শারমিনকেও পড়ে দেখতে বললাম। বাসার সবাই সেবার বইয়ে আসক্ত ছিল। বোনও ছাড়পত্র দিলো। তারপর আল্লাহ ভরসা বলে সহস করে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলাম ১১৩, সেগুন বাগিচার ঠিকানায়। পাঠিয়ে দেওয়ার পর ভুলে গেলাম। কারণ, আমি তো জানি, ওটা বের হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কাজীদা তো আর আমাকে চেনেন না! তিনি কেন এই বই বের করতে যাবেন? বেশ কিছুদিন গত হওয়ার পর একদিন আম্মা বললেন, ‘কিরে, বইটা সেবায় পাঠালি, একটু খোঁজখবর নে!’ একদিন সাহসে বুক বেঁধে গেলাম সেবায়। ততদিনে সময় গড়িয়ে গেছে অনেক। কুদ্দুস সাহেব সম্ভবত আমাকে চিনতে পারেননি। জানতে চাইলাম, রানওয়ে জিরো এইটের কি অবস্থা? তিনি বেশ খোঁজাখুঁজির পর কাগজপত্রের বিশাল ঢিবির ভেতর থেকে আমার অতি যত্নে তৈরি সেই পাণ্ডুলিপিখানা বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে সাফ জানিয়ে দিলেন, ওই জিনিস সেবা বের করবে না। কি আর করা! তবু বাঁধন খুলে দেখতে চাইলাম, প্রত্যাখ্যানের কোনও কারণ দেখানো হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, হয়েছে। কাজীদা তার অনন্য সুন্দর লেখায় স্পষ্ট কয়েকটা বাক্য চিরকুট আকারে পাণ্ডুলিপির সাথে এঁটে দিয়েছেন, যার মোদ্দা কথা: লেখাটা আরও ঘষামাজা করতে হবে, তবেই যদি প্রকাশযোগ্য হয়! একথায় বুকে পানি এলো। বাড়ি ফিরে আবার ‘ঘষামাজার’ কাজে লেগে পড়লাম। খেটেখুটে ফের পাণ্ডলিপি তৈরি করে জমা দিলাম। সেটা ছিল ‘৮৫ সালের মাঝামাঝি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা হওয়ায় আমি চিটাগাং চলে গেছি। পরীক্ষা শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা শেষে বছরের শেষনাগাদ ঢাকায় ফিরে এলাম। হাতপা ঝাড়া, হাতে কাজ নেই। গল্পের বই পড়ার অবারিত অবসর। অক্টোবরের এক দিন হাজির হলাম সেবায়, আবার একটু খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছা। কুদ্দুস সাহেবের সামনে গিয়ে খবর জানতে চাইলাম। তিনি বলে উঠলেন, ‘আরে, সাহেব (মানে কাজীদা) তো আপনাকে খুঁজছেন। আমরা আপনার ঠিকানা হারিয়ে ফেলায় যোগাযোগ করতে পারছিলাম না।’ আমার তখন থরহরি কম্প! কাজীদাকে যেখানে সাধনা করেও এক নজর দেখার উপায় নেই, সেখানে তিনি আমাকে খুঁজছেন! কুদ্দুস সাহেব বললেন, ‘আপনি এখুনি উপরে চলে যান।’ কাজীদা তখন পুরোনো কাজী মঞ্জিলের কোনার দিকের একটা কামরায় বসতেন। কুদ্দুস সাহেবের কথামতো উপরে এসে সভয়ে টোকা দিলাম দরজায়। বুক ধকধক করছে! ভেতর থেকে ঢোকার অনুমতি এলো। কাজীদার অফিস কামরায় পা রাখলাম আমি। বিরাট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন আমাদের কাজীদা! আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, ‘বসুন!’ বসলাম। কুশল বিনিময় শেষে তিনি বললেন, ‘রানওয়ে জিরো এইট আপনি লিখেছেন?’ ইতিবাচক উত্তর দিয়ে বললাম, ‘আপনি আমাকে তুমি করেই বলুন।’ কাজীদা বললেন, ‘রানওয়ে জিরো এইট তো বেরিয়ে গেছে।’ বলে কি! রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছি। হাতপা কাঁপছে, বই বেরিয়েছে! জানতে চাইলাম, ‘একটা দেখতে পারি?’ কাজীদার উত্তর, ‘কেন নয়? তোমার বই তুমি দেখবে না?’ আসন ছেড়ে নিজ হাতে রানওয়ে জিরো এইটের ঝকঝকে দুটো কপি বের করে তুলে দিলেন আমার অনিশ্চিত হাতে। বললাম, ‘একটা অটোগ্রাফ দেওয়া যাবে?’ ‘অবশ্যই,’ বললেন তিনি। একটা কপি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি জানতে চাইলেন, ‘কি নাম লিখবো?’ আমার ডাক নাম বললাম তাকে। কাজীদা লিখলেন, ‘ডালিমের জন্যে অনেক শুভেচ্ছা, কা. আ. হোসেন, ২৪.১০.৮৫।’
অনেক কথাবার্তা শেষে কাজীদা জানতে চাইলেন, ‘এরপর কি লিখবে ভাবছো?’
ইতিমধ্যে সেবা থেকে কাজি মাহবুব হোসেন (নুরু ভাই)-এর কলমে ‘আলেয়ার পিছে’র হাত ধরে বাংলা ভাষায় ওয়েস্টার্নের পথ চলা শুরু হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি ওয়েস্টার্ন তখন বাজারে। বললাম, ‘ওয়েস্টার্ন লিখবো ভাবছি।’
‘বেশ তো লিখ,’ বললেন কাজীদা। ‘আমরা তো ওয়েস্টার্ন লেখার জন্যে লেখক খুঁজছি। এক কাজ করো, প্রথম একটা অধ্যায় লিখে আমাকে দেখিয়ে নিও। তারপর বাকিটা কিভাবে লিখবে বাতলে দেবো।’
স্বয়ং কাজীদার কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে আর দেরি করিনি। নূরানীর কাছে পাওয়া লুই লা’মুরের দ্য ডার্ক ক্যানিয়ন হাতের কাছেই ছিল। চার আউট-ল আর এক তরুণের রোমহর্ষক কাহিনী। পরামর্শমতো প্রথম অধ্যায় শেষ করে কাজীদার হাতে দিয়ে এলাম। কদিন পর দেখা করলাম কাজীদার সাথে, তিনি টুকটাক কিছু সংশোধন শেষে সেই অংশটুকু ফিরিয়ে দিয়ে দ্রুত বইটা শেষ করে জমা দিতে বললেন। শুরু হলো আমার প্রথম ওয়েস্টার্ন লেখার অ্যাসাইনমেন্ট। এরপর দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, উত্তপ্ত জনপদ, সংঘাত, নীল নকশা, রুদ্ররোষ, নিষিদ্ধ প্রান্তরের মতো একে একে সেবায় আরও অনেকগুলো ওয়েস্টার্ন লিখেছি; সবকটাই আল্লাহর রহমতে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। রানওয়ে জিরো এইট ও ওয়েস্টার্ন ছাড়াও সেবা থেকে আমার বেশ কয়েকটি রোমাঞ্চোপন্যাস বেরিয়েছিল: শুভ্রশত্রু, অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস, উপদ্রব।
সেবায় লিখতে গিয়ে সেবার অন্য লেখক ও শিল্পীর সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে আছেন সর্বজন প্রিয় শেখ আবদুল হাকিম, কাজি মাহবুব হোসেন, রওশন জামিল (রওশন জামিল আমার বেশিরভাগ ওয়েস্টার্ন ও অন্যান্য বই সম্পাদনা করেছেন), রকিব হাসান, আসাদুজ্জমান (সেবার বইয়ের কিছু অনন্য প্রচ্ছদ তার হাতেই সৃষ্টি হয়েছে), ধ্রুব এষ (রহস্য পত্রিকার শিল্প সম্পাদক), খসরু চৌধুরী, নিয়াজ মোর্শেদ, খন্দকার মাজহারুল করিম, ইফতেখার আমিন, শরাফত খান (প্রচ্ছদ শিল্পী), আলীম আজিজ, প্রমুখ। আলীম আজিজ আমাকে বেশ কিছু ওয়েস্টার্ন যোগাড় করে দিয়েছিল, আমার ওয়েস্টার্নের চমৎকার কিছু প্রচ্ছদও আলীমের নিপুণ হাতের কাজ। এদের দুএকজনের সাথে এখনও যোগাযোগ আছে। হাকিম ভাই, নুরু ভাই ও খন্দকার মাজহারুল করিম মারা গেছেন।
কাজীদার পঞ্চ রোমাঞ্চের কমিক্স ভার্শন বের হওয়ার পর দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর একবার তার অটাগ্রাফ নিয়েছি। তিনি এবার লিখলেন: ‘সুপ্রিয় শওকত হোসেনকে অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাÑকাজী আনোয়ার হোসেন, ৭.১২.২০১৯।’
কাজীদার মৃত্যুর বছর দুই আগে আমার মেয়েকে নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেটাই শেষ দেখা ছিল। আমার অনুবাদে প্রকাশিত আইজ্যাক আসিমভের আই, রোবট বইটা কাজীদাকে উৎসর্গ করেছি। সেটারই একটা কপি তাকে দিতে গিয়েছিলাম। বেশ খুশি হয়েছিলেন তিনি।