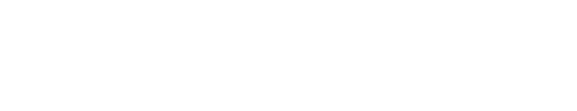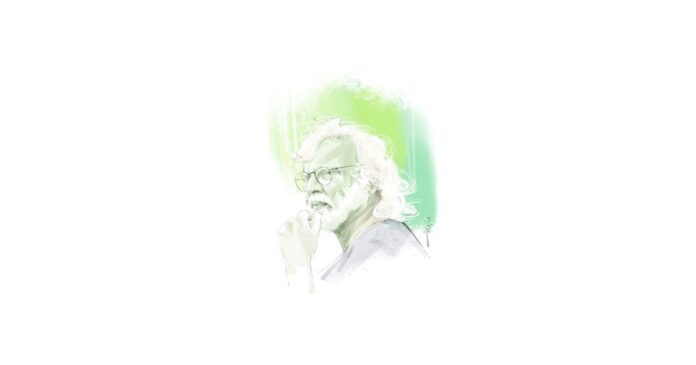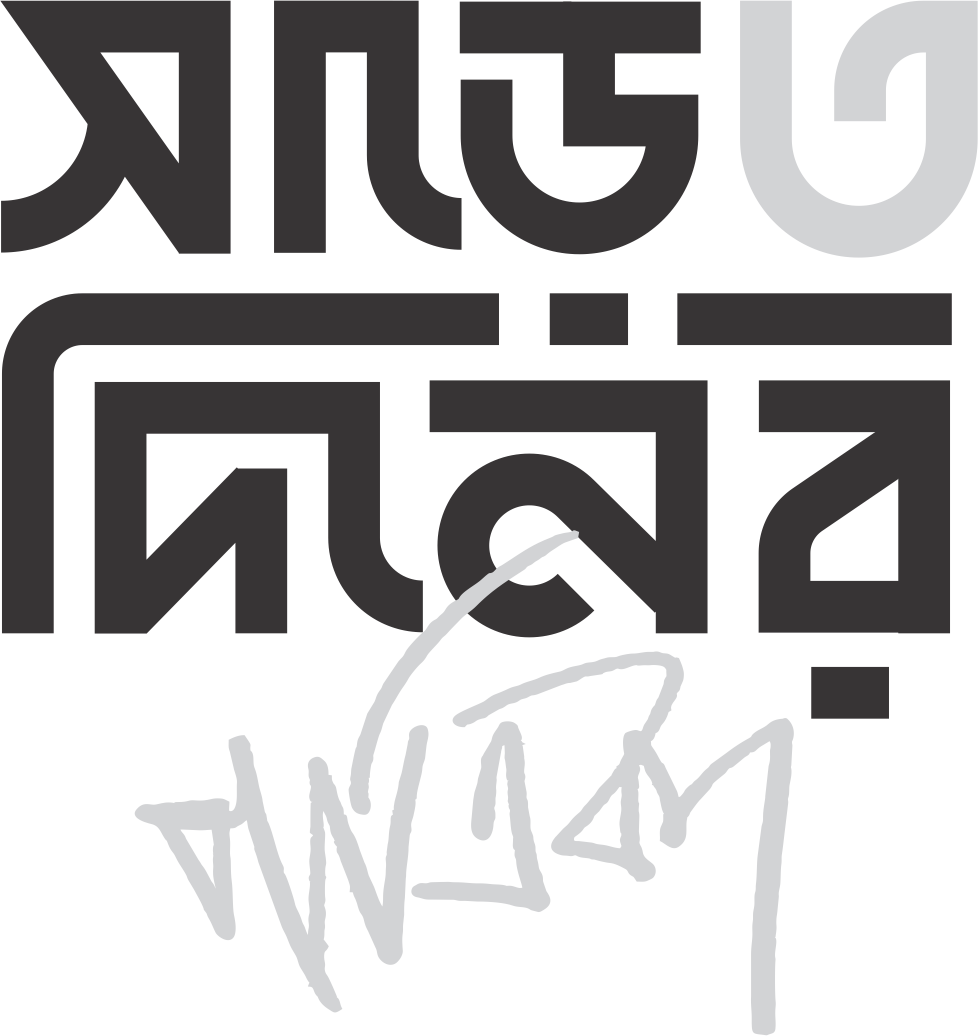মানজারে হাসীন মুরাদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক। তিনি বাংলাদেশে বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা। এক সময় চলচ্চিত্র নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন কাফকার শহর প্রাগের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ‘চার্লস ইউনিভার্সিটি’তে। এরপর দেশে ফিরে শুরু করেছিলেন চলচ্চিত্র আন্দোলন। সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার জন্য গুণী এই নির্মাতার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এহসান হায়দার
- আপনি তো চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষকতা করছেন, কেমন বোধ করেন বিষয়টি নিয়ে?
মানজারে হাসীন মুরাদ : শিক্ষকতা একটি মর্যাদার পেশা; কিন্তু আমি তো চলচ্চিত্রকারও। আমি যা জানি তা শিক্ষার্থীদের মাঝে জানানোর মধ্যে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করছি। এ পেশাকে পূর্ণাঙ্গ লালন করি।
- বিকল্পধারা চলচ্চিত্র আন্দোলন বিষয়টি সম্পর্কে বলবেন?
মানজারে হাসীন মুরাদ : আমরা যারা ছোট ছবি নির্মাণ করতাম, আমাদের সঙ্গে ব্যবসাসফল বা বাণিজ্যিক ছবির কাজের মিল ছিল না কখনও। তখন তো মূলত শর্টফিল্মই বানানো হতো। ৩০-৩৫ মিনিটের। এই ছবিগুলো বানাতে গিয়ে আমাদের যেসব সমস্যায় পড়তে হয়, ডিস্ট্রিবিউশন ও প্রোডাকশন নিয়ে এটা কমন ব্যাপার ছিল। এ সকল কারণে আমাদের যারা ছবি বানাচ্ছিলেন তাদের কাজের একটা মিল রয়েছে শর্টফিল্মের সঙ্গে। এরপর একটা আন্দোলনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমরা। এইভাবেই ’৮৬ সালে আমাদের একটি সংগঠন তৈরি হলোÑ‘বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরাম’। এটা বিকল্প চলচ্চিত্র আন্দোলন হয়ে উঠেছিল এক সময়।
- বিকল্পধারা চলচ্চিত্র বিষয়ে কোনো গ্রন্থ রয়েছে?
মানজারে হাসীন মুরাদ : ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সংগঠনটি। তিন যুগেরও অধিক সময়, আমরা এখন পর্যন্ত ঐ একই চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করছি। আপনি যদি আরও ভালো করে এটা নিয়ে বুঝতে চান, তাহলে আমাদের প্রথম ১০-১২ বছরের কাজ-ইতিহাস নিয়ে একটা বই বেরিয়েছে। সেটা দেখতে পারেন।
- তথ্যচিত্র আর প্রামাণ্যচিত্রÑএই দুটোর মধ্যে তফাৎ যদি বুঝতে চাই…
মানজারে হাসীন মুরাদ : আপনি যেমন জানেন কাহিনিচিত্রের ব্যাপারে, নানা ধরনের কাহিনিচিত্র আছে। সাদামাটাভাবে যেটাকে আমরা বলি ‘ফিল্ম জনরা’। যেমন আপনি জানেন, কমেডি বলতে যে হাস্যরসাত্মক ফিল্ম নির্মিত হয়। এরকম চলচ্চিত্র অনেকে তৈরি করে এটা আইডিন্টিফাই করার জন্য যে, এই ছবিটার মূল ভাবনা কী। এই জনরার বিষয়টি প্রামাণ্যচিত্রেও হচ্ছে। হয়তো বলা হলো তথ্যচিত্র, এর কারণ হচ্ছে প্রামাণ্যচিত্রে তথ্যটাকে প্রাধান্য দেওয়া। যে দর্শক তথ্য দেখতে চায় তার কাছে তথ্যটা আরও বেশি পৌঁছাতে হবে। কোনো কোনো ছবির হয়তো এডুকেশনাল অ্যাসপেক্টে বেশি, এগুলোর মধ্যে দিয়ে ইনফরমালি মানুষকে বেশি তথ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা যায়। কোনো ছবি পলিটিক্যাল, এই ছবিতে রাজনৈতিক দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে বানানো হয়। আমরা যখন ডকুমেন্টারি বলি, তখন এটার সাথে আমরা বলি যে অকাহিনিমূলক ফিল্ম বা নন-ফিকশন, এরই একটা অংশ হচ্ছে প্রমাণ্যচিত্র। যেটা যেকোনো পারপাসে হতে পারে। এটা এডুকেশনের জন্য হতে পারে, রাজনৈতিকভাবে হতে পারে, প্রোপাগান্ডা পারপাসেও হতে পারে; কিন্তু এর সাথে শিল্পের একটা সম্পর্ক থাকবে। আর অন্য ধরনের প্রামাণ্যধর্মী চলচ্চিত্র বা তথ্যচিত্র, যেখানে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অত বেশি নেই; কিন্তু সেটাও আবার দর্শকের জন্য প্রয়োজন। সেটাকে আমরা বলছি নন-ফিকশন। নন-ফিকশনের একটা অংশ হচ্ছে প্রামাণ্যচিত্র, যেখানে সব থাকতে পারে; কিন্তু সেটাতে শৈল্পিক দিকটা শিল্পগত যে ভাষা, এই ভাষার সৃজনশীল প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে, যেকোনো শিল্প যদিও সার্থক হয়ে ওঠে সেখানে যে তথ্যগুলো আসছে তার অভিঘাত মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সে কারণে বলছি যে, তথ্যসমৃদ্ধ বা এডুকেশনাল বা পলিটিক্যাল যে ছবিতে শিল্পের মাত্রাটা থাকবে, সেটা ডকুমেন্টারি, অন্যগুলো নন-ফিকশন।
- প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই অর্থের যোগান কীভাবে হয়, আপনিই সম্ভবত এই ধারাতে শুরুর দিকে কাজ শুরু করেছেনÑ
মানজারে হাসীন মুরাদ : না আমি একা না, আমাদের জেনারেশন বলাই ভালো। প্রামাণ্যচিত্রে একই সাথে তারেক মাসুদ, তানভীর মোকাম্মেল কিছুটা কাজ করেছেন। আমাদের আগে সৈয়দ বজলে হোসেন কাজ করেছেনÑজহির রায়হান তো আছেনই। প্রামাণ্যচিত্র আমাদের এখানে এত জনপ্রিয় ছিল না। তাছাড়া হলেও দেখানোর কোনো সুযোগ নাই। তখন ধরুন ৮০ কিংবা ৯০’র দশকে টেলিভিশন বলতে, কেবল বাংলাদেশ টেলিভিশন ছিল। এটা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং সরকার যে বিষয়গুলো জনগণের নজরে আনতে চান না, তখন সেগুলো দেখানো হয়নি। কিছু ভালো ছবি তৈরি হলেও সেগুলো দেখানো হয়নি, দর্শক দেখতে পারেনি। আর অর্থের কথা বললেন, অর্থটা কাহিনিচিত্র হোক আর প্রামাণ্যচিত্রই হোক, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, অর্থ কিছু লাগে।
- আপনি যখন নিজে স্ক্রিপ্ট করে জমা দিচ্ছেন সেটা দেখে কতটুকু আগ্রহী হয় এনজিওগুলো?
মানজারে হাসীন মুরাদ : এটা এক কথায় বলা যাবে না আগ্রহী, আবার আগ্রহী না এটাও বলা যাবে না। দুরকমই আছে। এখন যেটা হয়Ñসরকার যদি লগ্নি করে, তাহলে তারা চায় তাদের প্রচার, তাদের গুণগান করা। মানুষ যেন সেটা শুনে তাদের পক্ষে তাদের সাপোর্টার হয়ে ওঠে বা তাদের সহযোগী হয়ে ওঠে।
আমি যদি অন্যভাবে বলি, মনে করুন কোনো একটা অ্যাড ফিল্ম বানানো হলো, তাহলে কাজটা কী? যে টাকা লগ্নি করে সে চায় অ্যাডের মধ্য দিয়ে মানুষজনের কাছে এই ইনফরমেশন পৌঁছানো যে, তার পণ্য সবচেয়ে ভালো। তার জন্য যতপ্রকার আয়োজন করা দরকার করে। সুতরাং কেউ কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত চলচ্চিত্রে অর্থ বিনিয়োগ করবে? আপনি সচেতন থাকেন, ধরেন আমাদের দেশে নারীর উন্নয়ন এখনো পিছিয়ে আছেÑএখন একটা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নারী উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তাদের নিজস্ব কিছু বিষয় আছে, হতে পারে নারীর সামাজিক অবস্থা। তারা হয়তো একটা ‘প্রেসক্রিপশন’ করে এইভাবে যদি কাজ করা যায় তাহলে নারীর উন্নয়ন হবে। এখন সেখানে যদি আপনি এমন কিছু ক্যারেক্টার বের করতে পারেন যারা খুবই উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে, তারা তাদের জীবন দিয়েÑকর্ম দিয়ে, সংগ্রাম দিয়েÑ নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং আরও কয়েকজনকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন বা তারা নিজেদের জীবনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে একজন সংগ্রামী মানুষ সংগ্রাম করে তার জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। আপনি যদি একটা দেশকে জানতে চান, তাহলে সেদেশের ইতিহাস জানবেন, তাই তো? একটা এনজিও নারী উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে, তাকে আপনি যদি বলেন, আপনারা তো নারী উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন, আপনাদের যারা ক্লায়েন্ট হবে তাদের জানানো দরকার আপনাদের ইতিহাসটা। তখন হয়তো তারা দেখল কথাটা তো ঠিক। একটা নারীকে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে আরেকজন নারীর সংগ্রামের কথা বলা উচিত। এই ভূমিকাগুলো তাদেরও কাজে লাগবে। সামাজিকভাবে আমি যদি একটা প্রামাণ্যচিত্র বানাতে চাই সেটারও কাজে লাগবে। এখন আমরা নির্মাতারা এভাবে যদি বোঝাতে পারি একেবারে যে হয় না তা না। আমি নিজেও কিছু এমন ছবি তৈরি করেছি। আমি তাদের বুঝিয়েছি এই কাজটা আপনাদেরও কাজে লাগবে, আবার আমিও একটা ভালো ফিল্ম বানানোর চেষ্টা করলাম।
- প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে সমাজের মানুষ কী দেখে?
মানজারে হাসীন মুরাদ : কাহিনিচিত্র হোক বা প্রামাণ্যচিত্র আপনাকে শুধু বিনোদনই দেয় না। দিলেও সেটার মাত্রাটা ভিন্ন। একটা পথ হচ্ছে বেশি করে তাদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দেওয়া। আরেকটা পথ হচ্ছে বোঝানোÑযারা নীতি-নির্ধারক হোন তারা যদি বোঝেন, না এটা তো ভালোÑতবে বিষয়টি সহজ হয়। আমার একটা সিনেমা আছে, যেটা হচ্ছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে। এখন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পরিচিত এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষজন সবাই কমবেশি জানে। যখন বলা হয়েছে, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনভিত্তিক একটি ছবি, তখন বেশিরভাগ মানুষ এটা দেখতে আগ্রহী হয়েছে, শিক্ষকরাও এটা দেখেছেন।
- আমাদের বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রের গ্রন্থসম্ভার কেমন?
মানজারে হাসীন মুরাদ : আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নিয়ে বই আছে বাংলা ভাষায় খুবই কম। আর যা তা তো সবই ইংরেজিতে। চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ধরনের বই হয়ে থাকে। বিভিন্ন সেক্টরের কাজের ওপর। তবে বাংলা ভাষার বইগুলো সব যে চোখে পড়েছে এমন নয়, মান সম্পর্কে বলতে পারব না। অনুপম হায়াতের কথা বলতে পারি, যিনি সিনেমার ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার কাইজার চৌধুরী লিখতেন একটা সময়েÑতিনি পরে শিশুসাহিত্যে মন দেন, ফলে তাঁর সম্ভাবনা থাকলেও মরে গেছে। ভালো অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন, এখানে তা নেই।
- বাংলাদেশে মূলধারা বা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বর্তমান যে অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় আপনি দেখেন?
মানজারে হাসীন মুরাদ : যেকোনো কিছুই তো পরিবর্তন করা সম্ভব, যদি আপনার ইচ্ছে থাকে। এগুলো তো সবই মনুষ্যসৃষ্টি। সুতরাং যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বা সামাজিক ক্ষমতায় আছে তারা এটাকে এভাবে তৈরি করেছে। একটা কথা আমি সরাসরি বলবÑএকটা জিনিস যদি পচে যায় তখন আর সেটা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের দেশে যেটা হয়েছে, মূলধারা আমি বলি না, আমি বলি বাণিজ্যিক ধারা। কারণ মূলধারা বললে আপনার একটা ভুল ধারণা হবে। এটাই বোধ হয় চলচ্চিত্র। এটা তো চলচ্চিত্র না। এটায় চলচ্চিত্রের কিছু উপাদান আছে, যে উপাদানগুলো মনে করুন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আপনি তার ছবি তুললেন। আপনি একজন মানুষের ছবিই দেখবেন। এখন আমাদের দেশে আপনি যদি দেখেন শুরুতে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র, তখন তো আর অন্য কোনো চলচ্চিত্র ছিল না। ১৯৪৭ সালের পরে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র দেখেন, শুরুটা কিন্তু খারাপ ছিল না। ওই অর্থে নোংরামিও ছিল না, অবাস্তবতাও ছিল না, একটা সাধারণ জীবনকে তখন খুব সুন্দর করে চেনা যেত। তারপর এখানে একটা সমস্যা হলো, মূলত ভারতীয় ছবি ও পাকিস্তানি ছবির সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে। তাদের হয়তো অভিনেতা ভালো ছিল, কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা ছিল বা নতুন দেশে যে ধরনের মানসিকতার মানুষ থাকা দরকার, ছিল। শরীর প্রদর্শন বা যৌন আবেদনটাও তাদের সহজ ছিল। সেটা যখন অনুকরণ করা শুরু করল এদেশে, প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ওইরকম হলো। এরপর পাক-ভারত যুদ্ধের পর বিদেশি কোনো ছবি বাংলাদেশে দেখানো যেত না। প্রটেকশনে নেওয়া হলো। তার মানে কী হলো, আপনি ব্যবসা করছেন কিন্তু আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সাধারণত এটা হলে আপনি কী করবেন? ওই সুযোগটা নিয়ে আপনি আপনার প্রোডাক্টটাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে যারা ফিল্মে এসেছেন তাদেরকে বলব, তারা তখন মনে করেছেনÑআমার তো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, আমি যা দেব দর্শক তাই দেখতে বাধ্য। তখন তো সিনেমা ছাড়া আর কিছুই নাই। সিনেমাহলে যেতেই হতো সিনেমা দেখতে।
- সরকারি অনুদানে এখন সিনেমা নির্মিত হচ্ছে। কাহিনিচিত্রের মতো প্রামাণ্যচিত্রেও এমন অনুদান থাকে কি?
মানজারে হাসীন মুরাদ : নানান ধরনের দেন-দরবার, আন্দোলন, সেমিনারের মাধ্যমে আমরা সরকারকে বোঝাতে পেরেছিলাম যৌক্তিকতা। তখন থেকে কাহিনিচিত্রের পাশাপাশি প্রামাণ্যচিত্রেও অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়টা একটা বড় আকারে পরিবর্তন ঘটেছে। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, অনুদান কথাটা কিন্তু চালু করা হয়েছিল কেবল শিল্পসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের জন্য, বাণিজ্যিক সিনেমার জন্য নয়। এখন দেখা যাচ্ছে, যারা দায়িত্বে আছে এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র সেই অর্থে প্রযোজক পাচ্ছে না, তারাও কিন্তু সরকারের কাছে দাবি করছে তাদেরও অনুদান দেওয়া হোক। চলচ্চিত্রের যেকোনো ধারাতেই অনুদান দেওয়া উচিত। আর প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে এর দর্শক সবসময়ই কম।
- এখন চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, সরকারের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এরমধ্যে দিয়ে আমাদের নির্মাণে কারিগরি ব্যাপারগুলো কতটুকু এগিয়েছে?
মানজারে হাসীন মুরাদ : আমাদের দেশে সাধারণ মানের প্রযুক্তি দিয়েই সিনেমা নির্মাণ অসম্ভব কিছু নয়। এটা তো আপনি জানেন সবকিছুরই একটা চর্চার এবং ক্রিয়েটিভিটির প্রশ্ন আছে। চর্চাটা চালু না থাকলে প্রাথমিক স্তরে থাকবেই। ওটার চাইতে আমি বলবো, আমাদের দেশে আগে কখনো টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র শি¶া চালু ছিল না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। এখন যেহেতু হয়েছে এটা অবশ্য ভালো। সমাজের সুধীমহল মনে করছেন সিনেমাশি¶ার প্রয়োজন আছে। আগে তো মনে করা হতো সিনেমা আবার কী শেখার আছে? সিনেমাতে আবার কী শিখবে। এখন এই জিনিসটা কমে এসেছে। সমস্যা হচ্ছে পাঠ্যক্রমের কোন সামঞ্জস্য নেই, বাংলাতে ভালো বই নেই। একেকটা ভার্সিটির সাথে আরেকটা ভার্সিটির মিল নেই, দেখা গেলো ঢাবিতে যা পড়ানো হয় জাবিতে তা পড়ানো হয় না। এর বড়ো কারণ প্রতিটা প্রতিষ্ঠান মনে করছে আমি যেটা করছি সেটাই বোধ-হয় ঠিক। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট তৈরী হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো কারিগরি অবকাঠামো নেই। আপনি সমাজবিজ্ঞান পড়তে পারেন কারিগরি অবকাঠামো ছাড়া কিন্তু ফলিত রসায়ন পড়তে পারবেন না ল্যাব ছাড়া, তফাৎটা এখানেই।
- বাংলাদেশের শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু বলবেন কী?
মানজারে হাসীন মুরাদ : আমাদের দেশে শিশুতোষ চলচ্চিত্র কিছু তৈরী আছে যেমন ধরুন সুভাষ দত্তের ডুমুরের ফুল। আজিজুর রহমানের ছুটির ঘন্টা, তারপর মোরশেদুল ইসলামের আমার বন্ধু রাশেদ ভালো শিশুতোষ চলচ্চিত্র, দীপু নাম্বার টু, এই কয়েকটায়। আমাদের এখানে একটা ধারণা ছিল শিশুদের সিনেমা দেখা যাবে না। এটা বেশিরভাগ বাড়িতে মানতো না। ছোটবেলায় এবং কিশোর হওয়ার পরও সিনেমা দেখতে দিতো না। সিনেমা খারাপ। এজন্য শিশুরা এ্যাক্টিভ দর্শক হয়ে ওঠেনি এবং তাদের জন্য সিনেমাও বানানো হয়নি। যারা বানিয়েছেন তারা কর্মার্শিয়াল সিনেমার জায়গায় কিছুটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই বানিয়েছেন।