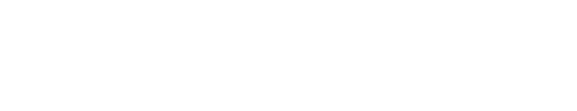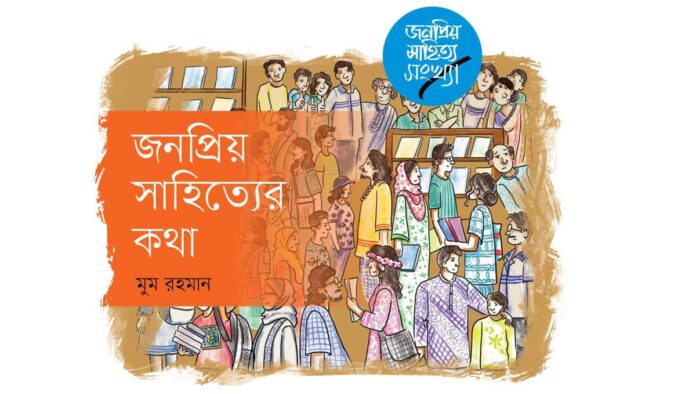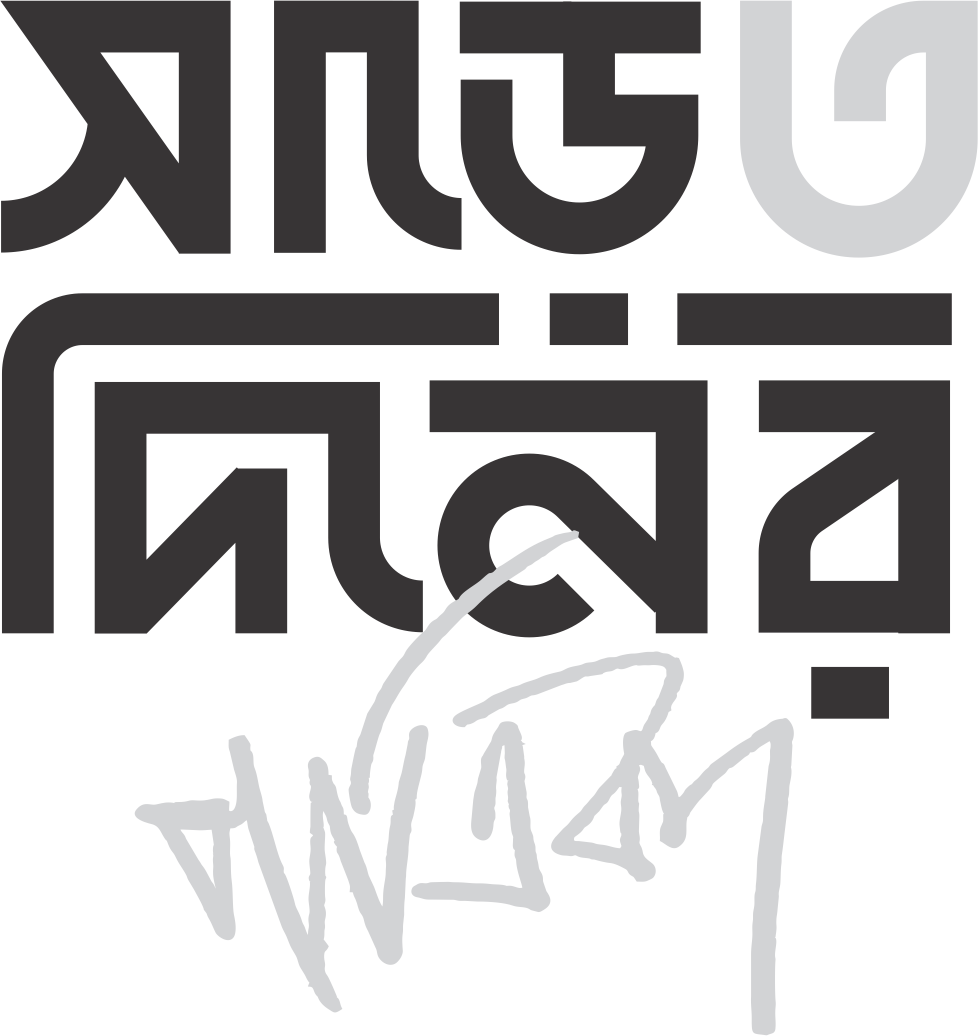জিওফ্রি চসার (১৩৪৩-১৪০০) ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি ছিলেন। নিজের সময় থেকে তিনি এগিয়ে ছিলেন, তাকে অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যের জনক বলে থাকেন। শেকসপিয়রেরও জন্মের আগে চসার ইংরেজি ভাষাকে আধুনিকিকরণ করেছেন। সহস্র শব্দ যোগ করেছেন। ফরাসী ও ইতালীয় প্রভাব বলয়ের বাইরে ইংরেজিকে তিনি সাধারণ লোকের ভাষার নিকটবর্তী করেছিলেন। ফলে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে আজকের দিনে চসারের ইংরেজি বোধগম্য নয়, আধুনিক ইংরেজিতে তা অনূদীত হয়ে থাকে এবং তারপরও চসার জনপ্রিয়।
চসারের উদাহরণটা এই কারণে দিলাম যে, জনপ্রিয় আর ধ্রুপদী সাহিত্যের একটা গোপন কোন্দল চলতেই থাকে। সেই কোন্দলে চসার, শেকসপিয়র, হোমারগণ একেকজন উজ্বল ব্যতিক্রম। তারা তাদের সময়ে যেমন জনপ্রিয়, শত বছর পেরিয়েও জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথের মতো তারাও মহাকালের কাছে কৌতুহলে জানতে চাইতে পারেন, ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছো বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে।’ (১৪০০)
জনপ্রিয় সাহিত্য, শিল্প বলতে সহজ কথায় তাই বলা যায় যেটা জন মানুষ গ্রহণ করেছে, যেটা লোকপ্রিয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে বেস্টসেলার দিয়েও আজকের দিনে জনপ্রিয়তার নিরিখ করা হয়। যেমন পাওলো কোহেলহো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় লেখক মনে করা হয়। ‘দ্য এলকেমিস্ট’ টানা ৪০০ সপ্তাহ ধরে নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় ছিলো। তার দার্শনিক প্রজ্ঞা, উপকথার ভঙ্গিতে, সরল ভাষায় গভীর কথা বলা তাকে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক করে রেখেছে।
আমাদের বাংলাদেশেও জনপ্রিয়তার কথা আসলেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা আসে। বঙ্কিম কিংবা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তার লোকপ্রিয়তা অধিক ছিলো। কিন্তু জনপ্রিয়তা বা লোকপ্রিয়তার একটা বড় সমস্যা হলো, সমালোচক, তাত্ত্বিক, অধ্যাপক কিংবা নীরিক্ষামূলক কিংবা সিরিয়াস ঘরাণার লেখকরা তাকে গুরুত্ব দেন না। একজন কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য সমাজে, বিশেষ করে একাডেমিক ক্ষেত্রে যতোটা গ্রহণযোগ্যতা আছে ততো শরৎচন্দ্রের ছিলো না, অন্তত তার সময়ে। তবে সময়ের আবর্তনে আজকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শরৎচন্দ্র এবং তার সাহিত্য যেমন পাঠ্য, উচ্চতর গবেষণার বিষয় তেমনি কমলকুমার মজুমদার ও তার সাহিত্যও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, যে ঢালাও অভিযোগটি আছে যে জনপ্রিয় সাহিত্যিক টিকবে না, তা সব সময় সঠিক নয়।
এ রকম একটি ধারণার অন্যতম কারণ হলো, একটু পড়ুয়া বা নিজেকে অধিক জ্ঞানী বিবেচনা করা লোকেরা জনরুচিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। জনগণ একটি ঢালাও শব্দ। জনগণ শব্দের মধ্যে, উচ্চ শিক্ষিত থেকে গণ্ডমূর্খও রয়ে যায়। জনগণের মধ্যে রয়েছে অনেক শ্রেণীভেদ। সেই দিক থেকে বিতর্ক তখন গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তার দিকে চলে যায়। গণতন্ত্রে যেমন একজন চোরের ভোট আর একজন পুরোহিতের ভোটও সমান, শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে তেমনটা হলে বিপদও। প্রতিটি সাহিত্যের একটা নির্দিষ্ট পাঠক আছে, প্রতিটি সিনেমার একদল নির্দিষ্ট দর্শক আছে। সবাই কাফকা পড়বে না, সবাই রাওলিং পড়বে না। সবাই ‘টাইটানিক’ দেখবে না, সবাই ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখবে না। সেই কারণেই ‘দ্য ট্রায়াল’-এর পাঠক ‘হ্যারি পটার’-এর পাঠক এক নয়। তাই বলে, এক শ্রেণীর পাঠক আরেক শ্রেণীর পাঠকের প্রতি উন্নাসিকতা দেখাতে দেখাতে পারে না। এই উন্নাসিকতা শিল্প-সাহিত্যের জন্য স্বাস্থকর নয়। কারণ একটা নির্দিষ্ট সময় না-গেলে আমরা কোন কিছুর স্থায়ীত্ব, এমনকি মান নিয়েই চূড়ান্ত মন্তব্য করতে পারি না।
সর্বোপরি, মানদণ্ডেরও তো ভেদাভেদ হয়। যে সায়েন্স ফিকশনকে এক সময় সাহিত্য সমালোচকরা সাহিত্যের কৌলিন আসরে ঠাঁই দিতে চাইতেন না, সেই সায়েন্স ফিকশন এলান পো, জুলভার্ন, ওয়েলস, এসিমভ, ক্লার্ক কিংবা ফিলিপ কে ডিক প্রমুখ লেখকের হাত ধরে ধ্রুপদী সাহিত্য আসরেও টিকে গেছে। একই কথা ফ্যান্টাসি কিংবা গোয়েন্দা কাহিনীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কখনো কখনো ‘লোকে যারে ভালো বলে সেই ভালো হয়’Ñ কথাও প্রযোজ্য।
এ কথা ঠিক, বাংলা সাহিত্যাসরে দস্যু বনহুর, কিরীটী, কুয়াশা, মাসুদ রানাÑ ইত্যাদি গোয়েন্দ কাহিনী তেমন করে আলোচ্য নয়, অথচ বই বিক্রির তালিকায় তারা নিঃসন্দেহে শীর্ষে। তরুণদের কাছে ‘মাসুদ রানা’ যতোটা জনপ্রিয় ছিলো, অভিভাবকদের ততোটাই চক্ষুশূল ছিলো। ‘তিন গোয়েন্দা’ কিশোর পাঠকের আরাধ্য ছিলো, কিন্তু সাহিত্যপ্রেমীর কাছে তার গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তাতে অবশ্য খুব বেশি লাভ-ক্ষতি কারোই হয় না। কারণ প্রত্যেকে তার নির্ধারিত শিল্পকর্মেরও একটা বাজার এবং নির্দিষ্ট ভোক্তার কথায় মাথায় রাখেন।
বাজারে বড় কোম্পানি যখন একটা পণ্য আনে তখন সে টার্গেট গ্রুপ (টিজি) ঠিক করে নেয়। এই টিজি কিন্তু সবাই না। একটা চিপস ছেলে বুড়ো সবাই কেনে না, একটা চা পাতা ছেলেবুড়ো সবাই কেনে না। কাজেই সাহিত্য, সিনেমা, নাটকের ক্ষেত্রেও এমন নির্ধারিত টিজি রয়েছে। যে নির্দিষ্ট লেখক বা শিল্পী তার কাঙ্খিত টিজি ঠিক করে কাজ করেন তিনি জনপ্রিয়তার ধাপগুলো পার হতে পারেন। কারণ জনপ্রিয়তার সঙ্গে বাজার রুচির সম্পর্কটা একেবারে হরিহর সংযোগ।
এইখানে আবার জনপ্রিয় সাহিত্য কখনোবা বাণিজ্যিক সাহিত্য হয়ে ওঠে। তখনই সমস্যাটা তৈরি হয়। কেননা, লোকপ্রিয়তার একটা বড় অসুবিধাও হলো সেটা জনগণ কি খায়, লোকে কি চায় তার চাহিদা মেপে তৈরি হয়। এক্ষেত্রেই জনপ্রিয় শিল্প-সাহিত্যের মান নিয়ে সম্পাদক-সমালোচকদের প্রশ্ন করার সুযোগ রয়ে যায়। বাণিজ্যিকভাবে সফল মানেই যে তা শিল্পমানোত্তীর্ণ হবে তা কিন্তু নয়। জনরুচিকে খুশি করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে লেখক-শিল্পীকে তার নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিতে হয়। অর্থ বা খ্যাতির সঙ্গে সব সময় গুরুত্ব বা মানটা সুনিশ্চিত করা যায় না। বিশেষত সাহিত্য ক্ষেত্রে।
সাহিত্য কোনভাবেই পণ্য নির্ভর নয়। অথচ, বই একটি পণ্য। বই বিক্রেতা এবং প্রকাশককে বই বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কোন কোন লেখককেও লিখেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সেক্ষেত্রে কখনোবা আপোষ করতে হয় শিল্পরুচির দুয়ারে। তার একটা নজির আমরা এ দেশের বইবিক্রির অন্যতম প্লাটফর্মগুলোতে গেলেও দেখতে পাবো। অধিকাংশ সময়ই তাদের বিক্রি তালিকার শীর্ষে তাকালে বিশুদ্ধ সাহিত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ সাহিত্য তার নিজের সময়ে প্রবল জনপ্রিয় না-হলেও একটা সময় ধ্রুপদী মর্যাদা লাভ করে যার ফলে সময় গেলে তার ক্রেতাও বাড়ে। কাল্ট ফিল্ম বা ফিকশনের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন ঘটেছে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও। আজও বাংলাদেশে প্রত্যেক বইমেলাতে তাদের বই বিক্রির তালিকাটা কম নয়। অন্যদিকে সাহিত্যের বাইরেও তো বই আছে। যেমন রান্নার বই, ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, ধর্মীয় বইÑ এগুলোর জনপ্রিয়তাও বিক্রির বিবেচনায় কম নয়, তবে সাহিত্যের বিবেচনায় এদের অবস্থান শীর্ষে নয়। সাহিত্য কর্ম যখন পণ্য হিসেবে আসে তখন বাজার সংস্কৃতির দিকে নজর রাখাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।
‘বেদের মেয়ে জোসনা’ সিনেমা হিসেবে যথেষ্ট বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের লোকপ্রিয় গল্পের বয়ানভঙ্গি, চরিত্রায়ণকে আত্মীকরণ করেছিলো এই সিনেমা। গ্রামীন মানুষের ফ্যান্টাসি ও শ্রেণী চরিত্র এই সিনেমায় থাকলেও দুঃখজনক হলেও সত্য এই সিনেমাকে বোদ্ধা সমালোচকরা শিল্পরুচির বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলেন না। লোকপ্রিয় হলেও সেই সিনেমা চলচ্চিত্র শিল্পে দীর্ঘস্থায়ী কোন ভূমিকা রাখেনি। একজন গদার, ফেলেনি, সত্যজিৎ তো দূরের কথা তোফাজ্বল হোসেন বকুল (বেদের মেয়ে জোসনা’র নির্মাতা)-কে আমরা আলমগীর কবির, তারেক মাসুদের সঙ্গে এক কাতারে দেখতে বসি না, বিবেচনা করতে বসি না। একই কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যবসার সঙ্গে জনপ্রিয়তার সম্পর্ক থাকতে হয়, শিল্পের সঙ্গে থাকাটা মূখ্য নয়।
একজন মাহমুদুল হক, হাসান আজিজুল হক তাদের জীবিতকালে ধ্রুপদী সাহিত্যিকের সম্মান পেয়ে যান। এটা ঠিক, তারা অল্পবিস্তর জনপ্রিয়তাও পান। কিন্তু যে প্রবল জনপ্রিয়তা একজন ইমদাদুল হক মিলন বা আনিসুল হক অর্জন করেন তা প্রশ্নাতীত। অন্যদিকে তাদের সাহিত্যকে ধ্রুপদী কাতারে আসবে কি আসবে না সে প্রশ্ন সময়ের হাতে নির্ধারিত হবে। কেননা সব সময়, সাহিত্যের জনপ্রিয়তা আর মান এক কাতারে চলে না। রোমেনা আফাজের ‘দস্যু বনহুর’ আমরা পড়েছি গোগ্রাসে, তবে আজ আর তা পড়ার প্রয়োজন বোধ করি না। এই যে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া সেটাও একজন সাহিত্যিকের ট্র্যাজেডি। কেবল জনপ্রিয়তার প্রয়োজন মেপে যে সাহিত্য রচিত হয়, সে সাহিত্যের প্রয়োজন সময় গেলে ফুরিয়ে যায়।
ফ্যাশনে একেক সময় একেটা চল আসে। একেক যুগে, একেক সময়ে একেকটা জিনিস জরুরি হয়ে ওঠে। কখনোবা একটা ট্র্যান্ড বা হুজুগও আসে। উঁচুদরের সাহিত্যিক এইসব এড়িয়ে চলেন। একটা যুগ বা সময়ের চাহিদা মিটিয়ে সাহিত্য তৈরি করলে তার পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাও হবে সাময়িক। সমকাল আর মহাকালের ফারাকটা অনেক।
আজকের দিনে এসেও মানিকের কুবের, বিভূতির অপু-দূর্গা, তারাশঙ্করের নিতাইকে আমরা সমকালীন ভাবতে পারি। তাদের মনোজগত, তাদের সমস্যা এবং সুখ-অসুখ চিরন্তন। দস্তয়ভস্কি তাই একই সঙ্গে সমকালীন, ধ্রুপদী এবং জনপ্রিয়। কেননা, দস্তয়ভস্কি মৌলিক। তিনি এমন করে বলেছেন, লিখেছেন যা কেবল তারই একান্ত ভঙ্গিমা। এমন একান্ত ভঙ্গিমার লেখনির নজির রেখে গেছেন বনফুল থেকে সৈয়দ শামসুল হক পর্যন্ত অনেকেই। অনেকেই বলছি, কেননা, বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রটি বিশাল এবং অবশ্যই ঋদ্ধ। বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব (্বসু), মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্কর, ইলিয়াস, আল মাহমুদ-এর মতো অগণিত নক্ষত্র বাংলা কবিতা, গল্প, গান, উপন্যাস, প্রবন্ধকে বিশ্ব সাহিত্যের আকাশে প্রজ্বলিত করে গেছেন। তারা ধ্রুপদী আবার কম-বেশি জনপ্রিয়ও।
আগেই বলার চেষ্টা করেছি, ধ্রুপদী সাহিত্য এক সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্য ধ্রুপদী হয়ে উঠবে এমন নিশ্চয়তা দেয়া মুশকিল। একমাত্র সময়ই নিশ্চিত করতে পারে তা।
দুই বাংলার সাহিত্যে প্রবল জনপ্রিয়তার এক ও অনন্য নজির হুমায়ূন আহমেদ। ঈর্ষনীয় জনপ্রিয়তা তিনি পেয়েছিলেন। এমনকি, বাজার অনুসন্ধানে দেখা যায় তার মৃত্যুর এক যুগ পর বই বিক্রির দিক থেকে এগিয়ে আছেন তিনি। তার জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরপরই কেউ কেউ বলেছিলেন বা ধারণা করেছিলেন, তিনি টিকবেন না। অর্থাৎ তার জনপ্রিয়তা সাময়িক। হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা এক অর্থে বৈপ্লবিক। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বইয়ের বাজার ধরে রেখেছিলো পশ্চিম বাংলার তথা কলকাতার বই। সুনীল, শক্তি, শীর্ষেন্দু, সমরেশ (মজুমদার) প্রমুখ লেখকদের লেখা এ দেশে প্রবল জনপ্রিয় ছিলো, এক অর্থে একচেটিয়া বাজার ছিলো তাদের। ইমদাদুল হক মিলন এবং পরবর্তীকালে হুমায়ূন আহমেদ এ দেশের পাঠককে, ক্রেতাকে বইমেলা কেন্দ্রিক করেছেন, এ দেশের প্রকাশনা শিল্পকে জোরদার করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সাহিত্যের একটা নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিমা তৈরি করেছেন। হুমায়ূন তার সাহিত্যে ঢাকা জেলা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের একটা পরিমিত বাংলা চালু করেছেন, অন্যদিকে ভাটি অঞ্চলের ভাষা নিয়েও কাজ করেছেন। অন্যদিকে মিলন তার সাহিত্যে বিক্রমপুরের ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি, বাংলাদেশের বহু লৌকিক উপাদান, উপাখ্যান ব্যবহার করেছেন। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা, বিশেষ ক্রিয়াপদের ব্যবহারও কলকাতা, নদীয়া ঘেষা ছিলো। কাজেই তাদের জনপ্রিয়তা নেহাত বাজার চলতি জনপ্রিয়তা নয়, নেহাত লোক মানুষের চাহিদা মিটিয়ে বই বিক্রির জনপ্রিয়তা নয়, বরং একটা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জনপ্রিয়তার ঘরাণা মিলন আর হুমায়ূন তৈরি করেছিলেন।
মার্কিন-ইতালীয় লেখক, শিল্পী ভান্না বোনটা একটা মোক্ষম কথা বলেছেন, ‘জনপ্রিয়তা কখনোই মানের নিশ্চয়তা দেয় না।’ এ কথা আজকের দিনে এসে আমাদের বাংলাদেশে প্রায়শই দেখতে পাই। বিশেষ করে সোস্যাল মিডিয়ার কল্যাণে, ট্রল, ম্যাম ইত্যাদি নয়া ডিজিটাল সংস্কৃতির পথ ধরে, যে কেউ রাতারাতি ‘ভাইরাল’ হয়ে যাচ্ছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, হিরো আলম, অনন্ত জলিল, মাহফুজুর রহমান, কেকা ফেরদৌস, জায়েদ খান এ দেশে জনপ্রিয় ব্যক্তির নাম। কিন্তু তাদের জনপ্রিয়তা তাদের স্ব-ক্ষেত্রের কাজের মানকে নিশ্চিত করে না। এ কথা লেখালেখির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হালের অনেক জনপ্রিয় লেখকও আছেন যারা নিজেদেরকে স্যোসাল মিডিয়ার লাইক শেয়ার দিয়ে বিবেচনা করেন। অনেক প্রকাশকই আছেন, সোস্যাল মিডিয়ায় যার সহস্রাধিক বা লক্ষ অনুসারী আছে তার বই করেন। আমাদের সোস্যাল মিডিয়ার সূত্র ধরেও কোন কোন লেখকের উত্থান হয়েছে। বিশ্বব্যাপী রূপী কৌরের মতো তরুণ কবির জনপ্রিয়তা ইন্সটাগ্রামের কল্যাণেই। তবু রূপী কৌরের মতো কবিকে ইন্সটা-কবিই বলা হয়।
আদতে, সাহিত্যের দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রশ্নে ক্ষণস্থায়ী সোস্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয় কবি-লেখককে গ্রহণ করা সহজ নয়। সাহিত্য জগতে মানোত্তীর্ণ এবং কালোত্তীর্ণ শর্ত দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই শর্ত পূরণ করে যারা এগিয়ে যাবেন তারাই একদিন সাহিত্যের ধ্রুপদী আসরে ঠাঁই করে নেবেন। জনপ্রিয়তা ও মানকে চলতে হবে পাশাপাশি। মনে রাখা জরুরি, পৃথিবীতে অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক উইলিয়াম শেকসপিয়র, ভিক্টোর হুগো, গ্যাব্রিয়েল মার্কেজ, হোর্হে বোর্হেস, পাওলো কোহেলহো থেকে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং হুমায়ূন আহমেদ একই সঙ্গে জনপ্রিয় এবং উচ্চ মান সম্পন্ন সাহিত্যগুণ ধারণ করেন।
কাজেই আজকের দিনে যারা লিখতে এসেছেন, লিখে ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাদেরকে তাকাতে হবে বাংলা সাহিত্য ও বিশ্ব সাহিত্যের মৌল প্রবণতা সমূহের দিকে। তারা যদি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি তৈরি করতে পারেন তবেই জনপ্রিয়তা পেরিয়ে কালোত্তীর্ণের পথে এগুতে পারবেন। মানোত্তীর্ণ লেখার সূত্র ধরেই আমাদের ইমতিয়াজ মাহমুদ, সাদাত হোসাইনকে কালোত্তীর্ণের সীমায় পৌঁছাতে হবে। আশার কথা, তারা নিজের সাহিত্যকর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং সাধনা অব্যহত রেখেছেন।
২০২৪ সালের বেস্টসেলার লেখক ইলমা বেহরোজ তার জনপ্রিয় উপন্যাস ‘পদ্মজা’র ভূমিকাতে সরল স্বীকারোক্তি করে লিখেছেন,
‘আমি ব্যাকরণ জানি না,
আমি সাহিত্যের সব গণ্ডি চিনি না,
বুঝি না কীভাবে টিকে থাকতে হয়,’’
তার এই স্বীকারোক্তি সততার পরিচয় দেয়। তিনি সাহিত্য জগতে একেবারেই নবীন, কিন্তু শুরুতেই তার তীব্র জনপ্রিয়তা ঈর্ষনীয়। একজন সাহিত্যিকের জন্য বিপুল পাঠক পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! আশা করা যায় ‘সাহিত্যের গণ্ডি’ নয় ‘সাহিত্যে সীমানা’ জেনে-বুঝে, সেই সীমানাকে পেরিয়ে যাবে ইলমার মতো তরুণ লেখকরা, তখনই তারা কালোত্তীর্ণ হবেন, টিকে থাকবেন। মানোত্তীর্ণ লেখা এবং মানোত্তীর্ণ লেখাই টিকে থাকার একমাত্র কৌশল যদি হয়, তবে জনপ্রিয় সাহিত্যও মূল ধারার তাত্ত্বিক, সমালোচক, গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।
জনপ্রিয় সাহিত্যের সন্ধানে | মুম রহমান
RELATED ARTICLES