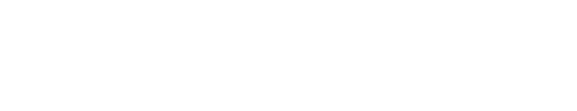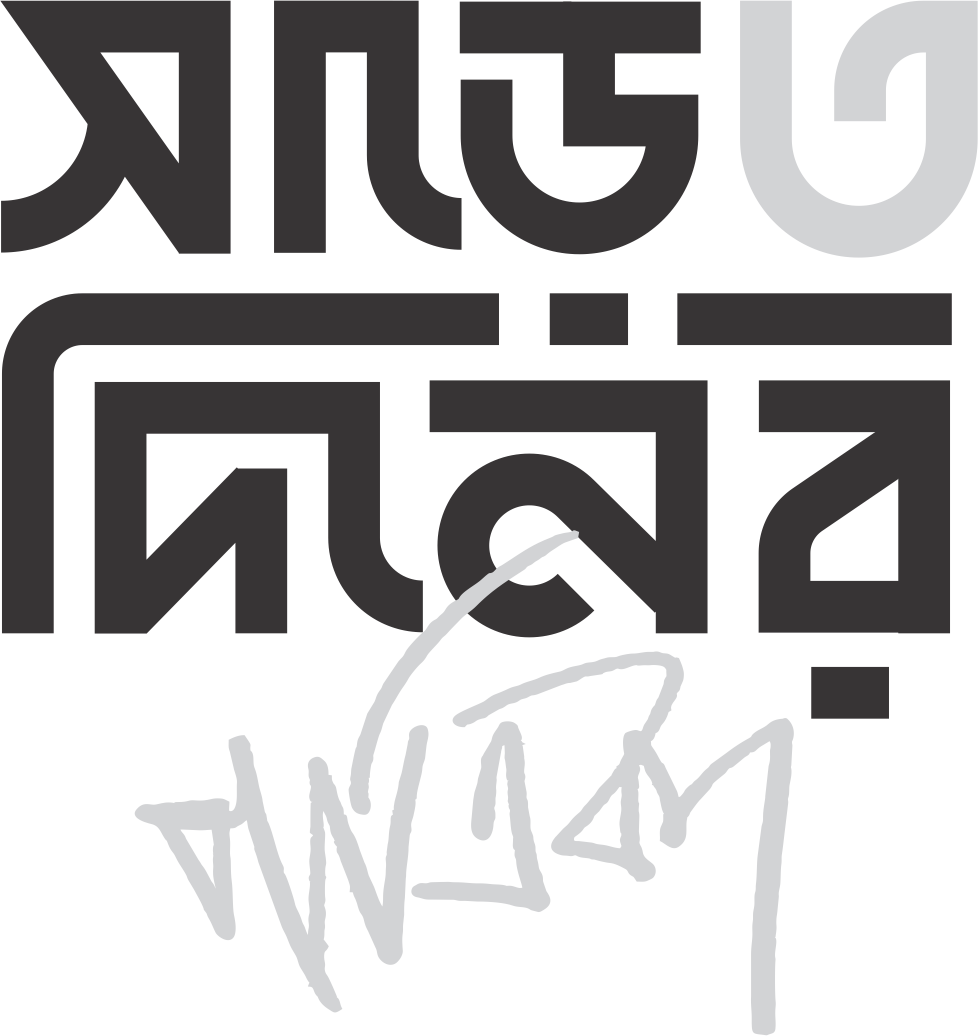অধ্যাপক রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী একজন অনুবাদক। তার জন্মশহর চট্টগ্রাম। বেড়ে উঠেছেন পুরনো পল্টনে। স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষাসাহিত্যে লন্ডন এবং স্পেন থেকে স্নাতক সম্মান ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। অধ্যাপনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে। লেখালিখির শুরু বিদ্যাপীঠ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন ও বিশ্বসাহিত্য থেকে অনুবাদ করেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থÑ গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর উপন্যাস : আমার দুঃখভারাতুর বেশ্যাদের স্মৃতিকথা; হুয়ান পাবলো বিইয়ালোবোস-এর উপন্যাস : পাতালপুরীতে মচ্ছব; গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস : কর্নেলকে কেউ লেখে না; ইতালীয় লেখক আলেসান্দ্রো বারিককো-র উপন্যাসের অনুবাদ সিল্ক, সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ আধুনিক লাতিন আমেরিকান গল্প প্রভৃতি। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ‘সাড়ে তিন দিনের পত্রিকা’র বিশেষ আয়োজন ‘অনুবাদ সংখ্যা’র জন্য গুণী এই অনুবাদকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন Ñ এহসান হায়দার
- আপনি যখন অনুবাদ চর্চা শুরু করেন তখনকার সময়টা সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ১৯৯০-১৯৯১ সাল। ইংরেজি সাহিত্য পড়বার পাশাপাশি গোগ্রাসে গিলছিলাম হুলিও কোর্তাসার, মারিও বার্গাস ইয়োসা, জর্জ আমাদু এবং গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের এক একটা উপন্যাস। নিতান্ত মনের আনন্দে তর্জমা শুরু করেছিলাম ছোট দৈর্ঘ্যরে কিছু টেক্সট্ দিয়ে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তখন (আজও, অনেকটুকুই) দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দেশে সুনামের সাথে কাজ করছেন হায়াৎ মামুদ, আলী আহমদ, আলম খোরশেদ, জি এইচ হাবীব প্রমুখ। বলে রাখা দরকার যে তর্জমা বলতে আমাদের এই আলাপটা সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে।
তখন যত তর্জমার কাজ হত তার সিংহভাগই ক্লাসিকস্ কিংবা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত কবি ও লেখকদের রচনার তর্জমা। সেবা প্রকাশনী তো আরও অনেক আগে থেকেই তার মতো করে একটা ভূমিকা রেখে চলছিল। পাশাপাশি অল্প কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা শুধু তর্জমানির্ভর বই দিয়েই বাজারে হাজির ছিল, যেমন ‘সন্দেশ’। আমরা কয়েকজন বিভিন্ন বয়সি বন্ধু নীলক্ষেতের পুরনো বইয়ের ঝাঁপিতে ঘুরেফিরে নিজেদেরকে সঁপে দিতাম। গরম গরম পুরির সাথে চা, নির্ভেজাল আড্ডা এবং বিদেশি বইয়ের সুলুক সন্ধান। কোন্ দিন কে দুর্লভ কোন্ তর্জমার বইটা শেষ পর্যন্ত বাগে এনে কিনতে পারল তা নিয়ে চলত এক ধরনের প্রতিযোগিতা। কে কোথায় কোন্ গুরুত্বপূর্ণ কবিতা বা গল্প-উপন্যাসের বই দেখেছে এবং এ যাবত কার সংগ্রহে কী কী আছে সেসব কথা উঠে আসত আড্ডায়। মধুর সেসব দিন।
- আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ অনুবাদ করছেন, কেমন মনে হয় এখন অনুবাদ সাহিত্য জগত?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : আগে আমরা ছাপার বই কিনে বা যোগাড় করে তর্জমার কাজটা চালাতাম। এখন তো ই-বুক ডাউনলোড করে কিংবা ওয়েব থেকে সংগ্রহ করে কাজ করা সহজ হয়েছে; মানে বইপত্র হাতের কাছে, চোখের সামনে হাজির করাটা সহজতর হয়েছে; কিন্তু তার ফলে অনুবাদ সাহিত্যের মানগত কী পরিবর্তন হয়েছে তা বলা মুশকিল। ডাটা ছাড়া কথা বলাটা ঠিক হবে না। এটা গবেষণার বিষয়। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় অনুবাদকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে কিন্তু মানসম্পন্ন সাহিত্যের তর্জমা কতটুকু কী হচ্ছে তা নিরিখের দাবি রাখে।
আপনার প্রশ্নের উত্তরেÑ অনুবাদ সাহিত্যজগত বলতে, আমি শুধু বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি। বিষয় হিসেবে অনুবাদের কদর কমবেশি সব সময়ই ছিল আমাদের দেশে। বর্তমানে সেটা আরও বেড়েছে। বহু সংখ্যক প্রকাশক তর্জমার বই ছাপেন, দেদারসে বিক্রিও হয়। ফি-বছর একুশের বইমেলায় হারুকি মুরাকামি, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, পাওলু কোয়েলিয়ো প্রভৃতি ভুবনজোড়া খ্যাতিমান লেখকের উপন্যাসের তর্জমার পাশাপাশি চলতি বছরে নোবেলজয়ীর বইয়ের তর্জমা এবং বেস্টসেলার থ্রিলার-সায়েন্স ফিকশন বইয়ের তর্জমা প্রকাশ করে ছোট-বড় অনেক প্রকাশনা সংস্থা। ফিকশনের বাইরে নন-ফিকশন এবং চিন্তামূলক বইয়ের তর্জমার চর্চা হচ্ছে আজকাল। আর ইসলামি চিন্তা-চেতনাভিত্তিক বইয়ের তর্জমা একটা চালু ব্যাপার, সেগুলোর বিক্রি-বাট্টা ঈর্ষণীয়রকম। জনাকয়েক ধীমান তরুণও তর্জমায় হাত মকশো করছেন এবং প্রকাশনার সাথে নিজেদেরকে জড়াচ্ছেন। এটা আশাব্যঞ্জক। ইদানিং অনুবাদ পত্রিকাও বের হচ্ছে দু-তিনটি। মধ্যযুগে তর্জমা সাহিত্য শাহ মুহম্মদ সগীর, আলাওলের হাতে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। আজ অবধি আমাদের তর্জমা সাহিত্যের যা কিছু অর্জন তা প্রধানত কয়েকজন সৃষ্টিশীল মানুষের পাগলামির ফসল। তারা এক একজন দোন কিহোতে। আশা করি সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমাদের তর্জমা সাহিত্য নিশ্চয়ই তার আকাঙ্খিত পথ খুঁজে পাবে।
- একটা বিদেশি ভাষায় লেখা কোনো রচনা যখন বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়, তখন একজন অনুবাদক সেই অনুবাদটিকে ঠিক কোন দিকগুলোকে ভাবনায় রেখে অনুবাদ করেনÑআপনি বিষয়গুলিকে কীভাবে দেখেন?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : তর্জমা একটি জটিল প্রক্রিয়া, যার মধ্যে থেকে একজন অনুবাদককে সময়ে সময়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিচিত্র হেতু আমলে নিয়ে তাকে ওই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয়। অনেক ভাবনা উঁকি দেয় Ñ কিন্তু কোনটি যুতসই হবে তা নির্ধারণ করে দেয় টেক্সটের ধরন, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ, অভিপ্রায় ইত্যাদি বর্গ। আবার প্রতিষ্ঠান এবং যারা ছাপাচ্ছে সেই প্রকাশনা সংস্থার একটা ভূমিকাও থাকতে পারে।
ভিন্ন ভাষা থেকে তর্জমা যেটিকে ভাষাতাত্ত্বিক রোমান ইয়াকবসন নাম দিয়েছিলেন translation proper. আমার আরাধ্য একটি বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে তর্জমা করতে গিয়ে আমার ভাবনায় যে দুটি বিষয় তার সমগ্রতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল : টেক্সট্ এবং প্যারাটেক্সট্। মূল টেক্সট্কে বুঝতে প্যারাটেক্সটের পাঠ জরুরি। কে যেন বলেছিলেন যে, অনুবাদক হলেন টেক্সটের একজন গভীরতম পাঠক। আমি মনে করি একজন অনুবাদককে পাঠকের সেরা পাঠক হতে হয়। ভিন্ন ভাষা থেকে যে টেক্সটটি তর্জমা করা হচ্ছে সেই কাজটি করতে গিয়ে অনুবাদককে মূল ভাষায় দক্ষ তো হতে হবেই, তার চেয়েও বেশি দক্ষতা দরকার লক্ষ্য ভাষায়, মানে যে ভাষায় তিনি তর্জমা করছেন। আর শুধু কি ভাষা জানলে হবে? না। তিনি তো cultural mediator। সুতরাং সংস্কৃতির পাঠটাও জরুরি। তার সাথে আমলে আনতে হয় ইতিহাস, সমাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, ডিসকোর্স ইত্যাদি অপরিহার্য বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি পড়তে পড়তে তর্জমা করি। আর মূল লেখকের অভিপ্রায়, সুর-স্বর, লেখনশৈলীকে গুরুত্ব দিয়ে আপস রফা করতে করতে (কূল রাখি না শ্যাম রাখি) এগোই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। একই লেখকের সব টেক্সটের সুর-স্বর কিন্তু এক রকম না, এটা আমি মেনে চলবার চেষ্টা করি। আর লেখকে-লেখকে তো তফাত আছেই।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো বই দ্বিতীয় একটি ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জাপানিজ ভাষায় রচিত কোনো একটি গ্রন্থ সরাসরি জাপানিজ ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় না, কারণ অনুবাদক জাপানিজ ভাষা জানেন নাÑ সেই কারণে ইংরেজি ভাষা থেকে (আরেকটা অনুবাদকৃত গ্রন্থ) অনুবাদ করছেÑ এইক্ষেত্রে শিল্পমান এবং ভাবের যে বিষয় সেটি কতটা পরিবর্তন হয় বা ঠিক থাকে বলে মনে করেন?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : মূল টেক্সটের ভাষা থেকে সরাসরি তর্জমায় (direct translation) পরিবর্তন বা shift হওয়াটা স্বাভাবিক। আর যদি তা তিন হাত ঘুরে হওয়া তর্জমা (অনুবাদের অনুবাদ) হয় তা হলে তো shift হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। দেখার বিষয় ওই শিফ্টের কারণে মূল টেক্সটের বৈভব, শৈলী, ব্যঞ্জনা, রেজিস্টার ও ভাব লক্ষ্য টেক্সটে (Direct বা Indirect যেভাবেই তর্জমা হোক না কেন) কতটুকু কীভাবে হাজির হচ্ছে। মূল আরবির মাহমুদ দারবিশ ও তাঁর কবিতা আমরা সরাসরি বাংলায় কী কতটুকু পাচ্ছি আর তিন হাত ঘুরে হওয়া তর্জমার মধ্য দিয়ে বাংলায় কতটুকু কী পাচ্ছিÑএই দুইয়ের মধ্যে একটি পদ্ধতিগত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা হয়তো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। এটা কেবল একটা উদাহরণ। এরকম অসংখ্য নিরীক্ষা হতে পারে।
তবে একটি কথা বলা দরকার, সরাসরি তর্জমা হলেই যে অনুবাদ ভালো হবে আর তিন হাত ঘুরে করলে মন্দ হবেÑএরকম হলপ্ করে বলা যায় না। উল্টোটাও হতে পারে। তর্জমার গুণাগুণ নির্ভর করে অনুবাদকের মুন্সিয়ানার ওপর। প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই তর্জমা মানেই শুধু মূলকে হারানো নয়, ওটাকে নতুন করে পাওয়াও তো বটে। উৎস টেক্সটের চিহ্নদের সমস্ত রকম সম্ভাবনাগুলিকে এক জবান থেকে আর এক জবানে অন্যভাবে মুক্তি দেয়ার নামই তর্জমা।
- আপনার অনুবাদকৃত গ্রন্থ ‘আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা’ পাঠকপ্রিয় এই বইটি। এই অনুবাদ গ্রন্থটিকে অনুবাদের সময় কেমনভাবে চিন্তা করেছিলেন- বইটির কোন্ কোন্ দিককে মাথায় রেখে কাজটা শুরু করেন?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : স্প্যানিশে একটি শব্দ আছে ঢ়ধংরষ্টহ, মানে প্যাশন। গার্সিয়া মার্কেসের ওই উপন্যাসটি তর্জমা করার পেছনে দারুণভাবে সহায়তা করেছিল ছাত্রজীবনের প্যাশন। আমি কাজটা শুরু করেছিলাম মাদ্রিদে, যখন স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক হিসেবে বৃত্তি নিয়ে কোমপ্লুতেনসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলাম। রবিবাসরীয় খোলা মার্কেট থেকে মাত্র ৫ ইউরো দিয়ে বইটি কিনেছিলাম। এরপর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তে পড়তে একদিন তর্জমা করা শুরু করলাম নেহায়েত মনের আনন্দে। গার্সিয়া মার্কেসকে আমার বাংলায় কতটুকু ধরা যায় সেই বাসনাই আমাকে কাজটার ভেতরে নিয়ে গেছে। এর আগে বছর কয়েক ধরে গার্সিয়া মার্কেসকে নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলাম।
- বাংলাভাষায় বিদেশি ভাষার যত বই অনুবাদ করা হয়েছেÑ এর বিপরীতে বাংলা ভাষার বই ভিনদেশি ভাষায় কী পরিমান অনুবাদ হয়েছে?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : খুব একটা না। গত দশ বছরে বেশ কিছু কাজ হয়েছেÑরাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। আর যা-ও হয়েছে, মানে ঃৎধহংষধঃরড়হ ড়ঁঃ-এর কাজ, তা মূলত বাংলা থেকে ইংরেজিতে। বিদেশি ভাষার ওপর সে পর্যায়ে দখল রাখেÑএরকম লোকের সংখ্যা হাতেগোনা।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে বিদেশি ভাষায় বাংলাভাষার ক্লাসিক রচনাগুলি অনুবাদের উদ্যোগ নেন কেমন, এ বিষয়ে আপনার ভাবনা কি?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগুনো দরকার। বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, নজরুল ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিত অনুবাদ-প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।
- অনুবাদসাহিত্যকে দেখেছি অনেক সময় খাটো করা হয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়Ñ বিষয়টিকে কীভাবে ভাবেন?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : বিখ্যাত তর্জমাতাত্ত্বিক লরেন্স ভেনুতি ‘দ্য ট্রান্সলেটরস্ ইনভিজিবিলিটি’ নামে একটি বই লিখেছেন। খোঁজ-খবর করলে দেখবেন বছর বিশেক আগেও তর্জমা বইয়ের প্রচ্ছদে অনুবাদকের নাম থাকত না। সে অবস্থা অনেকটুকু বদলেছে। তর্জমাকারীরা এখন অনেক বেশি দৃশ্যমান। তর্জমা ছাড়া দুনিয়া তো অচল। সুতরাং তর্জমা বিষয়টিকে যত বেশি গুরুত্ব দেয়া যাবে ততই মঙ্গল। আমরা যে তলস্তয়, সের্ভান্তেস, কাফকা, মালার্মে, বোর্হেসকে পড়ে জেনেছি সে তো তর্জমাকারীদের কল্যাণে। তাদের কথা কে-ই বা রাখে মনে!
- অনুবাদসাহিত্য বিষয়ে আপনার নিজস্ব ভাবনা জানাবেন কী?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : অপ্রধান ভাষাগুলো (যেমন বাংলা) অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ত্রিভুবনজুড়ে আরও পরিচিত ও দৃশ্যমান হয়ে উঠবেÑএটাই আমার আশা। আমাদের ঐতিহ্যবান অনুবাদসাহিত্য একাডেমিয়াতে আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে জায়গা করে নিক।
- নতুন যারা অনুবাদসাহিত্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী : পড়তে থাকুন জগতের নানা বিদ্যার বই। হয়ে উঠুন একজন প্রাগ্রসর সেরা পাঠক। চর্চা করতে করতেই শিখে নেবেন এর কলাকৌশল। মনে রাখবেন আপনি এক অসম্ভবকে খুজে বেড়াচ্ছেন যা কখনোই ধরা দেবে না।