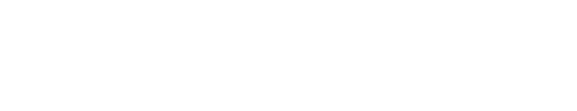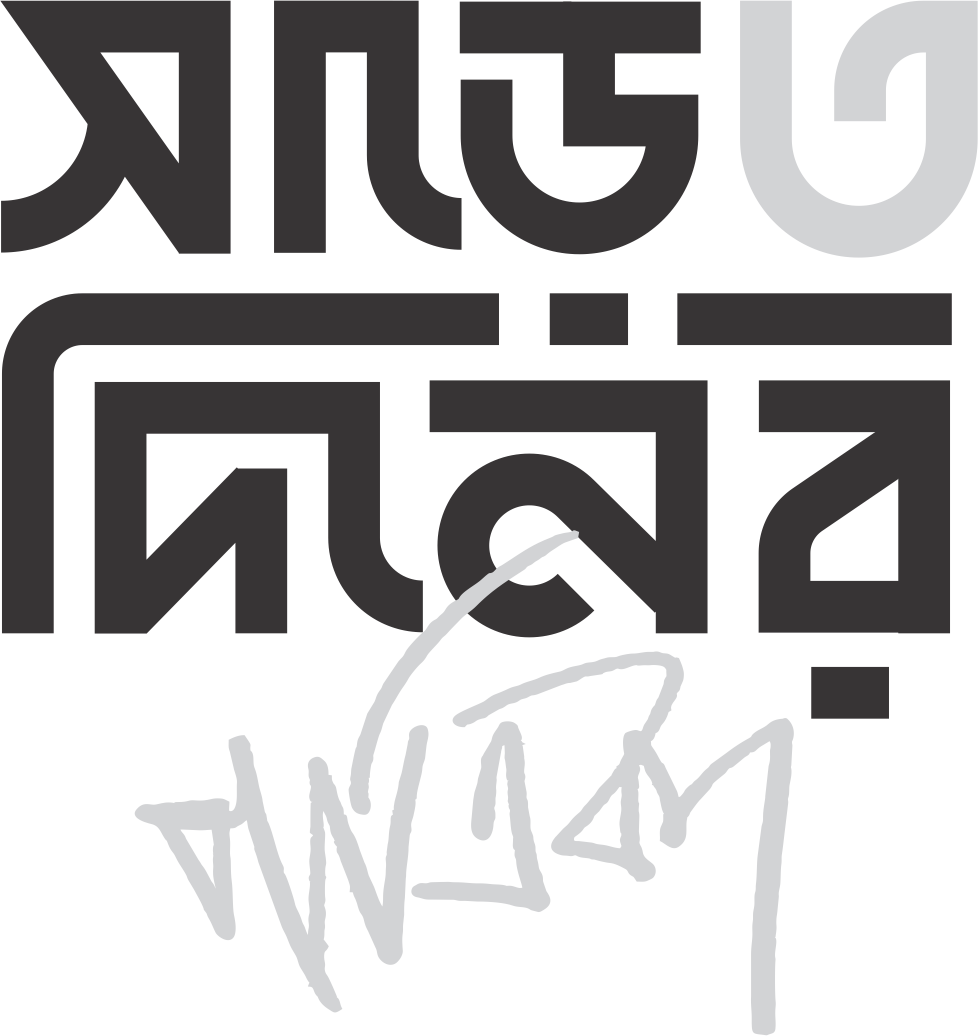সাদাত হোসাইন এই সময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। সাদাত গল্পের মানুষ। তার কাছে চারপাশের জীবন ও জগত, মন ও মানুষ সকলই গল্প। তিনি মনে করেন, সিনেমা থেকে পেইন্টিং, আলোকচিত্র থেকে ভাস্কর্য, গান থেকে কবিতা- উপন্যাস-নাটক, সৃজনশীল এই প্রতিটি মাধ্যমই মূলত গল্প বলে। গল্প বলার সেই আগ্রহ থেকেই একের পর এক লিখেছেন- আরশিনগর, অন্দরমহল, মানবজনম, নিঃসঙ্গ ন¶ত্র, নির্বাসন, ছদ্মবেশ, মেঘেদের দিন, অর্ধবৃত্ত, শঙ্খচূড়ের মতো তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস। ‘কাজল চোখের মেয়ে’, তোমাকে দেখার অসুখ’সহ দারুণ সব পাঠকপ্রিয় কবিতার বই। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বোধ, দ্য শুজ, প্রযত্নের পাশাপাশি নির্মাণ করেছেন গহীনের গান-এর মতো ব্যতিক্রমধর্মী পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও। সাড়ে তিন দিনের পত্রিকা’র অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বিশেষ আয়োজন ‘জনপ্রিয় সাহিত্য’ সংখ্যার জন্য তরুণ এই লেখকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এহসান হায়দার
- আপনার সাহিত্যচর্চার শুরুর সময়টা কেমন ছিল বিস্তারিতভাবে বলবেন…
সাদাত হোসাইন : আমার জন্ম মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার কয়ারিয়া গ্রামে। ওই সময়টাতে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই ছিলো মূলত কৃষিজীবি। গ্রামে তখন বিদ্যুৎ, রেডিও, টেলিভিশন কিছুই ছিল না। শিক্ষার হারও ছিলো খুবই কম। আর পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই পড়ার ব্যাপারটাতো ছিলো রীতিমতো অকল্পনীয়। আমার বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী কারোই সেই অর্থে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়ার চর্চা ছিল না। আমার মা ক্লাস টেন অবধি পড়েছিলেন। নানা খুব বই পড়তে পছন্দ করতেন। সম্ভবত সে কারণেই আম্মাও খুব বই পড়তেন। আর ওই পরম্পরা থেকেই কিনা জানি না, চারপাশের ওরকম বিরূপ পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও পাঠ্য বইয়ের বাইরে গল্পের বই পড়ার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ তৈরি হয় আমার। শুধু পড়তেই না, গল্প শুনতেও ভীষণ ভালো লাগতো। মা, নানি, দাদির কাছে গল্প শোনার বায়না ধরতাম খুব। রীতিমত নেশা হয়ে গেল। রাতেরবেলা গল্প শুনবো বলে কাউকে ঘুমাতে দিতাম না। বাজারে গেলে দুই তিনদিনের পুরনো পত্রিকাগুলো ঘেটে দেখতাম, পাঠ্য বইয়ের বাংলা গল্পগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে শেষ করতাম।
আব্বা তখন ঢাকায় খুব স্বল্প বেতনে ছোট্ট একটা চাকুরি করেন। আব্বার কাছে প্রায়ই বই কেনার বায়না ধরতাম। তিন চারমাস পর যখন তিনি বাড়ি আসতেন, তখন অফিসে জমে থাকা পুরনো সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো আমার জন্য নিয়ে আসতেন। যেহেতু গল্পের বই বা পত্রিকা খুব একটা সহজলভ্য ছিলো না গ্রামে, ফলে ওরকম নানান উপায়েই গল্প পড়ার ক্ষিদে মেটানোর চেষ্টা করতাম আমি। আর সেই থেকেই হয়তো গল্প বলার প্রতিও একটা আগ্রহ তৈরি হয়। আব্বা যখন লুঙ্গি বা মায়ের জন্য শাড়ি কিনে আনতেন, তখন সেসব কাপড়ের ভেতরে পুরনো দিনের পত্রিকা থাকতো। নানা ধরনের গল্প থাকতো তাতে। আমি সেগুলো জমিয়ে রেখে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। তখন ইত্তেফাক পত্রিকায় শিশু কিশোরদের নিয়ে একটা পাতা ছিল কঁচি কাঁচার আসর নামে। একদিন আচমকা দেখলাম সাদাত হোসাইন নামে ক্লাস ফোরে পড়া একটা ছেলের লেখা ছাপা হয়েছে তাতে। দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। নিজের নাম প্রথম ছাপার অক্ষরে দেখলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মন খারাপও হয়ে গেল। কারণ- একই নাম হলেও ওই ছেলেটা তো আমি না। অথচ সেও আমার মতো ক্লাস ফোরেই পড়ে তখন। ওই ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত শিহরণ তৈরি করেছিলো আমার মধ্যে।
শীতের সকালে আম্মা উঠানে পড়তে বসাতেন। তখন বইয়ের মলাট যাতে সহজে ছিড়ে যেতে না পারে, সেজন্য পুরাতন ক্যালেন্ডারের পাতা দিয়ে একটা ্এক্সট্রা মলাট লাগানো হতো বইয়ের ওপর। সেই ক্যালেন্ডারের পাতায় হঠাৎই চোখে পড়লো জীবনানন্দ দাশের কবিতার দুটো লাইন। আমি হঠাৎ আম্মাকে বললাম, আমিও কিন্তু এমন কবিতা লিখতে পারি। বলেই আমি আকাশের দিকে তাকালাম। একটা চিল উড়ে যাচ্ছিলো নীল আকাশে। আমি সেদিকে তাকিয়ে আম্মাকে বললাম, “আকাশ অনেক নীল, উড়ছে দেখো চিল।” আম্মা বেতের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করে বললেন, ‘সারাদিন শুধু দুষ্টুমি। পড়তে বসছিস, পড়।’ কিন্তু আমার মনে হলে লাইন দুটো খাতায় লিখে রাখা উচিৎ। পরে যদি ভুলে যাই! কিন্তু লিখতে গিয়ে আবার মনে হলো, আমি ওই লাইন খাতায় লিখতে চাই না। নিজের লেখা ছাপার অ¶রে দেখতে চাই। আসলে ওই ছেলেটির ছাপানো নাম আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিলো। কিন্তু আমার নাম কীভাবে ছাপার অক্ষরে দেখব? আমি জানি না পত্রিকায় কীভাবে লেখা পাঠাতে হয়। তাছাড়া, ওই গ্রামে সেরকম ভাবনার কোনো মানুষও ছিলো না যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু রাতে ঘুমাতে গিয়ে অদ্ভুত এক বিষয় মাথায় খেলে গেল আমার। একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার সংগ্রহে যত পত্রিকা ছিল, সেগুলো বের করলাম। তারপর সেখানে থাকা বিভিন্ন সংবাদ থেকে আমার কবিতার জন্য প্রয়োজনীয় অ¶রগুলো কেটে একটার পর একটা সাজিয়ে নিলাম পাশাপাশি। তারপর ভাতের আঁঠা দিয়ে সেগুলো একটি কাগজে লাগালাম। তারপর তাকিয়ে দেখলাম, ওই পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া অক্ষরগুলোই যেন আমার কবিতাটিকে ছাপার অক্ষরে লেখা কবিতার আদল দিলো। এবং সেই প্রথম আমি আমার নামও ছাপার অ¶রে দেখলাম। খুব উত্তেজনা নিয়ে আম্মাকে দেখালাম। এবং আম্মা যথারীতি বকা দিলেন, ‘সারাদিন শুধু দুষ্টুমি। দুষ্টুমি ছাড়া কোনো কাজ ন্ইে না?’
কিন্তু পাশের বাড়ির এক বড় ভাই আমার এই অভিনব কাজ দেখে ভীষণ বিস্মিত হলেন। বললেন- তুমি নিজেই জানো না তুমি কী অসাধারণ এক কাজ করেছো! নিজের অসম্ভব স্বপ্নকে নিজের অদম্য ইচ্ছে শক্তি দিয়ে পূরণ করেছো। তুমি যদি কখনো বড় লেখক হও, তবে তখন তোমার এই ঘটনাটি অনেক মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হবে। মানুষের জীবনে অনেক স্বপ্নে থাকে; কিন্তু নানা বাধার কারণে তারা সেই স্বপ্নটার পেছনে ছুটতে পারে না। খুব কম মানুষ আছে যারা সেই বাধা অতিক্রম করে, ভিন্ন পথ আবিষ্কার করে এমন কিছু করে যার মাধ্যমে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়।
তুমি সেরকম একটা কাজ করেছ। তখন তিনি আমাকে একটা লাল কালির কলম উপহার দিলেন। এই কলমটা আমার জীবনের প্রথম পুরষ্কার। ওই ঘটনা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করলো। লাল রঙ দিয়ে লেখার লোভে বইয়ের সাদাকালো যে ছবিগুলো থাকতো সেগুলোকে লাল রঙ করে দিতাম। বইয়ে একটা কবিতা, গল্প পড়ে সে কবিতা বা গল্পের মতো করে আমি নিজে একটা লেখার চেষ্টা করতাম। এই লাল কলম দিয়ে লেখার লোভে, গল্প অর্ধেকটা পড়ে চিন্তা করতাম, বাকি কাহিনীটা কেমন বা কীভাবে শেষ হতে পারে। বইয়ের পাতার ফাঁকা জায়গায় কল্পনা করে লেখা শুরু করলাম। তো এভাবেই লেখার শুরু। যত বড় হচ্ছিলাম, ততই বাড়ছিলো লেখার সংখ্যা। কিন্তু সেগুলো নিয়ে কখনো কোনো স্বপ্ন কিংবা আত্মবিশ্বাস ছিলো না। মনে হতো, এসব সত্যিই কিছু হয় কিনা কে জানে! কারণ, ওখানেতো লেখা নিয়ে সত্যিকারের মতামত দেওয়ার মতো কেউ ছিলো না। ফলে মনে মনে অপে¶া করছিলাম, কোনোদিন হয়তো কারো সঙ্গে দেখা হবে, যে আমার ওই লেখাগুলো সম্পর্কে সঠিক মতামত দিতে পারবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর আমি এমন একটা দলের সাথে যুক্ত হই, যারা সাহিত্য চর্চা করে, বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করে। একদিন খুব আগ্রহ নিয়ে তাদের ওই লেখাগুলো দেখাই। কিন্তু তারা একভাবে বেশ হাসিঠ্ট্টাাই করেছিলো সেদিন, যে ওগুলো কিছু হয়নি। এরপর থেকে আমি লেখালেখি পুরোপুরি বন্ধ করে দেই। ওসব করে আর কখনো সময় নষ্ট করবো না বলেও মনস্থির করি। এবং সেই ঘটনার পর দীর্ঘ সাত-আট বছর আমি আর লেখালিখি করিনি। সে সময়ে আমার বাবা অসুস্থ হয়ে প্যারালাইজড হয়ে যান। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস, বড় ছেলে হিসেবে আমাকে পড়ালেখা বাদ দিয়ে সকল দায়িত্ব নিতে হবে, নয়তো পরিবার বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পড়ালেখা করতে হবে। যেকোনো একটি করতে হবে, এমন কঠিন অবস্থার তৈরি হয়। শুরু হয় ভয়াবহ জীবন যুদ্ধ। পার্ট টাইম নানা কাজ করে একইসঙ্গে আমার পড়ালেখা এবং পরিবার দুটোই চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। স¶মও হই। মাস্টার্স পরী¶ার সময়ে আমাদের র্যাগ প্রোগ্রামে আমি একটা ছবি তুলি এবং সেটা অনলাইন সাইটে কন্সেপচুয়াল ফটোগ্রাফিতে সাবমিট করি। ‘কম্ব্যাট লাইফ ভারসেস টাইম’ ফটোটা পাঠক ভোটে সেরা নির্বাচিত হয়, এই ঘটনাটি আমার ভেতরে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। লেখালিখি যেহেতু আমার দ্বারা হয়নি, তাহলে ছবি তোলার মাধ্যমে তো গল্প বলা সম্ভব। এরপর আমি ছবির মাধ্যমে গল্প বলার চেষ্টায় অধিক আগ্রহী হলাম; কিন্তু আমার কোনো ক্যামেরা ছিল না, ধারকরা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা শুরু করলাম, মানুষের কাছে ছবিগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করলো। একটা সময় পরে আমি জাতীয় পত্রিকায় ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করা শুরু করলাম। ছবিগুলোর সাথে ক্যাপশন দেয়া খুব জরুরী বিষয় ছিল। লেখালেখির প্রতি আগ্রহ থাকার কারণে খুব ভালো ক্যাপশন দিতে পারতাম। সেই সুবাদে আমার আবার লেখালেখির চর্চা শুরু হলো। দেশের বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাতকারের সময় তাদের পোর্ট্টেট তোলার সুযোগ আমার হয়েছে। দ্বিজেন শর্মা, আব্দুশ শাকুর, আনোয়ার হোসেন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর থেকে শুরু করে অনেক কিংবনদন্তীদের ছবি তখন আমি তুলেছি। সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকারের অনুলিখন। তো পত্রিকার ফটো সম্পাদক পিউ ভাই একদিন বললেন, তোমার লেখার হাত তো ভালো, তাহলে তুমি লিখছ না কেন? উনি আমার খুব প্রশংসা করলেন। এবং প্রতি সপ্তাহে আমার তোলা ছবি নিয়ে গল্পছবি নামে একটি করে ফটোস্টোরি করার সুযোগ করে দিলেন। পওে ওই ফটো স্টোরি নিয়েই প্রথম বই প্রকাশিত হয়, যার নাম গল্প ছবি। প্রতিটি ছবির পেছনের গল্পটা লেখা, কিন্তু তা প্রতিবেদনের মতো করে নয়, ১৫-২০ লাইনের একটি গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ পেত। সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ছবির গল্পগুলো প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করে, বহু মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আর তখন অনেকবছর বাদে আবার আমার লেখালেখির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। মনে হয়, আমার মধ্যেও গল্প বলার একটা সত্ত্বা আছে, যা এতদিন ঘুমন্ত ছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, বা আশেপাশের মানুষ সেটা আমাকে বুঝতে দেয়নি। তখন প্রথম গল্পের বই প্রকাশ পায় জানালার ওপাশে। আর তারপর আসে আমার উপন্যাস ‘আরশিনগর।’ যা মূলত আমার লেখক জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ওই উপন্যাসটি পাঠক মহলে দারুণ প্রশংসিত হয়। ছড়িয়ে পড়তে থাকে মানুষের মুখে মুখে। এমনকি প্রকাশের প্রায় এক দশক পেরিয়ে গেলেও বইটির প্রতি পাঠকের আগ্রহ কমেনি। বরং এখনও প্রচুর পাঠক আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করছেন আরশিনগর।
- সাহিত্যে সবকালে জনপ্রিয় ধারার চর্চা ছিল, সিরিয়াস ধারারও। এখন এই জনপ্রিয় ও সিরিয়াস ধারার সাহিত্যকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
সাদাত হোসাইন : গ্রাম থেকে শহরে আসার পরে প্রথমদিকে আমি আমার চারপাশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত মানুষদের ভাবনা দ্বারা খুব প্রভাবিত হতে থাকি। কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় যত বাড়তে থাকে, তত মনে হতে থাকে তাদের প্রতিষ্ঠিত বহু ভাবনার সঙ্গেই আমার ভাবনার বিস্তর ফারাক রয়েছে। আমার চিন্তাগুলো ছিলো তাদের চিন্তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু একটা সময় অবধি সম্ভবত আত্মবিশ্বাসের অভাবে আমি আমার ভাবনাগুলো কারো সঙ্গে শেয়ার করতাম না। কিন্তু সময় যত যেতে থাকে, ততই আমি সম্ভবত আত্মবিশ্বাসী হতে থাকি। ফলে এখন মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ওই সব ভাবনার তুলনায় আমার ভাবনাগুলো সম্ভবত অনেক বেশি যৌক্তিক এবং বাস্তবিক। এই যে জনপ্রিয় ধারা এবং সিরিয়াস সাহিত্য নিয়ে যে ডিবেট বা বিভাজনটা আমাদের দেশে চলে, এটাও তেমন একটি। আমার কাছে মনে হয়, আমাদের দেশে শিল্প সাহিত্যের এই ধরনের বহু সংজ্ঞায়নই আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং ইউরোপ বা পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আহরিত। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের বাস্তবতা বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। এমনকি যেসকল পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ভাবনা ইউরোপেও সময়ের পরিক্রমায় বদলে গেছে, সেসকল ভাবনাও আমরা এখনও ঠিক সেই আগের মতোই, আগের প্যাটার্নেই আঁকড়ে ধরে বসে আছি। এখানে আমাদের বোঝাপড়ার বড় ফাঁক রয়েছে। অ্যান্থ্্েরাপলোজির ভাষায় একটা টার্ম আছে- সাংস্কৃতিক আপে¶িকতাবাদ। যাতে বলা হয় যে একটি সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে তাকে অন্য আরেকটি সংস্কৃতির সাপে¶ে বোঝা যাবে না। আরেক সংস্কৃতির ছাঁচে ফেলে তাকে আপনি মাপতে পারবেন না। আপনাকে বরং ও্ই সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির বাস্তবতায়, তার নর্মস, ভ্যালুস, বিলিভস, ইনস্টিট্উিশন- এমন নানান উপদানের সাপেক্ষে বুঝতে হবে। যদি আপনি তা না পারেন, তাহলে মূলত ওই সংস্কৃতিকে আপনি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবেন। বা জেনারেলাইজড করবেন। আর জেনারেলাইজেশন খুব সমস্যাজনক। এখন ইউরোপীয় সংস্কৃতি দিয়ে বা তার রিয়েলিটির ভিত্তিতে বা কনসেপচুয়াল প্যারামিটারে যদি আমাদের দেশের বাস্তবতাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটি কখনো এখানকার সত্যিকারের রিয়েলিটিকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। একটু স্থুল শোনালেও একটা উদহারণ দিতে চাই। ধরুন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি আঠারো থেকে বিশ কোটি হয়, তাহলে সেই জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১-২ ভাগ মানুষও যদি বই কেনে, তাহলে এই দেশের বইমেলায় অন্তত লাখ লাখ কপি বই বিক্রি হওয়ার কথা। কিন্তু আসলেই কি তা হয়? আমি জানি না। তবে সন্দেহ করি যে হয় না। তাহলে যেই দেশে শতকরা এক-দুইভাগ মানুষও বই কেনে না বা পড়ে না, সেই দেশে সিরিয়াস সাহিত্য-জনপ্রিয় সাহিত্যের ডিবেটের চেয়েও বেশি জরুরী পাঠভ্যাস তৈরিতে মনোযোগী হওয়া। পাঠক তৈরি করা। প্রথমে পাঠক তৈরি করতে হবে। তারপর অন্য বিতর্ক। ইউরোপ ওই বিতর্ক করতে পারে কারণ, তাদের দেশে প্রচুর মানুষ বই পড়ে। বিচিত্র ধরনের বিষয়ের, রুচির পাঠক আছে। আমার মনে হয়, আমাদের বাস্তবতায় এই সিরিয়াস সাহিত্য-জনপ্রিয় সাহিত্য আলোচনাটাই অদরকারি। ধরুন, জনপ্রিয় সাহিত্য না হয় বুঝলাম, যা বেশি মানুষ পড়ে। কিন্তু সিরিয়াস সাহিত্যের সংজ্ঞা আসলে কি? এটির সংজ্ঞা যদি আপনি আমাকে স্পষ্ট করতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে সেই সংজ্ঞার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট উত্তর দেব। গতবছর কলকাতায় এপিজে সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে সহবক্তা ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র। যিনি ও হেনরী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। বর্ষিয়ান মানুষ। কিন্তু সেখানেও এই সিরিয়াস সাহিত্য ও জনপ্রিয় সাহিত্য নিয়ে কথা উঠেছিলো। সেখানে ওনার ভাবনার সাপেক্ষে আমি আমার উত্তর দিয়েছিলাম। দারুণ জমজমাট আড্ডা হয়েছিলো। এখন ধরুন, আপনি যদি বলেন যে সিরিয়াস সাহিত্য হচ্ছে ধ্রুপদী, মানে ক্ল্যাসিক, যা কালজয়ী, যা মানুষের মনস্তত্ত্বে, সমাজ এবং রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। আবার বলা হচ্ছে সিরিয়াস সাহিত্য জনপ্রিয় সাহিত্য নয়। বা হতে পারবে না। মানে কি যে অল্প সংখ্যক পাঠকের পড়াটাও সিরিয়াস সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য? বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। ধরুন প্রচলিত ভাবনায় যদি আমি বুঝি যে এই বৈশিষ্টগুলো থাকলে তা সিরিয়াস সাহিত্য হয় আর জনপ্রিয় সাহিত্য হচ্ছে প্রচুর পাঠক যে বই পড়ছে, তাহলে কী দাঁড়ালো? কোনো সাহিত্য যদি হাতে গোণা দশ বারোজন পাঠকের মনস্তত্বে প্রভাব ফেলে, বা তারাই কেবল পড়ে- তাহলে কি সেটিকেই সমাজের বা রাষ্ট্রের বা মানুষের পরিবর্তন বলা যাবে? যাবে না। কারণ, কেবল ওই কয়েকজন মানুষই কিন্তু সমাজ নয়। কেবল তারাই এই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। বরং মূল সমাজ রয়ে যায় তাদের বাইরে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবিত হবে। অথচ তারা কিন্তু ওই সাহিত্যের কথা জানেই না। আমার কাছে বরং আমাদেরর দেশের বাস্তবতায় এই বিভাজনকে এক শ্রেণির মানুষের অতৃপ্তিকে আত্মতুষ্টিতে পরিণত করার কৌশল মনে হয়। না হলে পাওলো কোয়েলহো, হারুকি মুরাকামি এদের লেখা বই মিলিয়ন মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। তো তাহলে তারা কী? সিরিয়াস সাহিত্যক, না জনপ্রিয় সাহিত্যিক? কারো ব্ই জনপ্রিয় হল্ইে আর সে ক্ল্যাসিক নয়? তার সাহিত্য সিরিয়াস সাহিত্য নয়?
আমার বরং মনে হয়, এই বিতর্কটাই অনর্থক। অপ্রয়োজনীয়। একধরনের মানুষ তাদের হতাশা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে কিংবা নিজেদের প্রবোধ দিতে এইসব বিতর্ক তৈরি করে কৃত্রিম, আরোপিত আত্মতুষ্টিতে ভোগার চেষ্টা করেন যে যেহেতু আমাদের বইয়ের পাঠক যেহেতু কম, সেহেতু আমরা সিরিয়াস লেখক। আর যাদের ব্ই অনেক পাঠক কিনছে তারা ক্ল্যাসিক বা সিরিয়াস নয়। এখানে তারা জনপ্রিয় শব্দটাকে তুচ্ছার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। আর যদি সমাজে ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করাকে সিরিয়াস সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বলেন, তাহলে আমাদের দেশের বাস্তবতায় তার দৃশ্যমান উদাহরণ দেখতে আমি খুব্ই আগ্রহী। আমাদের দেশে-সমাজে-রাজনীতিতে কিংবা মানুষের মনস্তত্বে সেই অর্থে দৃশ্যমান ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে পেরেছে- সেরকম সিরিয়াস সাহিত্য আসলে কোনগুলো? এদেশের কোনো সাহিত্য কি ফরাসি রেভ্যুলেশনের মতো শক্তিশালী কোনো মনস্তাত্বিক বা সামাজিক গ্রাউন্ড তৈরি করতে পেরেছে? আমার অন্তত জানা নেই। আমিতো বরং দেখি হুমায়ূন আহমেদেও সাহিত্য নানাভাবে ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে। অথচ আমরা তাকে সিরিয়াস সাহিত্যিক হিসেবে গ্রহণ করতে নারাজ। ক্রিটিকদের কাছে তিনি সিরিয়াস সাহিত্যিক ছিলেন না বলে সমালোচিত। অথচ সাধারণ মানুষের জীবনে, সংস্কৃতিতে কিংবা মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে যদি কারো লেখা বিস্তৃতভাবে সক্রিয় প্রভাব ফেলতে পেরেছে, তিনি হুমায়ূন আহমেদ।
আপনি নিম্ন বর্ণের মানুষের অবহেলা, বঞ্চনার কথা লিখে তা নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসে চার পাঁচজন বোদ্ধার সাথে আলোচনা করলেন, কিন্তু সেই সাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো ভূমিকা কি আদৌ রাখতে পেরেছে? পারে? পারেনি। তাহলে সেই সাহিত্যের ইমপ্যাক্ট আসলে কোথায়? ইউরোপে মানুষের পাঠ অভ্যাসের যে হার তার সাথে আমাদের দেশের তুলনা করলে চলবে না। যখন অনেক মানুষ বই পড়বে তখন তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার সুযোগ তৈরি হবে। কম মানুষ বই পড়লে ইনফ্লুয়েন্স করার সুযোগ কম থাকবে। আর কম মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করলে তা সমাজের পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে কী করে? ইউরোপে ঐতিহ্যের কারণে, সভ্যতার ইতিহাসের কারণে, বা তাদের সংস্কৃতির কারণেই হোক- বেশিরভাগ মানুষ বই পড়ে। তাই সেখানে ওই কথিত সিরিয়াস সাহিত্যও পাঠকের কাছে পৌঁছাত এবং সেগুলো পড়ে তারা অনুপ্রাণিত আর উদ্বুদ্ধ হতো; কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় ওই একই সমান্তরালে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়াকে আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, অপরিপক্ব চিন্তা বলে মনে হয়। আমাদের সংস্কৃতিকে আমাদের সাপে¶ে চিন্তা করতে হবে। এদেশের কতজন মানুষ বই পড়ে? ফলে এখানে জনপ্রিয় ও সিরিয়াস সাহিত্য- এধরনের বিভাজনের কোনো যুক্তি আমি দেখি না। বরং এদেশে অনেক বেশি জনপ্রিয় সাহিত্য দরকার, যত বেশি জনপ্রিয় সাহিত্য তৈরি হবে, ততো বেশি মানুষ বই পড়বেÑ তখন ‘সিরিয়াস’ সাহিত্য বলে যা তারা রচনা করছেন, তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগও তৈরি হবে। লেখকদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, তারা নিজেদের ব্যর্থতা পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায় মুক্তির পথ খোঁজেন। যদি ভাবেন যে আপনার বই কেউ পড়ছে না, এর মানে সেটি পাঠকের সীমাবদ্ধতা এবং আপনি সেই পাঠকের তুলনায় সুপারিয়র, উত্তম, একারণে আপনার লেখা পাঠক হৃদায়ঙ্গম করতে পারছে না। তাহলে আমি বরং সেটিকে পাঠকের নয়, লেখকের ব্যর্থতা বলে বিবেচনা করতে চাই। পাঠকের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দিলে, লেখক হিসেবে এটা আপনার ব্যর্থতা বলে আমি মনে করি। কারণ লেখকের দায়িত্ব পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। ভাষা কিংবা সাহিত্যের কাজও তাই। কমিউনিকেশন তৈরি করা। লিঙ্গুইস্টিকস বা ভাষাতত্ত্বে এই বিষয়ে একটা ইন্টারেস্টিং আলোচনা আছে। সম্ভবত সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ ডি সস্যুঘ ভাষা কিভাবে ইমেজ তৈরি করে, বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে অর্থময়তা তৈরি করে যোগাযোগ স্থাপন করে, তা ব্যাখ্যায় দুটি টার্ম ব্যবহার করেছিলেন। সিগ্নিফায়ার ও সিগনিফায়েড। আমরা যখন কোনো কিছু লিখি বা বলি তখন সেটি আগে আমাদের কল্পনার জগতে ইমেজ তৈরি করে, ইঙ্গিত তৈরি করে। অর্থাৎ সিগ্নিফায়ার তৈরি করে। ধরুন আমি একটি নদীর বর্ণনা দেব, তাহলে সেই নদীটিকে আগে আমার মস্তিস্কে বা কল্পনায় থাকতে হবে। তারপর লেখা বা ভাষার মাধ্যমে সেটিকে আমি প্রকাশ করব। সেটি সিগ্নফায়েড হবে। অন্যের কাছে পৌঁছাবে। যোগাযোগ তৈরি করবে। অর্থাৎ ভাষা এভাবে তৈরি হয়। যা বলছিলাম, ভাষার কাজ কি? যোগাযোগ স্থাপন করা, তাইতো? সাহিত্যের কাজও কিন্তু তাই। সিরিয়াস সাহিত্য রচনা করে যদি পাঠকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা না যায়, তাহলে সেটির অর্থময়তা কী? সেই ব্যর্থতা কার? পাঠকের, না লেখকের? সিগনিফায়ার ও সিগনিফাইড-এর একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন, আপনি একটি রুমের মধ্যে বেলুন, মোমবাতি, কেক সাজিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ সিগনিফায়ার (ইঙ্গিত) দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে এখানে একটা জন্মদিনের পার্টি হবে। এখন যাদের সামনে আপনি মোমবাতি, বেলুন, কেক রেখেছেন তারা যদি না জানে যে এগুলোর সাথে জন্মদিনের কি সম্পর্ক, তাহলে সেটি তাদের কাছে কী অর্থময়তা প্রকাশ করবে? ওইসব ইঙ্গিতের অর্থ তারা বুঝতে পারবে? পারবে না। এখন তারা কেন বুঝতে পারছে না, এই বলে আপনি যদি তাদেরকে দোষ দেন, বলেন যে তারা কেন আপনার উঁচু চিন্তার জায়গায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না, তাহলেই কী আপনার দায় শেষ? আমার তা মনে হয় না। আমার বরং মনে হয়, হয় আপনাকে তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে, নয়তো আপনার ভাষা বোঝানোর মতো স¶মতা তাদের তৈরি করতে হবে। ভাষা এবং সাহিত্যের কাজ হলো সংযোগ স্থাপন করা, এখন লেখক যদি সংযোগ স্থাপন না করতে পারেন তাহলে এর দায়ভার একান্তই তার বলে মনে করি আমি। আমার কাছে মনে হয়, আমাদের দেশের যে বাস্তবতা, তাতে এতো বিভাজনের সুযোগ নেই। বরং সবার আগে সহিত্যকে, বই পড়াকে জনপ্রিয় করতে হবে। মানুষের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এবং একারণেই জনপ্রিয় সাহিত্য হতে হবে বেশি বেশি। মানুষকে সবার আগে বইয়ের কাছে আনতে হবে। তারা যদি বইয়ের কাছে আসে, তারপর এইসব বিতর্ক করার বহু স্পেস তৈরি হবে। তার আগে না।
- আপনি লিখতে শুরু করেন যখন, তখন আপনার প্রেরণা ছিলেন কোন কোন লেখক?
সাদাত হোসাইন : সেরকম কেউ ছিল না, তবে আমার কাছে মনে হয়েছে ছেলেবেলায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছেন। তার বড় পরিসরের উপন্যাস পড়তে আমার খুব ভালো লাগত।পাঠকজনপ্রিয়তার কারণেই সাহিত্যিক জনপ্রিয় হয়ে থাকেন, তবে সাহিত্যে জনপ্রিয় কিছু জনরা রয়েছে, সেইসকল জনরায় লেখার চর্চার মাধ্যমেও জনপ্রিয়তা তৈরি হয়Ñ আপনি এ সময়ের জনপ্রিয় একজন কথাসাহিত্যিক, এ বিষয়ে আপনার ভাবনা কেমন?
সাদাত হোসাইন : লেখকের সবচেয়ে বড় ¶মতা, পাঠককে পড়তে পারার ¶মতা। এটা নাহলে লেখক কোনোভাবেই সফল হবেন না। আইনস্টাইনের একটা বিখ্যাত উক্তি আছেÑ প্রত্যেকটি মানুষই আসলে প্রতিভাবান, কিন্তু সে কোন কাজে আসলে প্রতিভা দেখাতে স¶ম হবে সেটা তাকে বুঝতে হবে। বুঝতে গিয়ে অনেকেরই হয়তো সারা জীবন কেটে যায়। আত্ম অনুসন্ধান করাটা খুব জরুরী। এখন ওই সক্ষমতা না বুঝে কেবল ঝোঁকের বশে, বা ধরুন ট্রেন্ডে ভেসে গিয়ে যিনি হয়তো কবিতায় দক্ষ, দেখা গেলো তিনি থ্রিলার লেখার চেষ্টা করছেন। আবার যিনি থ্রিলারে সহজাতভাবেই সক্ষম, তিনি সামাজিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছেন, যিনি গল্পে ভালো, তিনি পদ্য লিখছেন। তখন কিন্তু তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। এ কারণেই লেখকের সবার আগে আত্ম অনুসন্ধান জরুরী। লেখকের এই অনুসন্ধানে তার সহজাত স¶মতা আবিষ্কার করতে পারলে, আর তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারবেন বা পাঠক প্রিয় হবেন। এত মানুষ থ্রিলার লিখেছে তবু রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা কেন এত জনপ্রিয় হয়েছে? তার জায়গায় একই জিনিস লিখতে এসে শামসুদ্দিন নওয়াব কি সেই সফলতা পেয়েছেন? পাননি। হুমায়ূন আহমেদ সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন, আবার মিসির আলির মতো চরিত্র তৈরি করেছেন আবার সায়েন্স ফিকশনও লিখেছেন, তার সব লেখাই কিন্তু মানুষের কাছে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে। কারণ, তিনি সবক্ষেত্রেই সাবলীল ছিলেন। এটা তার সক্ষমতা। কিন্তু অন্য কারো ক্ষেত্রেও যে তা এক্ইরকম হবে, তা কিন্তু নয়। জনপ্রিয় জনরা কাউকে জনপ্রিয় করতে পারে না, লেখক যখন তার নিজের দ¶তা আবিষ্কার করতে পারেন, তখন লেখাই লেখককে পাঠকপ্রিয় করে তোলে।
- সাহিত্যে যারা একবার জনপ্রিয় হন, সেই জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য অনেক ¶েত্রে অধিক গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব এসে পড়ে লেখকের ওপর, এ বিষয়টি কখনও অনুভব করেন কি?
সাদাত হোসাইন : এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পেশাদার লেখক। অর্থাৎ লিখে জীবনধারন করি। আমার পরিবার এই উপার্জনের ওপরই নির্ভরশীল। এখন ধরুন, মানে উদাহরণ দিতে গিয়ে যদি ধরেও নেই যে আমিই সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক, তাহলেও আমি আমার বইমেলার বই বিক্রি থেকে যে রয়ালিটি পাবো তা দিয়ে মোটামুটি ভালোভাবে কতদিন চলতে পারবো? একবছর? দুই বছর? তার বেশিতো নয়? তাহলে? পাঁচ বছরে একটি বই লিখে আমি সার্ভাইভ করবো কীভাবে? অথচ পৃথিবীর বহু দেশে একটি বেস্ট সেলার বই লিখেই কিন্তু লেখক বাকি জীবন আরামসে কাটিয়ে দিতে পারেন। পারেন না? কিন্তু আমরা পারি না। আমাদের লেখাকে পেশা হিসেবে নিতে হলে, যতই জনপ্রিয় হই না কেন, প্রতি বছরই লিখতে হবে। কারণ, আমাদেও পাঠক সংখ্যা ভয়াবহরকম কম। হয়তো এই বাস্তবতায় জনপ্রিয়তার কথাও ভাবতে হয়। আবার প্রকাশকদেরও ডিমান্ড থাকে। কারণ তাদেরও ভয়াবহ স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমরা হয়তো চট করে অভিযোগ করি যে তারা লেখকদের রয়ালিটি দেন না, হয়তো অনেকেই এটি করেনও। কিন্তু উল্টো বাস্তবতাওতো আছে। একটু খোঁজ নিলেই হয়তো দেখা যাবে, ঠিক কতজন লেখকের বই কতসংখ্যক কপি বিক্রি হয়। প্রকাশকের খরচ কত, দোকান ভাড়া কত, কর্মীদের বেতন দিয়ে তার আসলে আয় কত হচ্ছে। এখানে আমি কাউকে দায়মুক্তি দিচ্ছি না বা কাউকে দোষীও করছি না। আমি জাস্ট রিয়েলিটিটা বলছি। আমাদের লেখালেখি জগতের রিয়েলিটিটা ভীষণ কঠিন। এখানে বাইরে থেকে চট করে মন্তব্য করা সহজ। কিন্তু বাস্তবতা বোঝা সহজ নয়। এই বাস্তবতায় যতো বেশি জনপ্রিয় লেখক আসবেন, তত বেশি প্রকাশনা টিকে থাকবে। প্রকাশকরাও বিনিয়োগে বা ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হবেন। এখন জনপ্রিয় লেখকের সংখ্যাতো কম। হয়তো এ কারণেই তারা চান, যারা জনপ্রিয় তারা বেশি বেশি লিখুন। এ কারণে প্রেসার তো অবশ্যই থাকে। আর আমি যেহেতু পেশাদার লেখক, সেহেতু এই জায়গাতে আমাকে কখনো কখনো কম্প্রোমাইজ করতেই হয়।
- হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক লেখক। তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন, নাটক লিখেছেন, শিশুদের জন্য গল্প লিখেছেন, বড়দের জন্য গল্প লিখেছেন, সিনেমা পরিচালক হয়েছেন নিজে- পাঠকের নিকট তিনি নমস্য এক কথাকার- আপনার নির্বাচনে তার শ্রেষ্ঠ কাজগুলি নিয়ে জানতে চাই…
সাদাত হোসাইন : হুমায়ূন আহমেদকে বিস্ময়কর প্রতিভা মনে হয় আমার। তার ছোটগল্প অসাধারণ। উপন্যাসও খুব শক্তিশালী। তার লেখা শঙ্খনীল কারাগার, নন্দিত নরকে, অপে¶া, কোথাও কেউ নেই, এপিটাফ, জোছনা ও জননীর গল্প বিশেষভাবে ভালো লাগে। হলুদ হিমু কালো র্যাব- যখন লিখেছিলেন, তখনকার বাস্তবতায় সেটিও ভীষণ দুঃসাহসী কাজ ছিলো।
আপনার নিজের লেখার পরিধি কেমন হবে ভবিষ্যতে- সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের বাইরেও নিজেকে নিতে চান কীভাবে?
সাদাত হোসাইন : আমার স্বপ্ন যে আমার লেখা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হবে, আমাদের দেশে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের অনুবাদ এখনো হয় না। কেন হয় না, তা জানি না। কিন্তু যদি সেটি হতো, তাহলে আমাদের অনেক লেখকের লেখাই হয়তো বিভিন্ন দেশের মানুষ পড়তে পারত।
এ যাবৎ আপনার লেখা পাঠকপ্রিয় বইগুলোর মধ্যে আপনার প্রিয় বইটি নিয়ে বলুন…
সাদাত হোসাইন : নিজের লেখা থেকে আসলে সেভাবে আলাদা করে বলা যায় না। অনেকগুলোই প্রিয়। যেমন-অন্দরমহল, নির্বাসন, অর্ধবৃত্ত, আরশিনগর, শঙ্খচূড়। আসলে এটা বরং পাঠকই ভালো বলতে পারবে।
- আপনি একটি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কেমন প্রস্তুতি নেন?
সাদাত হোসাইন : প্রথম ভ্রমণ উপাখ্যান লিখেছি, সম্প্রতি ইউরোপ ট্যুরে গিয়েছিলাম, নাম হচ্ছে যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই। এটা লিখতে গিয়ে আমাকে অনেক পড়ালেখা করতে হয়েছে। আবার যখন অন্দরমহল লিখলামÑ কয়েকশত বছর আগের একটা গল্প, সেটার জন্য সেই সময়ের জীবনযাপন, ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হয়েছে। কনটেম্পরারি উপন্যাস লিখছি সেটা প্রস্তুতি ছাড়াই লিখতে পারি। আসলে প্রস্তুতি ডিপেন্ড করে কোন টপিকের উপরে লিখছি তার ওপর।