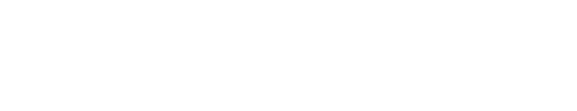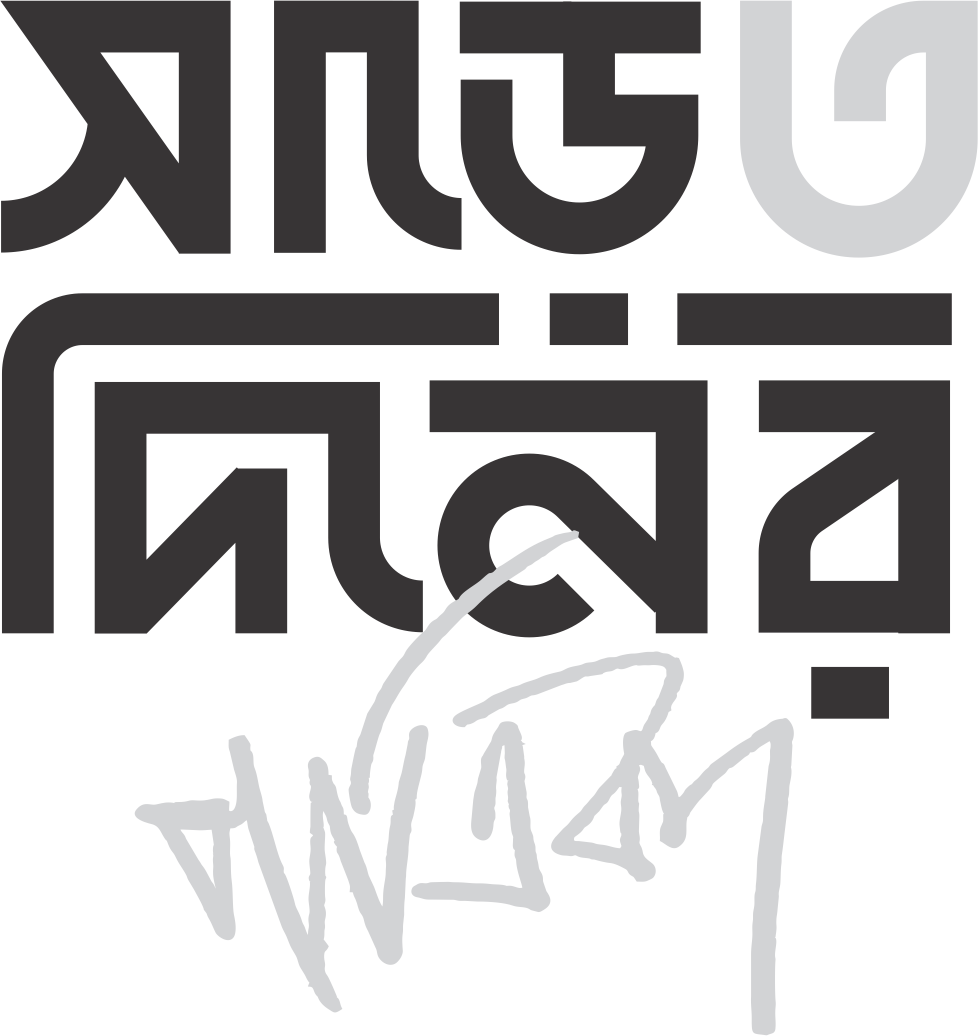শিশির ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। জন্ম ৪ আগস্ট, ১৯৬৩, চট্টগ্রামে। ভাষাবিজ্ঞানে তিনি পিএইচ.ডি করেছেন কানাডার মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ে দেশি ও বিদেশি জার্নালে প্রায় ৪০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ‘সঞ্জননী ব্যাকরণ’, ‘অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ’, ‘বাংলা ভাষা: প্রকৃত সমস্যা ও পেশাদারি সমাধান’, ‘বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা’ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক শিশির ভট্টাচার্য্যরে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাকির উসমান ও নুসরাত নুসিন
- একটা দেশের উন্নয়নে ভাষার গুরুত্ব কতখানি?
শিশির ভট্টাচার্য্য : দেশটা কি? দেশ তো সীমানা না শুধু। আমাদের প্রায় ১৬ কোটি মানুষ। এটা আমাদের জনশক্তি। এই জনশক্তির দুটো ব্যবহার আছে। দেশ চালায় তো আমাদের জনগণই, আবার আমরা জনশক্তি রফতানিও করি। যে কেউ চাইবে তার রফতানিযোগ্য মালের উন্নয়ন করতে। কারণ তাকে বেশি পয়সা পেতে হবে। খারাপ মাল দিলেন, পয়সা পাবেন না। জাপানি গাড়ির দাম নিশ্চয়ই চীনা গাড়ির চেয়ে বেশি। আমাদের লক্ষ্য হবে, যে জনসম্পদ বাইরে রফতানি করব তারা যেন উন্নতমানের সম্পদ হয়। রফতানি করার মতো যোগ্য হয়। শিক্ষা ছাড়া সেটা কীভাবে হবে? ধরেন, শ্রীলঙ্কান শ্রমিক, ভারতীয় শ্রমিক আর বাংলাদেশের শ্রমিকের বেতনের অনেক পার্থক্য আছে। কারণটা কী? শ্রীলঙ্কান শ্রমিক আর ভারতীয় শ্রমিক ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। আমাদের শ্রমিক বাংলাও ভালো করে বলতে পারেন না। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? ভাষার বিষয়ই তো দাঁড়ালো। আবার ভাষার উপর যদি দখল থাকে, যে কোনো জায়গায় গিয়ে নতুন করে মিশে যাওয়া, অন্যকে বুঝতে পারা, এসব দ্রুত ঘটবে। এসব শিক্ষা ছাড়া কিন্তু সম্ভব নয়।
জনগণের পেছনেই আমাদের ইনভেস্ট করতে হবে। তাদের শিক্ষা দিতে হবে। একটা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটা শিক্ষিত বাজার তৈরি করবে। সিঙ্গাপুরের বাজারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাজারের তুলনা করতে পারবেন? সিঙ্গাপুরের বাজারের মানুষের যে ক্রয়ক্ষমতা, কেন? শিক্ষিত হয়েছে বলেই তো। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সিঙ্গাপুর ছিল একটা জেলেপাড়া। তখন কি ক্রয়ক্ষমতা ছিল? ছিল না। শুধু শিক্ষা দিয়েই সিঙ্গাপুর আজকে উন্নত।
- যে উদ্দেশ্যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে করেন?
শিশির ভট্টাচার্য্য : বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়নি। কারণ বাঙালি বাংলাকে ঘৃণা করে। গরিবও ঘৃণা করে, বড়লোকও ঘৃণা করে, মধ্যবিত্তও করে। কী প্রমাণ? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখেন প্রত্যেকের ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে। তার মানে কি আপনি বাংলাকে বিশ্বাস করছেন না! এটা ছোটলোকের ভাষা, এটা গরিবের ভাষা, দারোয়ানের ভাষা। আমি এই ভাষায় আমার ছেলেমেয়েকে পড়াব কেন? ঠিক যেমন করে মধ্যযুগে বলতÑ ইংরেজি ছোটলোকের ভাষা, জার্মান, ফরাসি ছোটলোকের ভাষা। আমার ছেলেকে আমি ল্যাটিন পড়াব।
মধ্যবিত্তের দরকার একটা বড় চাকরি। এ জন্য ইংরেজি মাধ্যমে সন্তানকে পড়াতেই হবে। সবমিলিয়ে আমরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছি। ফলে আমরা ইংরেজিও শিখতে পারছি না। এ দেশে আপনি ইংরেজি কীভাবে শিখবেন? এখানে তো ইংরেজির ইনপুট নেই। আছে বাংলা ভাষার ইনপুট, আঞ্চলিক ভাষার ইনপুট। ইংরেজি কখনোই এখানে ঠিকমত পড়ানো যাবে না। এই অসম্ভব কাজ করতে গিয়ে ইংরেজিকেও হারাচ্ছি, বিষয়গুলোকেও হারাচ্ছি। বিষয়গুলো হারানোর পরে কী হচ্ছেÑ আমরা ভালো বিজ্ঞানী পাচ্ছি না, ভালো প্রকৌশলী পাচ্ছি না।
‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ এটা ছিল একটা অতি উন্নত মানের স্লোগান। যেটা আমরা করতে তো পারিই নাই; যেটা হয়েছে এখন আমাদের ‘মাতৃভাষা দিবস’। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না। ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়’ পুরোটাই মিথ্যা কথা। ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায় নাই। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিসিএস পরীক্ষায় ফেল করত। পাকিস্তানিরা এগিয়ে যেত। আমরা পিছিয়ে পড়তাম। এ জন্য রাষ্ট্রভাষা দরকার ছিল। তাতে কি আমরা পাকিস্তানের নাগরিক হতে পারতাম। পারতাম না। আমরা হতাম দুই নম্বর নাগরিক। ঠিক এখন যেমন গারো, সাঁওতালরা দুই নম্বর নাগরিক। ভালো ইংরেজি বাংলা না বলতে পারার কারণে। তাদেরকে আমরা সামনে আনতে চাই। কিন্তু পাকিস্তানিরা সেটা চায়নি। কারণ তারা আমাদের ঘৃণা করত। তো এই যে সমস্যাটা রাষ্ট্রভাষা তো তারা হাসিল করতে পারে নাই। ওই দিবসটাকে বানিয়েছে ‘মাতৃভাষা দিবস’। এটা আরেকটা মিথ্যা কথা। মিথ্যার উপর মিথ্যা। রাষ্ট্রভাষা না করলে ভাষার উপর দখল থাকবে না। আপনি ইংরেজিতে পড়তে গিয়ে ইংরেজিও শিখবেন না। কোটি কোটি বাঙালিকে ইংরেজি শেখানো সম্ভব না। সুতরাং এটা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু নিজের পায়ে কুড়াল মারছি। ফলে আমরা এখন মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে কামলা দিচ্ছি। কালকে বার্মায় গিয়ে কামলা দেব।
- এই যে ইংরেজি শেখানোর প্রবণতা এটা কি পুরোটাই হীনম্মন্যতা থেকে?
শিশির ভট্টাচার্য্য : এটা অনেক পুরোনো রোগÑ ওই ভাষা ভালো। ওইটাই পিওর ভাষা! আরে ইংরেজি তো ছোটলোকের ভাষা। ইংরেজি ছিল ফরাসিদের রাষ্ট্রভাষা। ইংরেজি তো ওরা বলতোই না। যেমন চাকরবাকররা বলত। বুয়ার ভাষা। চিটাগাইঙা, বরিশাইল্যারা, নোয়াখাইল্যারা যে ভাষায় কথা বলে তা বুয়ার ভাষা। একই ব্যাপার ছিল। তো বাংলাকে বুয়ার ভাষা গণ্য করে। সেজন্য তারা মনে করে, ইংরেজিতে পড়ালেখা করতে হবে। কালকেই একটা তর্ক হলো, বাংলাতে কেমন করে লেখাপড়া হবে? বাংলাতে তো পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাবে। যেন বাংলাতে পড়লে নষ্ট হয়ে যাবে। বাংলা তো একটা পড়ালেখার মাধ্যম মাত্র। সেটা আপনি বাংলাতে করেন, ইংরেজিতে করেন, ফরাসিতে করেন। অল দ্যা সেইম। কি পার্থক্য ওখানে? কিন্তু বাংলার উপর দখল থাকলে পড়ালেখাটা সহজ হবে। সরাসরি শাহবাগ যাওয়া এক জিনিস আর নীলক্ষে ঘুরে যাওয়া এক জিনিস। সমস্যা তো ওই জায়গায়।
- বাংলা ভাষার সম্ভাবনা কতটুকু বলে মনে করেন?
শিশির ভট্টাচার্য্য : বাংলা ভাষার বিশাল বাজার। আমার বাজারে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা থাকবে না। একটা ওষুধ যদি ঢোকে, আমার ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। আমাদের জিনিস বাঙালিরা সঙ্গে করে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণ আমাদের তরুণ জনশক্তি। বাংলাদেশে কেবল বাচ্চা হচ্ছে। অন্য কোথাও এত বাচ্চা জন্ম হচ্ছে না। এই যে তরুণ, আমাদের বিশাল বাজার। আমাদের ভাষা বিখ্যাত। চীনারা সারা পৃথিবীতে আটশ কনফুসিয়াস সেন্টার করেছে, যাতে চীনা ভাষা ছড়িয়ে দেয়া যায়। আমরা বাঙালিরা চারটা সেন্টার গড়ে তুলিÑ সবকিছু বাংলায় করতে হবে। ইংরেজিও পাশাপাশি থাকবে। বাংলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষাই হচ্ছে আমার প্রাণ। শিক্ষার মাধ্যম। আমার ভাষা ডেভেলপ করতে হবে।
- বাংলা শিক্ষার সার্বজনীন মাধ্যম হয়ে উঠছে না কেন?
শিশির ভট্টাচার্য্য : আমরা চাচ্ছি না বলে। আমরা জানি না এর কি শক্তি! নিজের বাচ্চাকে আপনি ‘জারজ’ বলছেন। আমার ভাষা, আমার মাকে আমরা অস্বীকার করছি। এটা হচ্ছে বোকা জাতি, বোকা লোকজন, যারা দেশের বাইরে গিয়ে কামলা দেবে। চীনা ভাষা কঠিন একটা ভাষা। ছয় হাজারের ওপর তার বর্ণমালা। তবু তারা সব চীনা ভাষায় করছে। আমাদের লোকজন বোঝে না এসব। ডাক্তার ডাক্তারি বোঝে না, ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বোঝে না, ভাষার লোক ভাষা বোঝে না। তারা কি বোঝে তারাই জানে না। আবার তারা বলে, ভাষার মাস। এটা কি জিনিস? ভাষা তো চব্বিশ ঘণ্টার জিনিস। সর্বক্ষণের অস্তিত্বের সঙ্গে ভাষা জড়িত।
- উন্নত অনেক দেশের কারিকুলাম নিজ দেশের ভাষায় করা, এমনকি নিজ দেশের মধ্যে যে আঞ্চলিক ভাষা আছে তা দিয়ে করা। আমাদের কারিকুলাম নিয়ে আপনার কোনো পর্যবেক্ষণ আছে?
শিশির ভট্টাচার্য্য : কারিকুলাম নিয়ে যথেষ্ট পড়ালেখা করেছি। আমাদের কারিকুলামটা চমৎকার! কারিকুলাম ঠিক আছে, সিলেবাস ঠিক আছে, ভাষাও ঠিক আছে। এখন এটা চালিয়ে যাওয়া যাবে কিনা এটা হচ্ছে কথা। আমাদের বর্তমান সরকারের গুণ হচ্ছে এই, ১৫টা করে বই ছাপিয়েছে আদিবাসী ভাষায়। এটা করা কঠিন কাজ। ইতিহাসে খুব বেশি দেখি নাই। ইতোমধ্যে আমাদের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে কিন্তু এমএ পাস শিক্ষক, সফটয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড এই দেশগুলো করে কি, আপনি ফিজিক্স থেকে পাস করলেন, ভাষা থেকেও আপনাকে একটা ডিগ্রি নিতে হবে। আপনাকে দুইটা ডিগ্রি নিতে হবে। আপনি প্রাইমারি স্কুলে কাজ করবেন। আপনার বেতন হবে সর্বোচ্চ। মন্ত্রীর চেয়ে বেশি। এ ভাবে তারা গত কুড়ি বছর চলছে। ফলে তাদের শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আসলে কারিকুলাম যাই হোক না কেন, পড়ানোর লোক যদি ভালো হয়, সে তো চক-পেন্সিল দিয়েই ভালো পড়াবে। ইতোমধ্যে ভালো শিক্ষকরা যোগ দিয়েছে। তাদের বেতনটা বাড়ানো হোক। শিক্ষায় বাজেট বাড়ানো হোক। দুটো সাবমেরিন কম কেনা হোক। বাজেটটা এখানে দেয়া হোক।
- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব পাঠ্যবই আছে, শিশুদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসব পাঠ্যবইয়ে কোনো ত্রুটি আছে কিনা?
শিশির ভট্টাচার্য্য : সব ঠিক আছে। সমস্যা হলো বাবা-মাকে নিয়ে। তাদের কোনো বিশ্ববীক্ষা নাই, নিজেরা লেখাপড়া জানে না। মানে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি যেমন ইংরেজি বলতে পারে না, বাংলায়ও কথা বলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির এই অবস্থা হলে বাকিদের অবস্থা আরও খারাপ। বাবা-মায়ের তো বাংলা ভাষার প্রতি দরদ নাই। বাবা-মা নিজেরাই মানুষ হননি। মানুষ না হওয়ার পেছনে দায়ি কে? আমাদের প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের রাষ্ট্র। আমাদের চিন্তাশীল মানুষ হতে হবে। আমরা লজিক্যালি চিন্তা করতে জানি না। ভাষায় দুর্বল মানে শিক্ষায় দুর্বল। সবই আমরা ভাসাভাসা জানি।
- তো আমাদের যে দুরবস্থা, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কী?
শিশির ভট্টাচার্য্য : পৃথিবীর দার্শনিকরা বলেন, গাছ লাগানোর আগে মানুষ লাগান। গাছ লাগালে পরিবেশ ঠিক হবে। কিন্তু মানুষ লাগালে সব ঠিক হয়ে যাবে। এর পেছনে দায় হলো আমাদের সামগ্রিক ঘাটতি। আমরা বুঝি না কোথায় ইনভেস্ট করতে হবে। শিক্ষায় বাজেট বাড়াতে হবে।